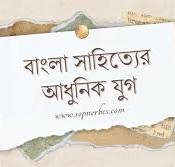বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি-বর্তমান)
বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি-বর্তমান)
বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরু প্রায় সুনিশ্চিতভাবেই ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ধরা হয়। এ যুগ নানা দিক থেকে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ, সমৃদ্ধি হওয়ার যুগ; বিশ্ব দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সুবিখ্যাত ও সমাদৃত হওয়ার যুগ।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থের রচয়িতা-
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শেখ হাসিনা
কাজী নজরুল ইসলাম
#.বাংলা গদ্যের সূচনা হয়-
নবম শতকে
ত্রয়োদশ শতকে
ষোড়শ শতকে
উনিশ শতকে
#.বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়-
১৮০১ সালে
১৮০২ সালে
১৮০৩ সালে
১৮৬১ সালে
#.বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের বৈশেষিক লক্ষণ নয় ----
ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য
গীতিকবিতা
শব্দালংকার
পারত্রিকতা
#.শ্রীকান্ত উপন্যাসটির কয় খন্ডে রচিত?
২
৩
৪
৫
বাংলা গদ্যের উৎপত্তি
বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ || আধুনিক যুগ
আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের শুরুতে রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে দৃশ্যমান হয় এবং বাংলা সাহিত্যে নতুন রাগিণী ধারার সূচনা ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতির সংস্পর্শে এসে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল আধুনিক যুগে। এ যুগের প্রতিভূ হলো বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল ধর্ম অথবা রাজবন্দনা আর আঙ্গিকে ছিল কেবলই কবিতা। কিন্তু আধুনিক যুগে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যের নব নব শাখা বিস্তৃত হলো। এ সময়ে মানবতাবোধ, যুক্তিবাদ, সমাজসচেতনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, গদ্যের প্রতিষ্ঠা, স্বদেশপ্রেম, রোমান্টিক দৃষ্টি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সাহিত্যে মূর্ত হয়ে উঠে । ১৮০১ থেকে বর্তমান পর্যন্ত আধুনিক হলে ও প্রকৃতপক্ষে আধুনিক যুগ শুরু ১৮৬০ সালের দিকে মাইকেল মুধুসূদনের আবির্ভাবের মাধ্যমে।
বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ
বাংলা সাহিত্যে গদ্যের সূচনা হয় উনিশ শতকে। ড. সুকুমার সেন বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ কালকে ৪ ভাগে ভাগ করেছেন যথা:
|
প্রথম স্তর |
সূচনা পর্ব- ষোড়শ শতাব্দী থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত |
|
দ্বিতীয় স্তর |
উন্মেষ পর্ব- ১৮০০ ( শ্রীরামপুর মিশন) থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত |
|
তৃতীয় স্তর |
অভ্যূদয় পর্ব- ১৮৪৭ ( বিদ্যাসাগর ) থেকে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত |
|
চতুর্থ স্তর |
পরিণতি পর্ব- ১৮৬৫ ( বঙ্কিমচন্দ্র) থেকে বর্তমান পর্যন্ত |
বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে যথা: প্রথম পর্যায় এবং দ্বিতীয় পর্যায়।
প্রথম পর্যায়
আধুনিক যুগকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। ১৮০১-১৮৬০ সাল পর্যন্ত প্রথম পর্যায় এবং ১৮৬১ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়। মানবিকতা, ব্যক্তিসচেতনতা, সমাজবোধ, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ, আত্মচেতনা ও আত্মপ্রসার, মৌলিকত্ব, নাগরিকতা, আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য, মুক্তবুদ্ধি প্রভৃতি আধুনিক যুগের লক্ষণ।
ঢাকার ভূষণার জমিদারপুত্রকে পর্তুগিজ দস্যুরা ধরে নিয়ে এক মিশনারীর কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। এ জমিদারপুত্রই পরে দোম এন্টিনিও দ্য রোজারিও নামে পরিচিত হন এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বই লিখেন। ১৭৪৩ সালে রচিত তাঁর ‘ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সূচনা। এটি লেখা হয় প্রশ্নোত্তর আকারে। এটি বাঙালির লেখা প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ কিন্তু বাংলা হরফে লিখা নয়। গ্রন্থটি রোমান হরফে পর্তুগালের লিসবন থেকে মুদ্রিত হয়েছিল।
আধুনিক যুগের উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে গদ্যরীতির প্রচলন ঘটে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে মূলত দলিল দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, আইনশাস্ত্রে গদ্য সীমাবদ্ধ ছিল। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে কোচবিহারের রাজার একটি পত্রকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন ধরা হয়। রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্রি মনো এল দ্য আসসুম্পসাঁও কর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত ‘কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নির্দশন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি বর্তমান গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ থানার নাগরী নামক স্থানে লিখিত। ১৭৪৩ সালে মনো এল দ্য আসসুম্পসাঁও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দকোষ তৈরির কাজ করেন যা তিনি শেষ করতে পারেননি। এছাড়া তিনি ব্যাকরণের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করেন।
দ্বিতীয় পর্যায়
১৮০০ সালে ডেনিশদের শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে বাংলা ভাষায় মুদ্রিত হয় মথি রচিত ‘মিশন সমাচার’ । তবে এটি বাঙালির লেখা নয়। ১৮০০ সালের ৪ মে কলকাতার লালবাজারে লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশে এ প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ অবদান রয়েছে।
১৮০১ সালের ২৪ নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন পাদ্রী উইলিয়াম কেরি। তিনি নিজে বাংলা বই রচনা করেন এবং নানা পণ্ডিত ও শিক্ষকদের দিয়ে বাংলা বই রচনা করান। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের বাংলা শিক্ষা দেয়া ।
উইলিয়াম কেরির ‘কথোপকথন' বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ।একে বাংলা ভাষার কথ্যরীতির প্রথম নিদর্শনও বলা হয়ে থাকে। তবে মথি রচিত ‘মিশন সমাচার’ বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বলা হলে ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে উইলিয়াম কেরির ‘কথোপকথন' । কারণ বাংলা গদ্য সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদানই সর্বাধিক। এক কথায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের মূল বিকাশ শুরু। রামরাম বসুর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাঙালির লেখা এবং বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত গদ্যগ্রন্থ। উইলিয়াম কেরি বাংলা শিখেছিলেন রামরাম বসুর কাছে। রামরাম বসু ছিলেন আরবি-ফারসি মেশানো সহজ বাংলার পক্ষপাতী। তিনি কেরি সাহেবের মুন্সী নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ‘লিপিমালা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্রসাহিত্য।
উইলিয়াম কেরি বঙ্গদেশে আসেন ১৭৯৩ সালে। ছাপাখানার কাজের প্রয়োজনে তিনি নিয়ে আসেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ও যশুয়া মার্সম্যানকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতার মুখে তিনি ডেনিশদের শ্রীরামপুর মিশনে আশ্রয় নেন এবং সেখানে ১৮০০ সালে প্রেস তৈরি করেন। তবে ব্রিটিশদের গ্রেফতারের ভয়ে তারা কলকাতায় যেতেন না। ১৮০০ সালে গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু করলে এর বাংলা বিভাগ চালু করার জন্য উপযুক্ত লোক পাওয়া যায়নি। সেজন্য তিনি উইলিয়াম কেরিকে দায়িত্ব দেন কেরির সকল শর্ত মেনে নিয়ে।
উইলিয়াম কেরি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সাহায্যে লিখেছিলেন একটি বাংলা ব্যাকরণ। তখনকার গদ্য ছিল আরবি-ফারসি শব্দপ্রধান। পরবর্তীতে ফরস্টার তাঁর মুনশীদের সংস্কৃত প্রধান রীতি অনুসরণ করে আইনের বই অনুবাদের নির্দেশ দেন। এর ফলে জমিদারের মত সহজ শব্দ হয়ে ওঠে ‘ভূম্যধিকারী’। পরবর্তীতে ১৮০৫ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার কেরিকে প্রভাবিত করে তাঁর ব্যাকরণের দ্বিতীয় সংস্করণে সংস্কৃতপ্রধান ভঙ্গি প্রতিষ্ঠা করেন ৷
১৮০১ সালে কেরি বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে নিযুক্ত হন। ১৮০৭ সালে তিনি এ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অপরাপর প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা প্রমুখ ।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.বাংলা গদ্যের জনক কে?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
উইলিয়াম কেরী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখান
শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা (Serampore Mission and Printing Press) একটি ঐতিহাসিক স্থান যা বাংলা ও ভারতীয় মুদ্রণ ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরি ও তার সঙ্গীরা শ্রীরামপুরে এই মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে স্থাপিত ছাপাখানাটি বাংলা এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় বই ও অন্যান্য প্রকাশনা মুদ্রণে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।
এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরা হলো:
·
প্রতিষ্ঠা:
শ্রীরামপুর মিশন ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়।
·
প্রতিষ্ঠাতা:
উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম ওয়ার্ড এবং মার্শম্যান এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
·
ছাপাখানা:
শ্রীরামপুর মিশন প্রেস বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্য, বাইবেল এবং অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
·
বহুভাষা প্রকাশনা:
এই প্রেস থেকে বাংলা ছাড়াও হিন্দি, অসমীয়া, ওড়িয়া, মারাঠি সহ বিভিন্ন ভাষায় বই প্রকাশিত হয়েছে।
·
গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা:
এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত কিছু উল্লেখযোগ্য বই হল "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" (রামরাম বসু), "বত্রিশ সিংহাসন" (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার)।
·
দিগ্দর্শন পত্রিকা:
শ্রীরামপুর মিশন থেকে ১৮১৮ সালে "দিগ্দর্শন" নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়, যা বাংলা ভাষার প্রথম দিকের সাময়িকীগুলির মধ্যে অন্যতম।
·
ঐতিহাসিক গুরুত্ব:
শ্রীরামপুর মিশন ও ছাপাখানা বাংলা গদ্যের বিকাশে, শিক্ষার প্রসারে এবং বহুভাষিক সাহিত্য প্রচারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
·
উত্তরাধিকার:
যদিও শ্রীরামপুর মিশন ১৮৪৫ সালে বন্ধ হয়ে যায়, এর ছাপাখানাটি ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত চালু ছিল
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ফোর্ট উইলিয়মের অভ্যন্তরভাগে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী কর্তৃক ১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যবিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। নবনিযুক্ত ইউরোপীয় আমলাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতি সাধনই ছিল এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। সুশিক্ষিত ও কুসংস্কারমুক্ত আমলাতন্ত্রের সহায়তায় কার্যকরভাবে ব্রিটিশ ভারত শাসনের এক পরিকল্পনা করেন লর্ড ওয়েলেসলী। বিদ্যমান ব্যবস্থায় পনেরো থেকে সতেরো বছর বয়সী বেশির ভাগ তরুণ অফিসার জেলা প্রশাসনে নিয়োগপ্রাপ্ত হতেন। কিন্তু স্থানীয় ইতিহাস, ভাষা ও শাসন-শৈলী সম্পর্কে কোন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হতো না। ওয়েলেসলী উপনিবেশিক প্রশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নবাগত অফিসারদেরকে প্রস্ত্তত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নৈতিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এভাবে একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রয়োজনীয়তা থেকেই লর্ড ওয়েলেসলী ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এর কলকাতা মাদ্রাসা ও জোনাথন ডানকানের বেনারস হিন্দু কলেজের মতো ওয়েলেসলীর এ কলেজ পরিপূর্ণ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারতবর্ষে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত চাঁদা এবং সরকারি ছাপাখানার আয়ের একটা অনির্ধারিত বরাদ্দ থেকে এ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের পরিকল্পনা করা হয়।
ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে কলেজে এক একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিটি বিভাগে ছিলেন একজন অধ্যাপক ও কয়েকজন সহকারী শিক্ষক। তৎকালীন ভারতে আদালতের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ফারসি শিক্ষাদানের জন্য কলেজে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর প্রধান ছিলেন সরকারের একজন ফারসি অনুবাদক নেইল বি. এডমনস্টোন। তাঁর সহকারী শিক্ষক দুজন ছিলেন সদর দীউয়ানি আদালতের বিচারক জন এইচ. হ্যারিংটন ও সৈনিক-কুটনীতিক ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন। ওয়েলেসলী আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য উইলিয়ম জোনস এর পরে সর্বোত্তম আরবি ভাষাবিশারদ হিসেবে বিবেচিত লেফটেন্যান্ট জন বেইলিকে নিযুক্ত করেন। হিন্দুস্থানি ভাষা বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় স্বনামধন্য ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সাহিত্যবিশারদ জন বি. গিলক্রাইস্টের উপর। সংস্কৃত বিভাগের প্রধান নির্বাচিত হন বিখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ এইচ.টি কোলব্রুক। বাংলাসহ ভারতের অনেক ভাষা বিশেষজ্ঞ ও ধর্মপ্রচারক উইলিয়ম কেরীকে স্থানীয় ভাষা বিভাগের প্রধান নিয়োগ করা হয়। সব কয়টি বিভাগে কয়েকজন পন্ডিত ও মুন্সি ছিলেন। কলেজ কর্মচারীদের মধ্যে তাঁরাই ছিলেন দেশীয়। এভাবে ১৮০৫ সালের মধ্যে কলেজে মোট ১২টি অনুষদ খোলা হয়। কলেজের কর্মচারীদের বেতন স্কেলে সমতা বিধান করা হয় নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপীয় অনুষদ সদস্যরা যেখানে প্রতি মাসে ১৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা বেতন পেতেন, সেখানে তাঁদের এদেশীয় সহকর্মীরা (তাদের ভাষা শিক্ষক ও সহকারী) পেতেন মাত্র ৪০ থেকে ২০০ টাকা। অনুষদ প্রফেসরদের নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল কলেজ প্রশাসন পরিচালনা করত। শৃঙ্খলামূলক বিষয়গুলি দেখাশোনার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল দুজন যাজক, প্রভোস্ট ও ভাইস-প্রভোস্টের উপর। কলেজ প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল। এ কলেজের সকল ছাত্র ছিলেন সদ্য আগত কোম্পানির সনদ প্রাপ্ত কর্মকর্তা। চাকরিস্থলে নিয়োজিত হওয়ার আগে তাদেরকে পরপর দুবছর ভাষা ও প্রশাসন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হতো। ওয়েলেসলী নিজে ছিলেন একজন উঁচুমানের বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর স্বপ্ন ছিল যে, তাঁর এ কলেজ কলা ও বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র হিসেবে এমনই বিকশিত হয়ে উঠবে যে একদিন তা ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’-এর মর্যাদায় উন্নীত হবে। বস্ত্তত কলেজটি সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে চলছিল।
শ্রীরামপুর প্রেস ও এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সহযোগিতায় গবেষণা ও প্রকাশনার কাজ শুরু হয়। কলেজের শিক্ষকবর্গ প্রাচ্য সভ্যতার ব্যাখ্যাকার হিসেবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের রচনা ও ধ্যান-ধারণা ইউরোপীয় প্রাচ্যবিশারদদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বহু ছাত্রও পরে প্রাচ্যবিশারদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রতিষ্ঠার প্রথম দশকের মধ্যে এ কলেজ থেকে উত্তীর্ণ সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা প্রাচ্যবিশারদ হিসেবে বিখ্যাত হন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: ডব্লিউ.ডব্লিউ বার্ড, আর. ব্রাউন, টি. ফোর্টেস্ক, এইচ.পি হগটন, এইচ. ম্যাকেঞ্জি, এম.বি মার্টিন, সি. মেটকাফে, এইচ.টি প্রিন্সেপ, এইচ. শেক্সপিয়ার ও এ. টড। কলেজের শিক্ষক ও প্রাক্তন বিদ্বান ব্যক্তিগণ বাংলাসহ ভারতের প্রায় সকল ভাষার সংস্কার ও আধুনিকায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। কলেজের বাঙালি শিক্ষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিলেন রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। এ সকল পন্ডিতের সাহায্যে কলেজের অধ্যাপকগণ বাংলা ভাষার মান উন্নয়ন ও বাংলা গদ্য রীতির প্রবর্তনের কাজে সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উৎসাহ ও সহযোগিতায় মুদ্রণ প্রযুক্তি ও বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশনা শুরু হয় এবং জ্ঞান চর্চার কয়েকটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৮০১ সালে সুবিখ্যাত শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, পরের বছর হিন্দুস্তানি প্রেস, ১৮০৫ সালে ফারসি ছাপাখানা এবং ১৮০৭ সালে সংস্কৃত ছাপাখানার যাত্রা শুরু হয়। এ ছাপাখানাগুলিই ছিল বাংলায় বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের প্রথম বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের দ্রুত পরিবর্তনের গোটা কৃতিত্বই ছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের। বস্ত্তত কলেজটি দ্রুত ‘প্রাচ্যের অক্সফোর্ড’ হয়ে উঠছিল।
কিন্তু কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স (পরিচালকসভা) পদ্ধতিগত কারণে এই প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান করে নি। তাঁদের যুক্তি ছিল, এ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পরিচালকসভার পূর্ব অনুমোদন নেওয়া হয়নি। পরিচালকসভা ওয়েলেসলীকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অচিরেই ইংল্যান্ডে স্থাপন করা হবে। ফলত ১৮০৫ সালে ইংল্যান্ডের হেইলিবেরি নামক স্থানে ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ স্থাপিত হয় যা সাধারণভাবে হেইলিবেরি কলেজ নামে পরিচিতি লাভ করে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের কয়েকজন বিখ্যাত পন্ডিতকে অধ্যাপক নিয়োগ করে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
তবে বাস্তব অবস্থার নিরিখে অবশ্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনার অনুমতি দেওয়া হয়। হেইলিবেরি কলেজ থেকে যে সব তরুণ অফিসার সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতেন তাঁদেরকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরও ভাষাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হতো। তবে অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, প্রশিক্ষণার্থীদের অনেকেই দেশীয় ভাষায় অধিকতর প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণ করতেন এবং আর্থিক সঙ্কট সত্ত্বেও কলেজের দেশীয় ও ইউরোপীয় শিক্ষকগণ দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে থাকেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক শিক্ষা ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রাচ্যবাদী পথ বর্জন করতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। তিনি দেশীয় ভাষায় বই লেখা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে কলেজের উদ্যোগে গৃহীত প্রকল্পগুলির জন্য তহবিল প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। ১৮৩০ সালে বেন্টিঙ্ক ইংরেজিকে জনশিক্ষার মাধ্যম করে তাঁর শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। ঐ বছরই তিনি কলেজের অধ্যাপকদের পদগুলি বিলোপ করেন এবং ১৮৩১ সালে কলেজ কাউন্সিলও বিলোপ করা হয়। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, বেন্টিঙ্ক কলেজের নামফলকটি অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং কয়েকজন দেশীয় পন্ডিতকে তাদের পদে বহাল রেখে আমলাদের ব্যক্তিগত শিক্ষক হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেন। ডালহৌসীর সরকার ১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়মের এ ফ্যানট্যাম কলেজটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলোপ করেন।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৭৯৯
১৮০০
১৮০১
১৮০২
#.কোন জন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ছিলন?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ভূদেব মুখোপাধ্যায়
রাজা রামমোহন রায়
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
#.ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ খোলা হয় কত সালে?
১৮০০ সালে
১৮০১ সালে
১৮১৭ সালে
১৮৩১ সালে
#.ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ কবে খোলা হয়?
১৮০০ সালে
১৮০৪ সালে
১৮০১ সালে
১৮০৫ সালে
#.ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের শিক্ষক নয়?
উইলিয়াম কেরি
বিদ্যাসাগর
রামমোহন রায়
রামরাম বসু
হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল
হিন্দু কলেজ ও ইয়ংবেঙ্গল একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়) ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যা 1817 সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কলেজের কিছু শিক্ষার্থী, যাদের মধ্যে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর (Henry Louis Vivian Derozio) অনুসারীরা ছিলেন, "ইয়ং বেঙ্গল" নামে পরিচিত একটি আন্দোলনের জন্ম দেন। ডিরোজিও ছিলেন এই কলেজের একজন শিক্ষক এবং তিনি এই দলের নেতৃত্ব দেন। ইয়ং বেঙ্গল সদস্যরা যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং সামাজিক সংস্কারের পক্ষে ছিলেন এবং তারা প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিগুলির সমালোচনা করতেন।
হিন্দু কলেজ:
·
এটি 1817 সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।
·
শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য এই কলেজটি স্থাপন করা হয়েছিল।
·
এই কলেজের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতের আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটে।
ইয়ং বেঙ্গল:
·
এটি ছিল হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একটি দল, যারা ডিরোজিওর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।
·
এই দলের সদস্যরা যুক্তিবাদী, প্রগতিশীল এবং সংস্কারপন্থী ছিলেন।
·
তারা প্রচলিত ধর্ম, কুসংস্কার ও সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনা করতেন।
·
এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের কুসংস্কার দূর করা এবং যুক্তিনির্ভর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
সুতরাং, হিন্দু কলেজ ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের সূতিকাগার ছিল এবং এই কলেজের কিছু ছাত্রের মাধ্যমেই এই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল।
মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি
মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি একটি সামাজিক সংগঠন। ১৮৬৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফ কর্তৃক কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত। সোসাইটির সেক্রেটারি আবদুল লতিফের কলকাতার ১৬ নং তালতলার বাসভবনে সোসাইটির সদর দপ্তর ছিল। মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ রহিমুদ্দীন এবং সহ-সভাপতি ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা জাহান কাদের বাহাদুর ও মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার। কমিটির মোট ১২ জন সদস্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অযোধ্যার প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ বাহাদুর ও প্রিন্স মুহম্মদ জাহ আলী বাহাদুর এবং মহীশূরের প্রিন্স মুহম্মদ হরমুজ শাহ ও প্রিন্স মুহম্মদ বখতিয়ার শাহ। বাংলার ছোটলাটকে সোসাইটির পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছিল। সমগ্র ভারতবর্ষের পাঁচ শতেরও বেশি মুসলমান সোসাইটির সাধারণ সদস্যভুক্ত ছিল। সোসাইটির মাসিক সভার কার্যক্রম উর্দু, ফারসি, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় পরিচালিত হতো।
আবদুল লতিফ এর ভাষায় ‘মুসলমানদের ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং সামাজিক আচরণ ও আদান-প্রদানে শিক্ষিত হিন্দু ও ইংরেজদের সমকক্ষ করে তোলাই ছিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বিজ্ঞান, কলা ও চলমান সমস্যা সংক্রান্ত এবং মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করেন। সোসাইটি মুসলমানদের ক্ষয়িষ্ণু আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার দ্বারা সমাজ উন্নয়নের নতুন ধারার প্রবর্তনা এবং এভাবে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক নির্ভরশীল সেতু স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। মুসলমানদের এই ধরনের সর্বপ্রথম সংগঠন হিসেবে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি কালক্রমে মুসলমানদের প্রভূত কল্যাণ সাধন করে।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি বাঙালি মুসলমানদের একটি সাহিত্য সংগঠন। কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (১৮৯৩) অনুপ্রেরণায় কয়েকজন উদীয়মান মুসলিম লেখক ১৯১১ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা হলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী,
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক প্রমুখ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমিতির সম্পাদক মনোনীত হন। একটি পরিচালক পরিষদ দ্বারা সমিতি পরিচালিত হতো।
১৯১৭-১৮ সালে পরিচালক পরিষদের সভাপতি পদে ছিলেন আবদুল করিম,
সহসভাপতি খান বাহাদুর আহছানউল্লা ও মোহাম্মদ আকরাম খাঁ,
সম্পাদক মোজাম্মেল হক এবং ২৫জন সদস্য। বাংলা সাহিত্যচর্চা,
আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায় রচিত ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ প্রকাশ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পীর-দরবেশদের জীবনী রচনা, মুসলমান সাহিত্যিকদের উৎসাহ প্রদান, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ইত্যাদি সাহিত্য সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। বস্ত্তত আত্মপরিচয় ও নবজাগরণের স্পৃহা থেকেই এসব কর্মসূচি নির্ধারিত হয়।
সাহিত্য সমিতি বত্রিশ বছরের ইতিহাসে মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিকাশ সাধনের চেষ্টা করে। সমিতির মাসিক সভা ও বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। সমিতির উদ্যোগে মোট সাতটি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তারমধ্যে তৃতীয় সম্মেলন চট্টগ্রামে, চতুর্থ সম্মেলন বসিরহাটে এবং বাকিগুলি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনগুলি খুব গুরুত্ব ও আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্যাপিত হতো। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা (বৈশাখ ১৩২৫/ এপ্রিল ১৯১৮) ও সাহিত্যিক (অগ্রহায়ণ ১৩৩৩/ ডিসেম্বর ১৯২৬) নামে এর দুটি মুখপত্র ছিল।
সমিতির ত্রিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৪১ সালের ৫-৬ এপ্রিল কলকাতায় রজত জুবিলি পালিত হয়। এ.কে ফজলুল হক অধিবেশনের উদ্বোধন এবং কাজী নজরুল ইসলাম তাতে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২১ সালে সাহিত্যিক জীবনের শুরুতে নজরুল ইসলাম সাহিত্য সমিতির আশ্রয় লাভ করেছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখাও প্রকাশিত হয়।
১৯৪৩ সালের ৮-৯ মে সমিতির সপ্তম ও শেষ বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনকে কেন্দ্র করে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি (১৯৪২) এবং ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৪২) গঠিত হলে সাহিত্য সমিতির গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং সম্ভবত বিভাগপূর্বকালেই এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি দীর্ঘকাল স্থায়ী একটি মুসলিম সংগঠন। জাতির ক্রান্তিলগ্নে মুসলমান লেখকগণকে একটি ব্যানারে একত্রিত করা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমাজের মধ্যে জাতীয় জাগরণ ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করা ছিল এর একটি বড় অর্জন।
ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ
মুসলিম সাহিত্য সমাজ ছিল বাংলাদেশের একটি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের দল বা সংগঠন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] এটি ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান ঢাকা কলেজ) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ণধার ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন, কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হোসেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র ছিলো বার্ষিক প্রকাশিত শিখা পত্রিকা। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মাত্র এক দশক চলেছিল এই ঢাকা কেন্দ্রিক গোষ্ঠীটির কার্যক্রম।[১][২]
লক্ষ্য
[সম্পাদনা]
সে সময় অবিভক্ত বাংলার সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া অংশ ছিল পূর্ব বাংলা এবং যার প্রধান শহর ছিল ঢাকা। এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন ছিলেন মুসলমান যাদের সামগ্রিক সামাজিক পরিমণ্ডল ছিল শাস্ত্র ও সংস্কারের অচলায়তনে আবদ্ধ। কাজী মোতাহার হোসেনের দ্বিতীয় বর্ষের কার্য বিবরণীতে পাওয়া যায় :
“আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহজ সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে। এক কথা আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা বস্তু জগত ও ভাবজগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।” [২] মুসলিম সাহিত্য সমাজের লক্ষ্য ছিল ধর্ম ও ধর্ম প্রভাবিত মুসলমান সমাজকে বৈজ্ঞানিক যুক্তির পাটাতনের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে। মুসলিম সাহিত্য সমাজ করণীয় সম্পর্কে পাওয়া যায় :
“মুসলিম সমাজে অনেক গলদ ঢুকিয়াছে। মিথ্যা হাদিস দ্বারা ঐ সবের সমর্থন চলিতেছে; অনেক সময় লোকেরা নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্য হাদিস সৃষ্টি করিয়াছে; যে সমস্ত হাদিস বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত নহে তাহা মানিতে হইবে না; কুরআনের ব্যাখ্যা যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা ব্যতীত আর হইতে পারিবে না, ইহা ঠিক নহে; কাল ও অবস্থা ভেদে ইহার নতুন ব্যাখ্যা দিতে হইবে।”[৩]
পাঁচ দফা
[সম্পাদনা]
১৯২৯ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন শেষে গ্রহণ করা হয়েছিল সমাজ সংস্কারের পাঁচ দফা প্রস্তাব :
1.
এই সভা বাংলার মুসলমান নর-নারীকে বিশেষভাবে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত বাংগালীকে কোরানের সহিত পরিচিত হইবার অনুরোধ জানাইতেছে।
2.
এই সভা বাংলার পল্লীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবার জন্য দেশের কর্মীদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে।
3.
এই সভা বাংলার বিভিন্ন মক্তব ও মাদ্রাসায় যাহাতে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে।
4.
এই সভা বাংগালী মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দকে পর্দাপ্রথা দূরীকরণার্থে আদর্শ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।
5.
এই সভা সাহিত্য সমাজের কর্মীবৃন্দকে মুসলিম ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মবিষয়ক আরবী ও ফার্সি গ্রন্থ সমূহ অনুবাদ করিবার জন্য একটি অনুবাদ কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।[৩]
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.নিচের কোন ব্যক্তি ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না?
কাজী আব্দুল ওদুদ
এস ওয়াজেদ আলি
আবুল ফজল
আবদুল কাদির
#.'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়-
১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯২২
১৯ জানুয়ারী ১৯২৬
১৯ মার্চ ১৯২৬
২৬ মার্চ ১৯২৭
#.ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' -এর মুখপত্র ছিল কোন পত্রিকা?
সওগত
মোহাম্মদী
শিখা
মুসলিম ভারত
#.ঢাকার ' মুসলিম সাহিত্য সমাজ' -এর প্রতিষ্ঠা কোন খ্রিস্টাব্দে?
১৯২৬
১৯১১
১৮৬৪
১৯০৫
#.'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন----
কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন প্রমুখ
মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ
মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখ
কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলাদেশের একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পিছনে পৃথিবীবিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক জনাব আহমদ হাসান দানী মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যান্যরা হলেন: জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এ.বি.এম.হাবীবুল্লাহ, আব্দুল হালিম, এবং অনেকে। প্রতিষ্ঠাতারা চেয়েছিলেন এটি যেন বিশেষ করে এশিয়া বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে।[১]
ইতিহাস
[সম্পাদনা]
এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে গবেষণার জন্য ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি[২] তৎকালীন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোনস দি এশিয়াটিক সোসাইটি নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সার্বিকভাবে এশিয়া এবং বিশেষভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ওপর পদ্ধতিগত গবেষণা পরিচালনার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠার ধারণা দেন এবং প্রাচ্যবিদ্যা অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে একটি নিয়মিত সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য জোনসের প্রস্তাব ফোর্ট উইলিয়ামের অন্যান্য সহকর্মীর কাছ থেকে জোরালো সমর্থন লাভ করে। ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি সমমনা ৩০ জন ইউরোপীয় ব্যক্তিত্ব কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের গ্র্যান্ড জুরি কক্ষে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোনসের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয় দি এশিয়াটিক সোসাইটি এবং উইলিয়াম জোনস এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।[২]
১৮২৯ সালে রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেন প্রতিষ্ঠিত হয়। 'বোম্বে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে বোম্বেতে এর একটি শাখা ছিল। শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, টোকিও, আমেরিকা (ভিন্ন নামে ওরিয়েন্টাল একাডেমি) এবং পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় (১৯৫২ সালে)। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে এর পুনঃনামকরণ করা হয় বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।
বাংলা একাডেমি
বাংলা একাডেমি হল বাংলাদেশের ভাষানিয়ন্ত্রক সংস্থা। এটি ১৯৫৫ সালের ৩রা ডিসেম্বর (১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা, গবেষণা ও প্রচারের লক্ষ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) এই একাডেমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন-পরবর্তী প্রেক্ষাপটে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন বর্ধমান হাউজে এই একাডেমির সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। একাডেমির বর্ধমান হাউজে একটি “ভাষা আন্দোলন জাদুঘর” আছে।
ইতিহাস
[সম্পাদনা]
বশীর আল-হেলালের মতে, বাংলা একাডেমির মতো প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও সংগঠনের চিন্তা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম করেন।[২] ড. শহীদুল্লাহ ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ এ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে ভাষা সংক্রান্ত একটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার দাবি করেন।[৩] এছাড়া দৈনিক আজাদ পত্রিকা বাংলা একাডেমি গঠনে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ১৯৫২ সালের ২৯ এপ্রিল পত্রিকাটি "বাংলা একাডেমী" প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে এ প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে সময় কিছু প্রচেষ্টা নেয়।[৩][৪] ১৯৫৪ সালে এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অর্থাভাবে প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হলে শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আজিজুল হক নির্দেশ দেন,[৪]
প্রধানমন্ত্রী বর্ধমান হাউজের বদলে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউজকে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।
অবশেষে ১৯৫৫ সালে ৩ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার উদ্বোধন করেন "বাংলা একাডেমি"। বাংলা একাডেমির প্রথম সচিব মুহম্মদ বরকতুল্লাহ। তার পদবি ছিল "স্পেশাল অফিসার"।[৩] ১৯৫৬ সালে একাডেমির প্রথম পরিচালক নিযুক্ত হন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক। বাংলা একাডেমির প্রথম প্রকাশিত বই আহমদ শরীফ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লায়লী-মজনু। স্বাধীনতার পর থেকে একাডেমি চত্বরে স্বল্প পরিসরে বইমেলা শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সাল থেকে বড়ো আকার ধারণ করে।[৪] ২০০৯-২০১১ খ্রিষ্টাব্দে একাডেমির বর্ধমান হাউজ ভবনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় ভাষা আন্দোলন জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.বাংলা একাডেমি মূল ভবনের নাম কি ছিল?
বর্ধমান হাউজ
বাংলা ভবন
আহসান মঞ্জিল
চামেলি হাউজ
#.বাংলা একাডেমি কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৯৫৫ খ্রি
১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
১৯৫২ খ্রি
১৩৫২ বঙ্গাব্দ
#.বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
১৯৫৫
১৮৫৫
১৯৪৫
১৭৫৫
#.কোন বিষয়ের উপর বাংলা একাডেমী প্রতি বছর পুরষ্কার প্রদান করে ?
শিক্ষা
সাংবাদিকতা
সাহিত্য
শিল্পকলা
#.বাংলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
১৯৪৭
১৯৪৮
১৯৫৩
১৯৫৫
১৯৭২