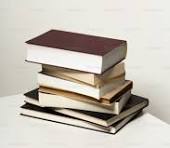বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ( ১২০১-১৮০০ খ্রি)
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ( ১২০১-১৮০০ খ্রি)
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত সময় মধ্যযুগ বলে চিহ্নিত। এর মধ্যে ১২০০ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত দেড় শ বছরকে কেউ কেউ অন্ধকার যুগ বা তামস যুগ বলে অভিহিত করেছেন। বাংলাদেশে তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমান শাসনামলের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি অনুমান করে এ রকম সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলার সেন বংশের শাসক অশীতিপর বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া বিনা বাধায় জয় করে এদেশে মুসলমান শাসনের সূত্রপাত করেন। ১৩৪২ সালে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসন দখল করে দিল্লির শাসনমুক্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পুত্র সেকান্দর শাহের আমলে বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাব হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কোন কবির মৃত্যুর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সমাপ্তি ঘটে?
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী
নারায়ন সেন
মানিক দত্ত
#.‘আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে’। এই মনোবাঞ্জাটি কার?
ভবানন্দের
ভাঁড়ুদত্তের
ইশ্বরী পাটনীর
ফুল্লারার
#.বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?
মারাঠি
হিন্দি
মৈথিলি
গুজরাটি
#.‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?
নেপালের রাজদরবার থেকে
গোয়ালঘর থেকে
পাঠশালা থেকে
কান্তজীর মন্দির থেকে
#.‘চন্ডীমঙ্গল’ কাব্যের উপাস্য 'চন্ডী' কার স্ত্রী?
জগন্নাথ
বিষ্ণ
প্রজাপতি
শিব
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য
'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্যযুগের প্রথম কাব্য এবং বড়ু চণ্ডীদাস মধ্যযুগের আদি কবি। ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের কৃষ্ণলীলা-সম্পর্কিত কাহিনি অনুসরণে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের প্রভাব স্বীকার করে, লোকসমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ প্রেম-সম্পর্কিত গ্রাম্য গল্প অবলম্বনে কবি বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচনা করেন। ১৯০৯ সালে (১৩১৬ বঙ্গাব্দ) বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ির গোয়ালঘর থেকে পুঁথি আকারে অযত্নে রক্ষিত এ কাব্য আবিষ্কার করে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটান। বৈষ্ণব মহান্ত শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র-বংশজাত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অধিকারে এই গ্রন্থটি রক্ষিত ছিল। ১৯১৬ সালে (১৩২৩ সনে) বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।
পুঁথিটির প্রথম দিকের দুটি পাতা এবং শেষের পাতাটি ছিল না। এ ছাড়া পুঁথির মধ্যেও কিছু পাতা নেই। রীতি অনুযায়ী পুঁথির প্রথম দিকে দেবতার প্রশংসা, কবির পরিচয় ও গ্রন্থনাম উল্লেখিত হয় এবং শেষ দিকের পাতায় পুঁথির রচনাকাল ও লিপিকাল লিখিত থাকে। প্রথম ও শেষ অংশ খণ্ডিত থাকায় কবির আত্মপরিচয় ও রচনাকালের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লোকচক্ষুর আড়ালেই রয়ে গেছে।
বৈষ্ণব মতবাদে গৃহীত রাধাকৃষ্ণের রূপকের বাইরে এ কাব্যের পরিচয়। বৈষ্ণব সাধনা ও ঐতিহ্যের বিরোধী এ কাব্য রুচিহীন গ্রাম্যতা, যৌনকামনা ও মিলনের বর্ণনায় অশ্লীল, সূক্ষ্ম ইন্দ্ৰিয়াতীত অনুভূতির ব্যঞ্জনার অভাব এ কাব্যকে করে তুলেছে বিতর্ক মুখর। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে কাব্যটি অচিরেই ব্যাপক কৌতূহলের সৃষ্টি করে ।
বাংলা সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্থানটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই কাব্যের মূল্য অসাধারণ বলে গ্রহণযোগ্য। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে প্রাচীন যুগের নিদর্শন চর্যাপদের পর এবং মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মাঝামাঝি সময়ে আর কোন বাংলা কাব্য আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সমকালে বা কিছু পরে রচিত বিদ্যাপতির পদাবলি, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ইত্যাদি কাব্যের প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নি। এ সবের ভাষা যুগের পরিবর্তনে অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয়ে পড়েছে। পরবর্তী বৈষ্ণব ভাবধারা ও রসপর্যায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শগত বিরোধ বিদ্যমান থাকায় কাব্যটি লোকসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। ফলে এর ভাষায় পরিবর্তন ঘটতে পারে নি।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কোনটি ‘শ্রীকৃ্ষ্ণকীর্তন’ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়?
বান খন্ড
তাম্বুল খন্ড
কালিদাস খন্ড
নৌকা খন্ড
#.‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ এর রচয়িতা কে?
জ্ঞানদাস
দীন চন্ডিদাস
বড়ু চন্ডীদাস
দীনহীন চন্ডিদাস
#.‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’ কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?
নেপালের রাজদরবার থেকে
গোয়ালঘর থেকে
পাঠশালা থেকে
কান্তজীর মন্দির থেকে
#.‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের রচয়িতা-
বড়ু চন্ডীদাস
দ্বিজ চন্ডীদাস
শ্রী চৈতন্যদেব
কাহ্নপা
#.শ্রীকৃষ্নকীর্তন কাব্যের সম্পাদক-
বসন্তরঞ্জন
বড়ৃ চন্ডীদাস
ত্রৈলোক্য আচর্য
ব্রজসুন্দর সান্ন্যাস
বৈষ্ণব সাহিত্য/পদাবলি
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম গৌরব বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্য। রাধা- কৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে এই অমর কবিতাবলির সৃষ্টি এবং বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদের প্রচারিত বৈষ্ণব মতবাদের সম্প্রসারণে এর ব্যাপক বিকাশ। জয়দেব-বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বৈষ্ণব গীতিকবিতার ধারা প্রবাহিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ষোল-সতের শতকে এই সৃষ্টিসম্ভার প্রাচুর্য ও উৎকর্ষপূর্ণ ছিল। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল বৈষ্ণব পদাবলি ।
পদাবলি সাহিত্য বৈষ্ণবতত্ত্বের রসভাষ্য। বৈষ্ণব পদাবলি বৈষ্ণবসমাজে মহাজন পদাবলি এবং বৈষ্ণব পদকর্তাগণ মহাজন নামে পরিচিত। বৈষ্ণবমতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিদ্যমান। এই প্রেম সম্পর্ককে বৈষ্ণব মতাবলম্বীগণ রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার রূপকের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। রাধা ও শ্রীকৃষ্ণের রূপাশ্রয়ে ভক্ত ও ভগবানের নিত্যবিরহ ও নিত্যমিলনের অপরূপ আধ্যাত্মিক লীলা কীর্তিত হয়েছে। বৈষ্ণবদের উপাস্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আনন্দময় তথা প্রেমময় প্রকাশ ঘটেছে রাধার মাধ্যমে । রাধা মানবী নয়, শ্রীকৃষ্ণরূপ পূর্ণ ভগবৎ-তত্ত্বের অংশ। ভগবানের লীলা চলে। তাঁর স্বরূপভূতা শক্তি রাধার সঙ্গে। বৈষ্ণবেরা ভগবান ও ভক্তের সম্পর্কের স্বরূপ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণকে পরামাত্মা বা ভগবান এবং রাধাকে জীবাত্মা বা সৃষ্টির রূপক মনে করে তাঁদের বিচিত্র প্রেমলীলার মধ্যেই ধর্মীয় তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন। ফলে “এক প্রাচীন গোপজাতির লোকগাথার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ এবং মহাভারতের নায়ক অবতার কৃষ্ণ কালে লোকস্মৃতিতে অভিন্ন হয়ে উঠেন। গোপী-প্রধানা রাধার সঙ্গে তাঁর প্রণয়ই জীবাত্মা-পরমাত্মার প্রণয়লীলার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে ধর্ম-দর্শনের ও সাধন-ভজনের অবলম্বন হয়েছে।' নীলরতন সেন মন্তব্য করেছেন, 'পদাবলির কাহিনি, তথ্য উপকরণ এবং ভক্তি-ভাবাশ্রিত সৌন্দর্য চিত্রায়ণে বৈষ্ণব কবিরা উপনিষদ, হালের গাথাসপ্তশতী, আভীর ও অন্যান্য জাতির মৌলিক প্রেমগাথা, ভাগবতসহ বিবিধ পুরাণ, বাৎসায়নের কামসূত্র, অমরুশতক, আনন্দবর্ধনের ধ্বন্যালোক, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, সদুক্তিকর্ণামৃত, সুভাষিতাবলী, সূক্তিমুক্তাবলী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ, লোকধর্ম ও
প্রেমগীতিকে আশ্রয় করে ভারতের পূর্বাচার্যদের অনুসৃত পথেই অগ্রসর হয়েছেন। চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) যুগান্তকারী আবির্ভাবের পূর্বেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম- লীলার মাধুর্য পদাবলিগানের উপজীব্য হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে নব্য মানবীয় প্রেমভক্তিধারার বিকাশ ঘটে তা অবলম্বনেই বিপুল ঐশ্বর্যময় পদাবলি। সাহিত্যের সার্থকতর রূপায়ণ সম্ভবপর হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে কৃষ্ণলীলা। বিষয়ক গানে ভক্তিরসের রং লাগলেও তা থেকে আদিরসের ক্লেদ দূর হয়ে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা ভক্তহৃদয়ের প্রতিফলন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.শৃঙ্গার রসকে বৈষ্ণব পদাবলিতে কি রস বলে?
ভাব রস
লীলা রস
প্রেম রস
মধুর রস
#.“ সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল” এই বৈষ্ণবপদের রচিয়তা কে?
জ্ঞানদাস
চন্ডীদাস
গোবিন্দ দাস
দ্বিজ চন্ডীদাস
#.বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে কোন ভাষা সম্পর্কিত?
সন্ধ্যাভাষা
অধিভাষা
ব্রজবুলি
সংস্কৃত ভাষা
#.বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা কে?
শ্রী চৈতন্য
বিদ্যাপতি
চণ্ডীদাস
জ্ঞানদাস
#.বৈষ্ণব পদকর্তা “চন্ডীদাস” কত জন?
৩ জন
২ জন
৪ জন
৫ জন
মঙ্গলকাব্য
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান কাব্য 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত। এগুলো খ্রিস্টীয় পনের শতকের শেষ ভাগ থেকে আঠার শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত পৌরাণিক, লৌকিক ও পৌরাণিক-লৌকিক সংমিশ্রিত দেবদেবীর লীলামাহাত্ম্য, পূজাপ্রচার ও ভক্তকাহিনি অবলম্বনে রচিত সম্প্রদায়গত প্রচারধর্মী আখ্যানমূলক কাব্য। বলা হয়ে থাকে, যে কাব্যে দেবতার আরাধনা, মাহাত্ম্য-কীর্তন করা হয়, যে কাব্য শ্রবণেও মঙ্গল হয় এবং বিপরীতটিতে হয় অমঙ্গল; যে কারা মঙ্গলাধার, এমন কি, যে কাব্য যার ঘরে রাখলেও মঙ্গল হয়—তাকেই বলা হয়। মঙ্গলকাব্য। 'মঙ্গল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'কল্যাণ'। যে কাব্যের কাহিনি শ্রবণ করলে সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় এবং পূর্ণাঙ্গ মঙ্গল লাভ ঘটে, তাকেই মঙ্গলকাব্য বলা যায়। মঙ্গলকাব্যের 'মঙ্গল' শব্দটির সঙ্গে শুভ ও কল্যাণের অর্থসাদৃশ্য থাকা ছাড়াও এসব কাব্যের অনেকগুলো এক মঙ্গলবারে পাঠ আরম্ভ হয়ে পরের মঙ্গলবারে সমাপ্ত হত বলে এ নামে অভিহিত হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর গুণগান মঙ্গলকাব্যগুলোর উপজীব্য। তন্মধ্যে স্ত্রীদেবতাদের প্রাধান্যই বেশি এবং মনসা ও চণ্ডীই এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লৌকিক দেবদেবীর কাহিনি অবলম্বনে রচিত মঙ্গলকাব্যগুলোতে ক. বন্দনা, খ. গ্রন্থ রচনার কারণবর্ণনা, গ. দেবখণ্ড ও ঘ. নরখণ্ড বা মূলকাহিনি বর্ণনা—মোটামুটি এই চারটি অংশ থাকত। বারমাসী' ও 'চৌতিশা' জাতীয় কাব্যাংশ মঙ্গলকাব্যে স্থান লাভ করত। কবি কাব্যে নিজের পরিচয়ও উল্লেখ করতেন।
মঙ্গলকাব্য প্রধানত কাহিনিকেন্দ্রিক। মূল কাহিনির সঙ্গে দেবলীলা, ধর্মতত্ত্ব ও নানা ধরনের বর্ণনায় এসব কাব্য বিপুলায়তন লাভ করেছে। কেউ কেউ মঙ্গলকাব্যকে সংস্কৃত পুরাণের শেষ বংশধর বলতে চান, কেউবা তাকে মহাকাব্য বলেছেন, কেউ মঙ্গলকাব্যকে ধর্মগ্রন্থ বলে ভক্তি করেন, আবার কেউবা এ ধরনের সাহিত্যসৃষ্টি থেকে বাংলার তৎকালীন যথার্থ ঐতিহাসিক স্বরূপ সন্ধান করতে আগ্রহশীল। তবে মঙ্গলকাব্য যে একটি মিশ্র শিল্প তাতে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত পুরাণের সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্যগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পুরাণে যেমন দেবমাহাত্ম্য বা রাজবংশের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, মঙ্গলকাব্যের সীমাবদ্ধ পরিসরে প্রায় অনুরূপ ব্যাপার আংশিক ভাবে সমাধা হয়েছে বলে লক্ষ করা যায়। তবে মঙ্গলকাব্যে সংস্কৃত পুরাণের আদর্শ কিছুটা ছায়াপাত করলেও তাকে পুরোপুরি পুরাণ বলা যায় না। লৌকিক ও পৌরাণিক আদর্শ-মিশ্রিত লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারক এবং ভক্তের গৌরববাচক এই মঙ্গলকাব্যগুলো আখ্যানকেন্দ্রিক ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে গৃহীত হতে পারে। মঙ্গলকাব্যে লৌকিক গ্রামীণ সংস্কার, আর্যেতর দেববিশ্বাস এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কার ও চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে সমন্বয় লাভ করে। মঙ্গলকাব্যে সাম্প্রদায়িক দেবকাহিনি সর্বজনীন মানবিক সংবেদনাপূর্ণ সাহিত্যরূপে নবজন্ম লাভ করেছিল। গোষ্ঠিগত সাধনায় মঙ্গলকাব্যের শিল্পধর্মী অভিব্যক্তি ঘটেছিল। সৃষ্টির পটভূমি ও স্রষ্টা—উভয়পক্ষের বিচারেই মঙ্গলকাব্যকে যৌথ শিল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায় । সে আমলে কবিরা নিত্যনতুন কাহিনি রচনার পথ পরিহার করেছিলেন। তখন হয়ত নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অভাব ছিল। কবিদের প্রতিভার গুণেই কাব্যগুলো বৈচিত্র্যহীন অনুকরণমাত্র না হয়ে শিল্পসম্মত যুগজীবনবাণী রূপে প্রতিভাত হয়েছে।
মঙ্গলকাব্যের উন্মেষ পর্যায়ে পনের শতকে রচনারীতি গতানুগতিক ছিল। তখন বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ছিল বৈশিষ্ট্যবর্জিত। নায়ক স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু তাকে অভিশাপগ্রস্ত হয়ে কোন দেবতার পূজাপ্রচারের জন্য মানবীর গর্ভে পৃথিবীতে জন্ম নিতে হত। পূজাপ্রচারের বিপদসঙ্কুল পথে মঙ্গলকারী দেবতা তার রক্ষক। ষোল শতকের পরবর্তী কাব্যগুলোতে বিষয়বস্তুগত কোন অভিনবত্ব নেই, কেবল চরিত্রগুলোর মার্জিত রসরূপ দান করা হয়েছে। এর সঙ্গে নানা উপকরণের সংযোগে মঙ্গলকাব্যগুলোর যে কাহিনিগত কাঠামো দাঁড়িয়েছে তাতে আছে : প্রথমেই পঞ্চদেবতার বন্দনা, তারপর গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বর্ণনা, সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা, মনুর প্রজাসৃষ্টি, প্রজাপতির শিবহীন যজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, উমার তপস্যা, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, গৌরীর বিয়ে, কৈলাসে হরগৌরীর কোন্দল, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, পার্বতী-চণ্ডী বা শিবের সম্পর্কিত অন্য কেউ যেমন মনসা প্রভৃতির নিজেদের পূজাপ্রচারের চেষ্টা, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে পূজাপ্রচার, স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশুর স্বর্গে প্রত্যাবর্তন প্রভৃতির বৈচিত্র্যহীন বর্ণনা। তাছাড়া বারমাসী, নারীগণের পতিনিন্দা, চৌতিশা বা বর্ণানুক্রমিক চৌত্রিশ অক্ষরে দেবতার স্তব প্রভৃতিও মঙ্গলকাব্যের অঙ্গ হয়ে আছে।
বাংলা সাহিত্যের নানা শ্রেণির কাব্যে মঙ্গল কথাটির প্রয়োগ থাকলেও কেবল বাংলা লৌকিক দেবতাদের নিয়ে রচিত কাব্যই 'মঙ্গলকাব্য' নামে অভিহিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের চৈতন্যমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গল নামধেয় কাব্যের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের কোন যোগসূত্র নেই। প্রকৃতপক্ষে মঙ্গলকাব্যগুলোকে শ্রেণিগত দিক থেকে পৌরাণিক ও লৌকিক এই দু ভাগে ভাগ করা যায়। পৌরাণিক শ্রেণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি । লৌকিক শ্রেণি হল : শিবায়ন বা শিবমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল (বা বিদ্যাসুন্দর), শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।
মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তির উৎস এদেশের সুপ্রাচীন ধর্মাদর্শের সঙ্গে বিজড়িত। বাংলাদেশে আর্য আগমনের পূর্বে এখানকার আদিম জনগণ নিজস্ব ধর্মাদর্শ ও দেবদেবীগণের পরিকল্পনার অনুসারী ছিল। পরবর্তী কালে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মাধ্যমে আর্যদের সঙ্গে অনার্যদের সংস্পর্শ ঘটার ফলে তাদের আদিম দেবপরিকল্পনা ও ধর্মসংস্কার পরিবর্তিত হয়েছে। তবে তারা তাদের নিজস্ব আদর্শানুসারে নিজ নিজ লৌকিক দেবতাদের পূজাপদ্ধতি ও মহিমাজ্ঞাপক কাহিনি নিয়ে পাঁচালি রচনা করেছে। এগুলোই পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্যের আকার পেয়েছে।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.মঙ্গলকাব্যের শেষ কবি -
দ্বিজ বংশীদাস
চন্দ্রাবর্তী
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
কানাহরি দত্ত
#.‘ফুল্লাবার বারমাস্যা’ কোন মঙ্গলকাব্যের অন্তগর্ত?
মনসামঙ্গল
চন্ডীমঙ্গল
অন্নদাসমঙ্গল
ধর্ম মঙ্গল
#.'মঙ্গলকাব্য' -এ ধর্মীয় আরাধনা মূখ্য হলে ও এর অন্যতম সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো -
ব্যক্তির মুক্তি
সামাজিক মিথস্ক্রিয়া
অন্ত্যেবাসী মানুষ
শ্রেণিদ্বন্দ্ব
#.'বেগুলা - লখিন্দরের' কাহিনী পাওয়া যায় কোন মঙ্গলকাব্যে?
মনসাঙ্গল
অন্নদামঙ্গল
শীতলামঙ্গল
সারদামঙ্গল
#.’বেহুলা’ চরিত্রটি কোন মঙ্গলকাব্যের সম্পদ?
অন্নদামঙ্গল
ধর্মমঙ্গল
চন্ডীমঙ্গল
মনসামঙ্গল
জীবনী সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের গতানুগতিক ধারায় জীবনী সাহিত্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের জীবনকাহিনি অবলম্বনে। এই জীবনী সাহিত্যের সৃষ্টি। তবে এর মধ্যে চৈতন্য জীবনীই প্রধান। চৈতন্যদের জীবিতকালেই কারও কারও কাছে অবতাররূপে পূজিত হন। তাঁর শেষজীবন দিব্যোন্মাদ রূপে অতিবাহিত হয়েছে বলে তাঁর পক্ষে ধর্মমত প্রচার করা সম্ভব হয় নি। তাঁর শিষ্যরা এ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকাহিনি আলোচনা করতেন। চৈতন্যের জীবদ্দশায়ই সংস্কৃত শ্লোকে, কাব্যে ও নাটকে এবং বাংলা গানে ও কাব্যে তাঁর চরিতকথা স্থান পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জীবনী সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচুর্য এসে বাংলা সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য এনেছে। বৈষ্ণব জীবনী সাহিত্যেই রক্ত-মাংসের মানুষ সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে একক প্রসঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করল। চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলোর সমবেত উপাদান থেকে শ্রীচৈতন্যের নরলীলার দেশ-কাল-চিহ্নিত বিশেষিত স্বভাবের একটি নির্ভরযোগ্য মোটামুটি কাঠামো আবিষ্কার করা সম্ভব ।
আধুনিক জীবনী সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের জীবনী সাহিত্যের পার্থক্য সম্পর্কে অধ্যাপক আহমদ কবির মন্তব্য করেছেন, ‘একালের জীবনীগ্রন্থ বলতে আমরা যা বুঝি, বৈষ্ণব চরিতকাব্যগুলো সেরকম নয়। জীবনচরিতে বাস্তব মানুষের জীবনালেখ্য, কর্ম, কীর্তি ও আদর্শের পরিচয় থাকে, আর থাকে তাঁর দেশকালের ছবি। যে-মানুষ তাঁর কর্ম ও আদর্শের প্রেরণায় বহু মানুষকে প্রভাবিত করেছেন, সে মানুষেরই জীবনী রচিত হয়। ভক্ত ও অনুরাগীরাই এ-জীবনী লিখে থাকেন। এভাবে জীবনী রচিত হয়েছে ধর্মগুরু, দার্শনিক, লেখক, কবি, বিজ্ঞানী, রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, ত্যাগী মানবদরদী কীর্তিধন্যদের। এঁরা অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব— এঁদের গুণমাহাত্ম্য ও মহিমা অপরকে প্রভাবিত করে। অবশ্য ব্যক্তি দোষেগুণে মানুষ। শুধু গুণের আদরে ব্যক্তিকে ভূষিত করলে ব্যক্তির পূর্ণ ছবি পাওয়া যায় না। ভক্তের লেখায় ব্যক্তির দোষ সাধারণত পরিত্যাজ্য। তবু একালের জীবনীগ্রন্থ অনেকাংশে বস্তুনিষ্ঠ। সন্দেহ নেই যে, একালে মানুষের ভক্তিনিষ্ঠাও অনেক কমেছে এবং মানুষ ক্রমশ বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে। তাছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তিদের জীবনসম্পর্কিত তথ্যাদি ও বিবরণ পাওয়ার সুবিধাও হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের খবর, ব্যক্তিগত ডায়েরি, আত্মজীবনী, ঘনিষ্ঠজনের স্মৃতিকথা, ক্যাসেট, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিডিও চিত্র ফিল্ম ইত্যাদি একজন লোকমান্য ব্যক্তির জীবনী-প্রণয়নে সহায়তাদান করে। এভাবে গড়ে ওঠে একটি তথ্যনিষ্ঠ সত্য জীবনকাহিনি। একালের জীবনচরিত রক্তমাংসের বাস্তব মানুষেরই বাস্তব জীবনালেখ্য।
ধর্মীয় বিষয় অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য। চৈতন্য জীবনী সাহিত্যও এই বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নয়। কারণ চৈতন্যদেবকে অনেকেই অবতার হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন এবং তাঁকে অবলম্বন করে রচিত কাব্য ভক্তিকাব্য হয়ে পড়েছে। ভক্তেরা চৈতন্যদেবকে মানুষরূপে কল্পনা করেন নি, করেছেন নররূপী নারায়ণরূপে। ফলে জীবনীগ্রন্থ হয়েছে দেব-অবতারের মঙ্গলপাঁচালী। তবে কৃষ্ণলীলার আদলে নরনারায়ণের জীবনলীলা বর্ণনা কালে কবিরা নিজেদের দেশ-কাল-পরিবেশ উপেক্ষা করতে পারেন নি। ড. আহমদ শরীফের মতে, জীবনী সাহিত্য 'ষোল শতকের শাস্ত্রিক সামাজিক ভৌগোলিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িক, প্রশাসনিক, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের সংবাদ-চিত্র বহন করেছে। চরিতাখ্যানগুলির সর্বাধিক গুরুত্ব এখানেই।' জীবনী কাব্যগুলো যে সামাজিক ইতিহাস হিসেবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ নেই।
চৈতন্য জীবনের কাহিনিতে কবিরা অলৌকিকতা আরোপ করেছেন। তবু চৈতন্য ও তাঁর শিষ্যরা বাস্তব মানুষ ছিলেন এবং এ ধরনের বাস্তব কাহিনি নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। এ পর্যন্ত রচিত বাংলা সাহিত্যের বিষয় ছিল পৌরাণিক গল্প, দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনি ও রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদাবলি। কিন্তু জীবনী সাহিত্যে সমকালীন ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তব মানুষের জীবনকাহিনি সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। চৈতন্য জীবনী সাহিত্য সম্পর্কে ড. অসিতকুমার বন্ধ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, ইহাতে একজন মহাপুরুষের ভাবজীবনের গভীর ব্যাকুলতা, তাঁহার সর্বত্যাগী পার্ষদগণের পূত জীবনকথা, ভক্তিদর্শন ও বৈষ্ণবতত্ত্বের নিগূঢ় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, বৈষ্ণবসমাজ ও বৈষ্ণবসমাজের বাহিরে বৃহত্তর বাঙালি হিন্দুসমাজ, হিন্দু মুসলমানের সম্পর্ক প্রভৃতি বিবিধ তথ্য সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই এই জীবনীকাব্যগুলি শুধু জীবনী মাত্র হয় নাই, – ইহাতে গৌড় বিশেষত নবদ্বীপ, শান্তিপুর, খড়দহ, নীলাচল ও ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস, বিকাশ, পরিণতি প্রভৃতি ব্যাপারে ঐতিহাসিক তথ্যের যে প্রকার বাহুল্য দেখা যায়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাহার মূল্য বিশেষভাবে স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে গেলে চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির সাহায্য অপরিহার্য।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক প্রথম কাহিনী কাব্য কে রচনা করেন?
বৃন্দাবন দাস
লোচন দাস
জয়ানন্দ
পরাগল খাঁ
বাংলা জীবনী সাহিত্য
#.চৈতন্য জীবনী কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?
কৃষ্ণদাস কবারাজ
জয়ানন্দ
বৃন্দাবন দাস
কবি কর্ণপুর পরামানন্দ
#.জীবনী সাহিত্যের ধারা গড়ে ওঠে কাকে কেন্দ্র করে?
শ্রীচৈতন্যদেব
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
বিদ্যাপতি
কাহ্নপা
অনুবাদ সাহিত্য
সকল সাহিত্যের পরিপুষ্টিসাধনে অনুবাদমূলক সাহিত্যকর্মের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। সমৃদ্ধতর নানা ভাষা থেকে বিচিত্র নতুন ভাব ও তথ্য সঞ্চয় করে নিজ নিজ ভাষার বহন ও সহন ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলাই অনুবাদ সাহিত্যের প্রাথমিক প্রবণতা। ভাষার মান বাড়ানোর জন্য ভাষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হয়, আর তাতে সহায়তা করে অনুবাদকর্ম। উন্নত সাহিত্য থেকে ঋণ গ্রহণ করা কখনও অযৌক্তিক বিবেচিত হয় নি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার সীমিত শব্দাবলিতে কোন বিশেষ ধ্যানধারণা তত্ত্ব-তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। উন্নত ও সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্যের সান্নিধ্যে এলে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিশব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়, অন্য ভাষা থেকে প্রয়োজনীয় শব্দও গ্রহণ করা যায়। অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের বক্তব্য আয়ত্তে আসে। ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পদশাহী ভাষায় উৎকর্ষপূর্ণ সাহিত্যসৃষ্টির অনুবাদ একটি আবশ্যিক উপাদান । নতুন বিকাশমান ভাষার পক্ষে অনুবাদ 'আত্মোন্নতি সাধনের এক অপরিহার্য পন্থা ।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে অনুবাদ সাহিত্যের চর্চা হয়েছিল এবং পরিণামে এ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য। সত্যিকার সার্থক সাহিত্য অনুবাদের মাধ্যমে সৃষ্টি করার বিস্তর বাধা থাকলেও ভাষা সাহিত্যের গঠনযুগে অনুবাদের বিশেষ প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাই ড. দীনেশ সেন। মন্তব্য করেছেন, “ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিতে প্রথমত অনুবাদ গ্রন্থেরই আবশ্যক।' অনুবাদমূলক সাহিত্যসৃষ্টি ভিত্তি করেই মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হয়ে থাকে । আবার এ ধরনের রচনা সাহিত্যকে সম্প্রসারিত হতে সাহায্য করে। শ্রেষ্ঠ ভাষা থেকে সাহিত্যিক অনুবাদের মাধ্যমে নতুন ভাষা কেবল সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার ও দক্ষ প্রকাশরীতিই আয়ত্ত করে না, শ্রেষ্ঠতর ভাবকল্পনার সঙ্গেও পরিচিত ও অন্বিত হতে পারে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ শাখার ভূমিকা থেকে এ কথার তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করা যায় ।
জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়ের বেলায় শুদ্ধ অনুবাদ অভিপ্রেত। কিন্তু সাহিত্যের অনুবাদ শিল্পসম্মত হওয়া আবশ্যিক বলেই তা আক্ষরিক হলে চলে না। ভিন্ন ভাষার শব্দ সম্পদের পরিমাণ, প্রকাশক্ষমতা ও বাগভঙ্গি অনুযায়ী ভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত কথায় সংকোচন, প্রসারণ, বর্জন ও সংযোজন আবশ্যিক হয়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে অনুবাদের ধারাটি সমৃদ্ধি লাভ করে তাতে সৃজনশীল লেখকের প্রতিভা কাজ করেছিল। সে কারণে মধ্যযুগের এই অনুবাদকর্ম সাহিত্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় কে অনুবাদ করেন?
মুনিদত্ত
প্রবোধচন্দ্র বাগচী
কীর্তিচন্দ্ৰ
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
#.বাংলা সাহিত্যের কোন যুগে কবিরা অনুবাদ সাহিত্যে হাত দেন?
প্রাচীন যুগে
মধ্যযুগে
আধুনিক যুগের প্রারম্ভে
আধুনিক যুগের মধ্যযুগে
কোনটিই নয়
#.বাংলা সাহিত্যের কোন যুগে কবিরা অনুবাদ সাহিত্যে হাত দেন?
প্রাচীন যুগে
মধ্য যুগে
আধুনিক যুগের প্রারম্ভে
আধুনিক যুগের মধ্যভাগে
কোনোটিই নয়
#.বাংলায় প্রথম পবিত্র কোরনের অনুবাদক-
মীর মোশাররফ হোসেন
মাওলানা আকরাম খান
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
গিরিশচন্দ্র সেন
#.সংস্কৃত রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করেন-
নলিনীকান্ত ভট্টশালী
কাশীরাম দাস
মালাধর বসু
কৃত্তিবাস ওঝা
রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান
বাংলাদেশে মুসলমান আগমনের ফল ছিল দু ধরনের—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। তের শতকের মুসলমান শাসনের সূত্রপাতের পরিপ্রেক্ষিতে অবহেলিত বাংলা সাহিত্য তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে প্রাণচাঞ্চল্য লাভ করেছিল তা হল পরোক্ষ ফল। আবার মুসলমান কবিরা পনের-ষোল শতকে রোমান্টিক প্রণয়কাব্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রত্যক্ষ অবদান সৃষ্টিতে সক্ষম হন। বাংলা সাহিত্যে মুসলমান শাসকগণের উদার পৃষ্ঠপোষকতায় যে নবজীবনের সূচনা হয়েছিল সে সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মন্তব্য করেছেন, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে বাংলার মুসলমানদের যতখানি হাত রহিয়াছে, হিন্দুদের ততখানি নহে। এদেশের হিন্দুগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্মদাতা বটে; কিন্তু তাহার আশৈশব লালন পালন ও রক্ষাকর্তা বাংলার মুসলমান। স্বীকার করি, মুসলমান না হইলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মনোরম বনফুলের ন্যায় পল্লীর কৃষককণ্ঠেই ফুটিয়া উঠিত ও বিলীন হইত, কিন্তু তাহা জগতকে মুগ্ধ করিবার জন্য উপবনের মুখ দেখিতে পাইত না, বা ভদ্র সমাজে সমাদৃত হইত না।' পরোক্ষ এই প্রভাবের সঙ্গে মধ্যযুগে মুসলমান কবিগণ মানবিক গুণসম্পন্ন রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করে প্রত্যক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে অনন্য ভূমিকা রেখে গেছেন।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলমান কবিগণের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান এই রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান বা প্রণয়কাহিনি। এই শ্রেণির কাব্য মধ্যযুগের সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান জুড়ে আছে। ফারসি বা হিন্দি সাহিত্যের উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত অনুবাদমূলক প্রণয় কাব্যগুলোতে প্রথমবারের মত মানবীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যযুগের কাব্যের ইতিহাসে ধর্মীয় বিষয়বস্তুর আধিপত্য ছিল, কোথাও কোথাও লৌকিক ও সামাজিক জীবনের ছায়াপাত ঘটলেও দেবদেবীর কাহিনির প্রাধান্যে তাতে মানবীয় অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই শ্রেণির কাব্যে মানব-মানবীর প্রেমকাহিনি রূপায়িত হয়ে গতানুগতিক সাহিত্যের ধারায় ব্যতিক্রমের সৃষ্টি করেছে। মুসলমান কবিগণ হিন্দুধর্মাচারের পরিবেশের বাইরে থেকে মানবিক কাব্য রচনায় অভিনবত্ব দেখান। রোমান্টিক কবিরা তাঁদের কাব্যে ঐশ্বর্যবান, প্রেমশীল, সৌন্দর্যপূজারী, জীবনপিপাসু মানুষের ছবি এঁকেছেন। ড. সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করে মন্তব্য করেছেন, 'রোমান্টিক কাহিনি কাব্যে পুরানো মুসলমান কবিদের সর্বদাই একচ্ছত্রতা ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দেবদেবীর কল্পনার কোন অবকাশ ছিল না। তাই বাংলা সাহিত্যের ধর্মীয় পরিবেশের বাইরে থেকে এই কবিরা স্বতন্ত্র কাব্যধারার প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন এসব কাব্যে নতুন ভাব, বিষয় ও রসের যোগান দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যের বাইরে নতুন ভাবনা চিন্তা ও রসমাধুর্যের পরিচয় এ কাব্যধারায় ছিল স্পষ্ট। ধর্মের গণ্ডির বাইরে এই শ্রেণির জীবনরসাশ্রিত প্রণয়োপাখ্যান রচিত হয়েছিল বলে তাতে এক নতুনতর ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয় ।
রোমান্টিক প্রণয়কাব্যগুলোতে স্থান পেয়েছে বিষয়বস্তু হিসেবে মানবীয় প্রণয়কাহিনি। এই প্রণয়কাহিনি মর্ত্যের মানুষের। ড. ওয়াকিল আহমদ মন্তব্য করেছেন, 'মানুষের প্রেমকথা নিয়েই প্রণয়কাব্যের ধারা, কবিগণ মধুকরী বৃত্তি নিয়ে বিশ্বসাহিত্য থেকে সুধারস সংগ্রহ করে প্রেমকাব্যের মৌচাক সাজিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে তা অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। মুসলমান কবিরাই এ কৃতিত্বের অধিকারী।”
প্রণয়কাব্যগুলোর বিকাশ ঘটেছিল বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পরিসরে। মুসলমান কবিগণের সামনে দৃষ্টান্ত হিসেবে ছিল হিন্দুপুরাণ পরিপুষ্ট পাঁচালি। এই একঘেঁয়ে ধর্মগীতির ধারা তাঁদের কাছে প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে নি। বরং প্রণয়কাব্য রচনায় মূল্যবান অবদান রেখে তাঁরা বাংলা কাব্যে সঞ্চার করে গেছেন এক অনাস্বাদিত রস। মঙ্গলকাব্যের কাহিনি গ্রথিত হয়েছে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু প্রণয়কাব্যের লক্ষ্য ছিল শিল্পসৃষ্টি ও রসসঞ্চার। রোমান্টিক কথা ও কাহিনির অসাধারণ ভাঙার আরবি-ফারসি সাহিত্যের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় বাংলা সাহিত্যে এই ধারার সৃষ্টি। আর এতে আছে জীবনের বাস্তব পরিবেশের চেয়ে ইরানের যুদ্ধামোদী রাজদরবার ও নাগর সমাজের মানসাভ্যাসের প্রতিফলন।' প্রণয়কাব্যগুলোতে উপাদান হিসেবে স্থান পেয়েছে 'মানবপ্রেম, রূপ-সৌন্দর্য, যুদ্ধ ও অভিযাত্রা, অলৌকিকতা ও আধ্যাত্মিকতা।
বাংলার মুসলমান কবিগণের মধ্যে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর চৌদ্দ শতকের শেষে বা পনের শতকের প্রথমে 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য রচনা করার মাধ্যমে এই ধারার প্রবর্তন করেন। তারপর অসংখ্য কবির হাতে এই কাব্যের বিকাশ ঘটে এবং আঠার শতক পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত হয়। এই দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমান কবিগণের স্বতন্ত্র অবদান ব্যাপকতা ও ঔজ্জ্বল্যে বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা সাহিত্যকে আরবি ফারসি হিন্দি সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে যে নতুন ঐতিহ্যের প্রবর্তন করা হয় তার তুলনা নেই। পরবর্তী পর্যায়ে দোভাষী পুঁথির মধ্যে এই ধরনের বিষয় স্থান পেলেও তাতে কোন ঔজ্জ্বল্য পরিলক্ষিত হয় না।
আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য
আরাকান রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের যে বিকাশ সাধিত হয়েছিল তা এদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙালি মুসলমান কবিরা ধর্মসংস্কারমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনি অবলম্বনে কাব্যধারার প্রথম প্রবর্তন করে এ পর্যায়ের সাহিত্যসাধনাকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী করেছেন। ধর্মীয় ভাবভাবনায় সমাচ্ছন্ন কাব্যজগতের পাশাপাশি মুক্ত মানবজীবনের আলেখ্য অঙ্কনের মাধ্যমে মুসলমান কবিগণ সূচনা করেছেন স্বতন্ত্র ধারার। সুদূর আরাকানে বিজাতীয় ও ভিন্ন ভাষাভাষী রাজার অনুগ্রহ লাভ করে বঙ্গভাষাভাষী যে সকল প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছিল তাঁরা তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অবদানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন এবং মধ্যযুগের ধর্মনির্ভর সাহিত্যের পাশে মানবীয় প্রণয়কাহিনি স্থান দিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিগণকর্তৃক সৃষ্ট কাব্যরসাস্বাদনের নতুন ধারাটি বাংলা সাহিত্যের মূল প্রবাহ থেকে স্বতন্ত্র এবং ভৌগোলিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তা সর্বজনীন বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল।
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিগণের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিষয়টি পণ্ডিতদের দৃষ্টিতে আসতে বিলম্বিত হয়েছে। মুসলমান কবিরা ইসলামি বিষয় অবলম্বনে কাব্যরচনা করায় বৃহত্তর হিন্দুসমাজ তার প্রতি সমাদর দেখায় নি। ফলে হিন্দুসমাজে এসব কবির নাম অজানা ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখের উদ্যোগে হাতে লেখা পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হলেও মুসলমান কবিদের রচনা উপেক্ষিত থেকেছে। পরবর্তী কালে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মুসলমান কবিগণের পুঁথি আবিষ্কার করে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের বিস্ময়কর অবদানের বিশাল ভাণ্ডার উদ্ঘাটন করেন। বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় মধ্যযুগের মুসলমান কবিগণ স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক কারণে আরাকানের মুসলিম সংস্কৃতি বাংলাদেশের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়লেও তার মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ নতুন সাহিত্যসৃষ্টি যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম প্রকাশ হিসেবে দেখা। দিয়েছিল তা বাংলাদেশের গবেষকগণের ঐকান্তিকতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
বাংলাদেশের বাইরে বার্মার (বর্তমান মায়ানমার) অন্তর্ভুক্ত মগের মুল্লুক আরাকানে বাংলা কাব্যচর্চার বিকাশ বিশেষ কৌতূহলের ব্যাপার বলে মনে হতে পারে। আরাকানকে বাংলা সাহিত্যে 'রোসাং' বা 'রোসাঙ্গ' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্মার উত্তর-পশ্চিম সীমায় এবং চট্টগ্রামের দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এর অবস্থান ছিল। আরাকানবাসীরা তাদের দেশকে 'রখইঙ্গ' নামে অভিহিত করত। কথাটি সংস্কৃত 'রক্ষ' থেকে উৎপন্ন বলে মনে করা হয়। আরাকানি ভাষায় 'রখইঙ্গ' শব্দের অর্থ দৈত্য বা রাক্ষস এবং সে কারণে দেশকে বলে 'রখইঙ্গ তঙ্গী' বা রাক্ষসভূমি। 'রখইঙ্গ' থেকেই 'রোসাঙ্গ' শব্দের উৎপত্তি। আইন-ই-আকবরিতে এদেশ 'আখরত্ব' নামে অভিহিত হয়েছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হক 'রখইং' শব্দের ইংরেজি অপভ্রংশ 'আরাকান' বলে উল্লেখ করেছেন। আরাকানের অধিবাসীরা সাধারণভাবে বাংলাদেশে 'মগ' নামে পরিচিত। এই 'মগ' বা "মঘ শব্দটি ‘মগধ' শব্দজাত এবং শব্দটি আরাকানি ও বৌদ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বিবেচিত।
বাংলাদেশ মুসলমান অধিকারে আসার পূর্বে আরাকানে মুসলমানদের আগমন ঘটে। খ্রিস্টীয় আট-নয় শতকে আরাকানরাজ মহাতৈং চন্দয় (৭৮৮-৮১০) এর রাজত্বকালে যে সকল আরবিয় বণিক স্থায়ীভাবে সে দেশে বসবাস শুরু করে তাদের মাধ্যমেই সেখানে ইসলাম ধর্মের প্রচার হয়। একই সময় থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলেও ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে ধর্মীয় বন্ধনের মাধ্যমে এই দুই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণ মিলে যে, আরাকানরাজারা দেশধর্মের প্রভাবের ঊর্ধ্বে একটি সর্বজনীন সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেখানে ছিল মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব। মেঃৎ-চৌ-মৌন-এর আমলে ১৪৩০ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত রোসাঙ্গ গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দিন মহম্মদ শাহর করদরাজ্য রূপে বিদ্যমান ছিল।
‘বার্মার মূল ভূখণ্ড ও আরাকানের মধ্যেকার দুরতিক্রম্য পর্বতই আরাকানের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন সত্তার এবং সমুদ্রসান্নিধ্য তার সমৃদ্ধির কারণ।' আরাকান রাজ নরমিখলা বার্মারাজার ভয়ে ১৪৩৩ সালে চট্টগ্রামের রামু বা টেকনাফের শত মাইলের মধ্যে অবস্থিত 'মোহ' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। সে সময় থেকে ১৭৮৫ সাল পর্যন্ত তিন শ বছর ম্রোহঙ আরাকানের রাজধানী ছিল। এই ম্রোহঙ শব্দ থেকেই রোসাঙ্গ নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকের ধারণা।
রোসাঙ্গের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। এই সময় থেকে তাঁরা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সঙ্গে এক একটি মুসলমানি নাম ব্যবহার করতেন। তাঁদের প্রচলিত মুদ্রার একপীঠে ফারসি অক্ষরে কলেমা ও মুসলমানি নাম লেখার রীতিও প্রচলিত হয়েছিল। যে সব ইসলামি নাম তাঁরা ব্যবহার করেছেন সেগুলো হল : কলিমা শাহ্, সুলতান, সিকান্দর শাহ্, সলীম শাহ্, হুসেন শাহ প্রভৃতি। ১৪৩৪ থেকে ১৬৪৫ সাল পর্যন্ত দুই শতাধিক বৎসর ধরে আরাকান রাজগণ মুসলমানদের ব্যাপক প্রভাব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এই সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. মুহম্মদ এনামুল হক মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গের (মোগল-পাঠান) মুসলিম রাজশক্তির সহিত স্বাধীন আরাকান রাজগণের মোটেই সদ্ভাব ছিল না, অথচ তাঁহারা দেশে মুসলিম রীতি ও আচার মানিয়া আসিতেছিলেন। ইহার কারণ খুঁজিতে গেলে মনে হয়, আরাকানি মঘসভ্যতা, রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার হইতে বঙ্গের মুসলিম সভ্যতা রাষ্ট্রনীতি ও আচারব্যবহার অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত ছিল বলিয়া আরাকানি রাজগণ বঙ্গের মুসলিম প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।
মর্সিয়া সাহিত্য
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'মর্সিয়া সাহিত্য' নামে এক ধরনের শোককাব্য বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন কি তার বিয়োগাত্মক ভাবধারার প্রভাবে আধুনিক যুগের পরিধিতেও তা ভিন্ন আঙ্গিকে এসে উপনীত হয়েছে। শোক বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে সাহিত্যসৃষ্টি বিশ্ব সাহিত্যের প্রাচীন রীতি হিসেবে বিবেচিত। 'মর্সিয়া' কথাটি আরবি, এর অর্থ শোক প্রকাশ করা। আরবি সাহিত্যে মর্সিয়ার উদ্ভব নানা ধরনের শোকাবহ ঘটনা থেকে হলেও পরে তা কারবালা প্রান্তরে নিহত ইমাম হোসেন ও অন্যান্য শহীদকে উপজীব্য করে লেখা কবিতা মর্সিয়া নামে আখ্যাত হয়। আরবি সাহিত্য থেকে মর্সিয়া কাব্য ফারসি সাহিত্যে স্থান পায়। ভারতে মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশে ফারসি ভাষায় মর্সিয়া প্রচলিত হয় এবং পরে উর্দু ভাষাতেও তার প্রসার ঘটে। এসব আদর্শ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলন হয়। ভারতে বিভিন্ন ভাষায় মর্সিয়া সাহিত্যের প্রচলনের পিছনে পারস্য দেশীয় বণিক, দরবেশ, পণ্ডিত, কবি প্রমুখের অনুপ্রেরণা বিশেষ ভাবে কাজ করেছে।
এসব কাব্যের কোন কোনটি যুদ্ধ কাব্য হিসেবে বিবেচনার যোগ্য। যুদ্ধের কাহিনি নিয়ে কোন কোনটি পরিণতিতে চরম বিয়োগাত্মক রূপ গ্রহণ করেছে। শেষে কাব্য হয়ে উঠেছে মর্সিয়া বা শোক কাব্য। কোথাও কোথাও যুদ্ধকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে জঙ্গনামা। কারবালার বিষাদময় কাহিনিতে যুদ্ধের ঘটনা যত প্রাধান্য পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে শোকের অনুভূতি। এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম সাকলায়েন মন্তব্য করেছেন, ‘জঙ্গনামা বা যুদ্ধকাহিনি-সংবলিত কাব্যগুলি মুসলিম কবিসৃষ্ট সাহিত্যধারার মধ্যে নানাকারণে বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। কারবালা-যুদ্ধভিত্তিক কাব্যনির্মাণ সেকালের কবিদের কাছে ফ্যাশান হিসাবে গণ্য হতো এবং সেটা প্রলোভনের ব্যাপারও ছিল। তার কারণ সুস্পষ্ট। মুহরম মাস এলেই বাংলার গ্রামে-গঞ্জে মুসলমানদের মন বেদনাকরুণ পুথিপাঠের আসর বসাতো আর সেইজন্য কবিরাও কারবালার করুণ কাহিনি নিয়ে শহীদে কারবালা, জঙ্গনামা, হানিফার লড়াই ইত্যাদি কাব্য লেখার তাগিদ বোধ করতেন।'
মর্সিয়া কাব্য বা শোক কাব্যের পটভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. আহমদ শরীফ লিখেছেন, 'যুদ্ধ কাব্যের মধ্যে কারবালাযুদ্ধ কাব্যই ষোল-সতের শতক থেকে বাংলার মুসলিম সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হতে থাকে। তার কারণ দাক্ষিণাত্যের বাহমনিরাজ্যে- বিজাপুরে-বিদরে-বেরারে-গোলকুণ্ডায়-আহমদনগরে ইরানি বংশজ শিয়ারাই সুলতান ও শাসকগোষ্ঠী ছিলেন। শিয়ারা কারবালা যুদ্ধকে স্মরণ করা অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় পার্বণ বলেই জানে। চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের শিয়াদের ও ইরানি শিয়াদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, সে সূত্রে ষোল শতক থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'মাতুল হোসেন' (হোসেন নিধন) কাব্য রচিত হতে থাকে, তারপর শিয়া সাক্ষাতী-শাসিত ইরানে আশ্রিত হুমায়ুনের দিল্লি প্রত্যাবর্তনের পরে দরবারসূত্রে ইরানের ও ইরানীয় প্রভাব প্রবল ও সর্বব্যাপী হতে থাকে। আবার আঠার শতকে সাফাতী রাজত্বের অবসানে ভারতে বাংলায় আশ্রিত শিয়া ইরানিদের প্রভাবে মুহররম তাজিয়াদি সহ একটি জনপ্রিয় জাতীয় পার্বণের মর্যাদায় স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পায়।
মোগল আমলে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে শিয়া শাসক ও আমীর ওমরাগণ শাসনকার্য উপলক্ষে এসে বসবাস করতেন। মুসলমানদের মধ্যে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা মর্সিয়া সাহিত্য বিকাশের প্রেরণা দান করেন। তৎকালীন শিয়া শাসকরা কবিগণকে উৎসাহ প্রদান করতেন। অনেক কবি মুর্শিদাবাদের নবাবের মনোরঞ্জনের জন্য মর্সিয়া রচনায় আত্মনিয়োগ করতেন।
মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে ড. আহমদ শরীফ মন্তব্য করেছেন, 'যদিও ইমাম হাসান-হোসেনের প্রতি সমকালে হযরত আলীর ভক্ত-অনুগতদের ছাড়া আর কারও তেমন সমর্থন সহানুভূতি ছিল না, তবু কালক্রমে আল্লাহর বান্দা ও রসুলের নাতি বলেই মুসলিম মাত্রই হাসান-হোসেনের ভক্ত-সমর্থক এবং মুয়াবিয়া-এজিদের নিন্দুক হয়ে ওঠে। যেহেতু পরবর্তী কালে মুসলিমমাত্রই রসুলের আত্মীয় বলে তাঁর হতভাগ্য দৌহিত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে, অর্থাৎ পরাজিত পক্ষের সমর্থক হয়ে যায়, যেহেতু নায়ক বিজয়গৌরব হীন, সেহেতু তার প্রধান রস করুণ হতেই হয়—শোকের বা কান্নার আধার বলেই এ বিলাপ-প্রধান সাহিত্যের নাম 'মর্সিয়া সাহিত্য বা শোক সাহিত্য।'
মর্সিয়া সাহিত্যের উৎপত্তি কারবালার বিষাদময় কাহিনি ভিত্তি করে হলেও তার মধ্যে অন্যান্য শোক ও বীরত্বের কাহিনির অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফাগণের বিজয় অভিযানের বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনিও এই শ্রেণির কাব্যে স্থান পেয়েছে। 'জঙ্গনামা' নামে বাংলা সাহিত্যে এ ধরনের কাব্য রচিত হয়েছে। মর্সিয়া সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. গোলাম সাকলায়েন তাঁর 'বাংলায় মর্সিয়া সাহিত্য' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'এই কাব্যগুলির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান তাঁহাদের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলেন ও তাঁহারা ইহার মারফত অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিখিলেন। বাংলা মর্সিয়া কাব্যগুলি প্রধানত অনুবাদ সাহিত্য হিসাবেই গড়িয়া উঠে। বাঙালি কবিগণ যদিও মূলত ফারসি ও উর্দু কাব্যগুলির ভাবকল্পনা ও ছায়া আশ্রয় করিয়া তাহাদের কাব্যাদি রচনা করিয়াছিলেন তথাপি এগুলির মধ্যে তাঁহাদের মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় বিদ্যমান। ফলে এই কাব্যগুলি এক প্রকার অভিনব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদূর আরব পারস্যের মানুষের কাহিনি কাব্যাকারে লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া কবিগণ যে বাগভঙ্গি ও পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব ও উদ্ভট হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, বাঙালি কবিগণ মাটির প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।'
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কোনটি মর্সিয়া সাহিত্য?
মধুমালতী
চন্দ্রাবতী
লায়লী- মজনু
জঙ্গনামা
#.’মর্সিয়া’ শ্বদটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
উর্দু
সংস্কৃত
ফারসি
আরবি
#.'ইউসুফ জুলেখা' মর্সিয়া সাহিত্যের লেখক কে?
শেখ ফয়জুল্লাহ
দৌলতখাঁ
আব্দুল হাকিম
আব্দুল করিম
#.মর্সিয়া সাহিত্যের বিষয়বস্তু-
শোক
প্রকৃতি
সৌন্দর্য
আনন্দ
#.”মর্সিয়া” শব্দের উৎস ভাষা--
আরবি
ফারসি
উর্দু
তুর্কি
লোকসাহিত্য
লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য যা পুরানো ঐতিহ্য ও সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে রচিত হয়। লোকসাহিত্য লোকসংস্কৃতির একটি জীবন্ত ধারা; এর মধ্য দিয়ে জাতির আত্মার স্পন্দন শোনা যায়।
তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে ‘জনপদের হূদয়-কলরব’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। লোকসাহিত্যকে প্রধানত লোকসঙ্গীত, গীতিকা, লোককাহিনী, লোকনাট্য, ছড়া, মন্ত্র, ধাঁধা ও প্রবাদ এই আটটি শাখায় ভাগ করা যায়…আরো পড়ুন
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.বাংলা লোকসাহিত্য সংশ্লিষ্ট 'আলকাপ' হল একপ্রকার-
কর্মসঙ্গীত
পালাগান
সারি গান
বিবেকের গান
#.নিচের কোন কবি লোকসাহিত্য সংগ্রাহক ছিলেন?
কাজী নজরুল ইসলাম
সমর সেন
আবুল হোসেন
জসীমউদ্দীন
#.লোকসাহিত্য কাকে বলে ?
লোক সাধারনের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ্রামের অশিক্ষিত ও অক্ষত লোকদের সৃষ্ট রচনাকে
লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী গান ছড়া ইত্যাদিকে
গ্রামীন নরনারীর প্রনয় সংবলিত উপাখ্যানকে
#.লোকসাহিত্য কাকে বলে
গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে
লোক সাধারণের কল্যাণে স্তুতিমূলক রচনাকে
লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদিকে
গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে
ধর্মীয় উপখ্যানকে
#.লোকসাহিত্য বলতে কি বোঝায়?
ছড়া, গান, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন
কবিতা, গান
উপন্যাস, নাটক
প্রাচীন চিত্রকলা
ছড়া
বাংলা সাহিত্যের একটি শক্তিশালী শাখা হলো ছড়া। প্রাচীন যুগে ‘ছড়া’ সাহিত্যের মর্যাদা না পেলেও বর্তমানে সে তার প্রাপ্য সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখনও অনেকেই ছড়া সাহিত্যকে শিশু সাহিত্যেরই একটি শাখা মনে করেন কিংবা সাহিত্যের মূল ধারায় ছড়াকে স্বীকৃতি দিতে চান না, তবুও অসংখ্য ছড়াকারের প্রচেষ্টাতে ছড়া এখন বাংলা সাহিত্যের এক শানিত উচ্চারণ, বলিষ্ট প্রতিনিধি। দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ছড়াকে স্থান না দিলেও ইতোমধ্যে বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিদিনের আয়োজনে ছড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ ছড়াকে ‘কবিতা’ বলার পাশাপাশি আধুনিক গদ্য কবিতার যুগে এসব মিলযুক্ত কবিতা বা পদ্যের অবস্থানকে হালকা করে দেখা সত্ত্বেও ছড়া সাহিত্যের গতিপথে তেমন কোন ব্যাঘাতই সৃষ্টি হয়নি। বরং তাদের এসমস্ত অবজ্ঞার কারণে ছড়াকারদের চেতনাবোধ আরো জাগ্রত হয়েছে, এগিয়ে গেছে ছড়া আন্দোলন।
ছড়া প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, ‘সুদূর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য (ছড়া) যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা অর্থেও অতীত রস পেয়েছে। ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মধ্যে। সেই জন্য অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর (ছড়া) আয়ু বেড়ে চলেছে।’ এক সময় ছড়াকে মনে করা হতো শুধুই শিশু সাহিত্য। তবে এখন আর তা মনে করা হয় না, বাংলা সাহিত্যে ছড়া তাঁর নিজস্ব অবস্থান তৈরি করতে পেরেছে। এখন ছড়াকে বিভিন্ন প্রকারে ভাগ করা হয়। **যেমন- শিশুতোষ ছড়া, রাজনৈতিক ছড়া, ছড়ার ছন্দাশ্রিত কিশোর কবিতা প্রভৃতি। এর মধ্যে শিশুতোষ ছড়া তৈরি হয় কেবলমাত্র শিশু-মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। এ জাতীয় ছড়ায় ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যের অর্থ থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে। যেমন- ‘হাট্টিমাটিম টিম/ তারা মাঠে পাড়ে ডিম/ তাদের খাড়া দুটো শিং…./
তারা হাট্টিমাটিম টিম’। কিংবা- ‘আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে/ ঢাল মৃদঙ্গ ঘাঘর বাজে’। অথবা- ‘বাকবাকুম পায়রা/ মাথায় দিয়ে টায়রা/ বউ সাজবে কাল কি? চড়বে সোনার পালকি?’ প্রভৃতি। এসব ছড়া শিশুদের কল্পলোকে নিয়ে যায় অনেকটাই রূপকথার গল্পের মতো। বাস্তবে হাট্টিমাটিম টিম কিংবা আগডুম বাগডুম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই! কোন কোন ছড়া আবার একই সাথে শিশুদের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি বড় ধরনের রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক চিত্র অংকন করে থাকে। কিংবা প্রতিবাদী চেতনা জাগ্রত করে জনতার মনে। যেমন- ‘খোকন খোকন ডাক পাড়ি/ খোকন গেল কার বাড়ি/ আয়রে খোকন ঘরে আয়/ দুধমাখা ভাত কাকে খায়’। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা হলো এক মা তার ছোট্ট খোকার জন্য ভাত বেড়ে অপেক্ষা করছে। কিন্তু খোকন সোনা অন্যের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সেই দুধমাখা ভাত এসে কাকে খেয়ে ফেলছে। এই চিত্রটি শিশুদের মনোরঞ্জনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শুধুমাত্র এই চারটি লাইনই একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতোষ গল্পের বিকল্প স্থান দখল করতে সক্ষম। অন্যদিকে এই ছড়ার মূল ভাবটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ছড়াকার এখানে দেশের যুবসমাজকে আহ্বান করছেন। এখানে ‘দুধমাখা ভাত’ বলতে দেশের সম্পদ এবং ‘কাক’ বলতে বিদেশী বেনিয়াদের বুঝানো হয়েছে। ছড়াটি বৃটিশ আমলের লেখা, তাই এর ভাবার্থ বুঝতে কারো অসুবিধা হবার কথা নয়। আরেকটি জনপ্রিয় শিশুতোষ ছড়া দেখুন-‘ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে/ বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দিব কিসে?’ শিশু মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এই ছড়াতে নবাব আলীবর্দির আমলে মারাঠা কর্তৃক সাবেক বাংলায় লুটতরাজের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। নবাব আলীবর্দির বয়স কম করে হলেও তিনশ বছর তো হবেই। তাহলেই ভাবুন, সেই তিনশতাধিক বছর থেকে বাংলা সাহিত্যে ছড়া কিভাবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িয়ে আছে! শিশুতোষ ছড়া তাই কোন কোন সময় শুধুমাত্র শিশুদের জন্য রচিত হয় আবার কোন কোন সময় শিশুতোষ ছড়াতেই লুকিয়ে থাকে বড়দের জন্য বড় ধরনের সামাজিক চেতনা।
রাজনৈতিক ছড়াকে অনেকেই সাময়িক বা ক্ষণস্থায়ী বলে থাকেন। কারণ কোন নির্দিষ্ট সরকারের বা কোন মন্ত্রী এমপির দূর্নীতির চিত্র ছড়ায় অংকিত হলে তা সাময়িকভাবে মানুষের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করলেও সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এসব ছড়ার আবেদন ফুরিয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ আশির দশকের স্বৈরাচার বিরোধী অনেক ছড়াই এখন আর পাঠ করার প্রয়োজন পড়ে না। তবে একথাও মানতে হবে যে, এসব ছড়ায় সংশ্লিষ্ট সময়ের একটি রাজনৈতিক চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় যা পরবর্তী যুগের লেখকদের গবেষণার বিষয়ও হতে পারে। ‘সাহিত্যকে সমাজের আয়না বলা হয়’ এ কথাটি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ছড়াকার আবু সালেহ এর ‘পল্টনের ছড়া’ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একটি চিত্র দেখা যেতে পারে। ছড়াকার কোন প্রকার রাখঢাক না করেই স্পষ্ট উচ্চারণ করছেন, ‘ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা/ রক্ত দিয়ে পেলাম শালার এমন স্বাধীনতা!/ যার পিছনে জানটা দিলাম যার পিছনে রক্ত/ সেই রক্তের বদল দেখ বাঁচাই কেমন শক্ত!/ ….বাঁচতে চেয়ে খুন হয়েছি বুলেট শুধুই খেলাম/ উঠতে এবং বসতে ঠুকি দাদার পায়ে সেলাম!/ ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা/ রক্ত দিয়ে পেলাম শালার আজব স্বাধীনতা!’
শিশু এবং কিশোর দু’টি আলাদা শব্দ হলেও আমরা অনেক সময় ‘শিশু-কিশোর’ বলে তাদের একত্রিত করে ফেলি ৭/ ৮ বছর বয়সের একটি শিশুর মনমানসিকতা আর ১৩/১৪ বছর বয়সের একটি মন মানসিকতা কখনোই সমান হতে পারে না। অথচ আইনের দৃষ্টিতে অভ্যস্থ হয়ে আমরা সাধারণত: ১৮ বছরের কম বয়সী সবাইকেই শিশু মনে করে থাকি। অনেক গল্প উপন্যাস কিংবা সিনেমা নাটকে ১৮+ বলে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করা থাকে যাতে পাঠক মাত্রই বুঝতে পারে এটা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য। বয়স দিয়ে শিশু এবং কিশোরের সীমারেখা আলাদা করা বেশ জটিল। সংস্কৃত শ্লোকে ছেলেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লালন, দশ বছর পর্যন্ত তাড়ন এবং ষোল বছর প্রাপ্তিতে বন্ধুর মতো আচরণ করতে বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে সাত বছর বয়সে শিশুকে নামাজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে এবং দশ বছর থেকে নামাজ পড়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি করতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র প্রমুখ পন্ডিতগণ তেরো- চৌদ্দ বছরের ছেলেকে কিশোর বলেছেন। সবমিলিয়ে আমরা বারো বছর পর্যন্ত ‘শৈশব’ এবং তেরো থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত ‘কৈশোর’ বলতে পারি। ইংরেজিতেও থারটিন টু নাইনটিন বয়সীদের ‘টিনেজার’ বলা হয়ে থাকে। ছড়ার ছন্দাশ্রিতা কিশোর কবিতাগুলো তাই মূলত: এই টিনেজারদের জন্যই রচিত হয়। এগুলোকে কেউ কেউ ‘ছড়া-কবিতা’ নামেও চালিয়ে দেন। এসব ‘ছড়া-কবিতা’ বা ‘কিশোর কবিতা’ বিষয়ধর্মী ও বক্তব্য প্রধান হয়ে থাকে। তবে এসব কবিতায় ব্যবহৃত হয় ছড়ার ছন্দ। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল কিংবা শামসুর রাহমান-আল মাহমুদের অনেক ছড়াই তাই ছড়াত্ব না হারিয়েও কবিতার মর্যাদা লাভ করেছে। যেমন- রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন- ‘ওরে সবুজ ওরে অবুঝ ওরে আমার কাঁচা/ আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা’। নজরুলের ‘লিচু চোর’ কিংবা ‘ভোর হল, দোর খোল খুকুমনি ওঠ রে/ ওই ডাকে জুঁই শাখে ফুল খুকি ছোট রে’। অনুরূপ ভাবে শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদের অনেক লেখাই একদিকে ছড়া, অন্যদিকে কবিতা।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে’ ছড়াটি কার রচনা?
বঙ্কিমচন্দ্র
সুফিয়া কামাল
জীবনানন্দ দাশ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
#.ছড়া কোন ছন্দে রচিত হয়?
স্বরবৃত্ত
পয়ার
অমিত্রাক্ষর
ত্রিপদী
#.‘উলুবনে মুক্তা ছড়ানো’ প্রচলিত এমন শব্দগুচ্ছকে বলে
প্রবাদ প্রবচন
এককথায় প্রকাশ
ভাবসম্প্রসারণ
বাক্য সংকোচন
#.একজন শিক্ষার্থী ছন্দ ও ছড়ার মাধ্যমে শিখতে পছন্দ করে এবং ভালোভাবে শেখে। এ বিষয়টি কোন শিখন কাজে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হয়েছে?
করন শিখন
চিরায়ত সাপেক্ষা তত্ত্ব
গঠনবাদ
বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব
#.'ফুটপাতে ওরা সব এলিয়ে পড়ে রয়েছে। ছড়ানো খড় যেন।' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র 'নয়নচারা' গল্প থেকে গৃহীত উদ্ধৃতাংশটি __ এর দৃষ্টান্ত ।
উৎপ্রেক্ষঋদ্ধ চিত্রকল্প
উপমাসঞ্জাত রুপক
প্রতীকায়িত ব্যজস্তূতি
অন্যাসক্ত রুপকাভাস
লোকগীতি/লোকগান
লোক সঙ্গীত বাংলাদেশের সঙ্গীতের একটি
অন্যতম
ধারা।
এটি
মূলত
বাংলার
নিজস্ব
সঙ্গীত। গ্রাম
বাংলার
মানুষের জীবনের
কথা,
সুখ
দুঃখের
কথা
ফুটে
ওঠে
এই
সঙ্গীতে। এর
আবার
অনেক
ভাগ
রয়েছে। এটি
একটি
দেশের
বা
দেশের
যেকোনো
অঞ্চলের সংস্কৃতিকে তুলে
ধরে।
যেমন ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, পল্লীগীতি, গম্ভীরা ইত্যাদি।
একতারা
বাজিয়ে লোকসংগীত গাইছেন
ভাণ্ডারী আবদুল
জাব্বার, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান,
ঢাকা,
বাংলাদেশ।
বৈশিষ্ট্য
[সম্পাদনা]
·
মৌখিকভাবে লোকসমাজে প্রচারিত।
·
সম্মিলিত বা
একক
কণ্ঠে
গাওয়া
যেতে
পারে।
·
প্রজন্ম থেকে
প্রজন্মে মানুষের মুখে
মুখে
এর
বিকাশ
ঘটে।
·
সাধারণত নিরক্ষর মানুষের রচনায়
এবং
সুরে
এর
প্রকাশ
ঘটে।
·
আঞ্চলিক ভাষায়
উচ্চারিত হয়।
·
প্রকৃতির প্রাধান্য বেশি
।
·
দৈনন্দিন জীবনের
সুখ-দুঃখ, প্রকাশ পায়।
·
গ্রাম
বাংলার
মানুষের জীবন
যাপন
সম্পর্কে ধারণা
পাওয়া
যায়।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.ভাওয়াইয়া কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত?
রাজশাহী
রংপুর
কুষ্টিয়া
ময়মনসিংহ
গীতিকা (Ballad)
গীতিকা (Ballad) হল এক ধরনের গান বা কবিতা যা সাধারণত একটি গল্প বলে। এটি একটি প্রাচীন সাহিত্যিক রূপ, যা লোকসাহিত্যে বেশ প্রচলিত। বাংলা সাহিত্যে "মৈমনসিংহ গীতিকা" একটি বিখ্যাত সংকলন, যাতে পালাগানগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে।
গীতিকা সাধারণত গানের আকারে পরিবেশিত হয় এবং এতে একটি আখ্যান বা গল্প থাকে। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ছন্দে রচিত হয় এবং প্রায়শই পুনরাবৃত্তিমূলক লাইন থাকে। ইংরেজি সাহিত্যেও গীতিকার একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে।
বিভিন্ন ধরনের গীতিকা রয়েছে, যেমন -
·
ঐতিহ্যবাহী গীতিকা:
এগুলি সাধারণত লোকসাহিত্যে প্রচলিত এবং প্রাচীন গল্প বা ঘটনা বর্ণনা করে।
·
আধুনিক গীতিকা:
এগুলি আধুনিক গান বা কবিতায় ব্যবহৃত হয়, যা প্রায়শই প্রেম, বিচ্ছেদ বা অন্য কোনো আবেগপূর্ণ বিষয় নিয়ে রচিত হয়।
·
পালাগান:
বাংলা লোকসাহিত্যে পালাগান এক বিশেষ ধরনের গীতিকা, যা সাধারণত দীর্ঘ এবং নাটকীয় হয়।
মৈমনসিংহ গীতিকা, যা ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত পালাগানগুলির একটি সংকলন, বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সংকলনে "মহুয়া", "দেওয়ান-ভাবনা", "কমলা" ইত্যাদি বিখ্যাত পালাগান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সুতরাং, গীতিকা হল একটি গল্প-ভিত্তিক গান বা কবিতা, যা লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন,
আশুতোষ ভট্টাচার্য
দীনেশচন্দ্র সেন
চন্দ্রকুমার দে
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
#.’মৈমনসিংহ গীতিকা’কে সংগ্রহ করেন?
সুকুমার সেন
হীরালাল সেন
দীনেশচন্দ্র সেন
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
#.মৈমনসিংহ গীতিকা নয়-
মহুয়া
চন্দ্রাবতী
মলুয়া
ভেলুয়া
#.মৈমনসিংহ গীতিকা নয়-
মহুয়া
চন্দ্রাবতী
মালুয়া
ভেলুয়া
#.'মৈয়মনসিংহ গীতিকা' -এর সংগ্রাহক কে ছিলেন?
চন্দ্রকুমার দে
দীনেশচন্দ্র সেন
আশুতোষ ভট্রাচার্য
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
নাথগীতিকা/নাথসাহিত্য
নাথসাহিত্য বলতে নাথধর্মের অনুসারী যোগীদের দ্বারা রচিত সাহিত্যকে বোঝায়, যা মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নাথগীতিকা এই সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা মূলত রাজা গোপীচন্দ্রের (বা গোপীচাঁদ) জীবন এবং তার মা ময়নামতীর ধর্ম ও যোগ সাধনার কাহিনী নিয়ে রচিত। এই সাহিত্য ধারায় গোরক্ষনাথ, মীননাথ, হাড়িপা প্রমুখ যোগীদেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।
নাথসাহিত্য এবং নাথগীতিকা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য:
·
নাথধর্ম ও সাহিত্য:
নাথধর্ম একটি যোগ based ধর্ম, যার অনুসারীরা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের জন্য যোগ ব্যায়াম ও ধ্যান করত। নাথ সাহিত্য মূলত এই ধর্মের আচার-আচরণ এবং যোগী-সাধকদের জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত।
·
নাথগীতিকা:
নাথগীতিকাগুলি লোকসাহিত্যের একটি ধারা, যা মূলত রাজা গোপীচন্দ্রের জীবন এবং তার মা ময়নামতীর ধর্ম ও যোগ সাধনার কাহিনী নিয়ে রচিত।
·
গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র:
নাথসাহিত্য ও নাথগীতিকার প্রধান চরিত্রগুলি হল রাজা গোপীচন্দ্র, তার মা ময়নামতী, এবং গুরু জালন্ধরীপাদ, গোরক্ষনাথ, মীননাথ।
·
গোপীচন্দ্রের গান:
নাথগীতিকার মধ্যে গোপীচন্দ্রের গান খুবই জনপ্রিয়। এই গানগুলিতে রাজা গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস গ্রহণ, যোগ শিক্ষা, এবং ময়নামতীর ধর্ম ও যোগ সাধনার কাহিনী বর্ণিত আছে।
·
প্রাচীন সাহিত্য:
নাথসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের একটি প্রাচীন ধারা, যা বৌদ্ধগান ও দোঁহার ভাষারূপের পরিচয় বহন করে।
·
আঞ্চলিকতা:
নাথগীতিকা মূলত উত্তরবঙ্গের হলেও, মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা পূর্ববঙ্গের সম্পদ, যা নাথসাহিত্য থেকে জনপ্রিয়তার দিক থেকে এগিয়ে।
·
সংরক্ষণ:
স্যার জন গ্রিয়ারসন রংপুর জেলার কৃষকদের কাছ থেকে নাথগীতিকা সংগ্রহ করে তা লিপিবদ্ধ করেন।
মৈমনসিংহ গীতিকা
মৈমনসিংহ গীতিকা ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন পালাগানের সংকলন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা থেকে স্থানীয় সংগ্রাহকদের সহায়তায় প্রচলিত এ পালাগানগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে মৈমনসিংহ গীতিকা (১৯২৩) নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি বিষয়মাহাত্ম্য ও শিল্পগুণে শিক্ষিত মানুষেরও মন জয় করে।
মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে, যথা—মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ানা মদিনা। ভনিতা থেকে কিছু গীত রচয়িতার নাম জানা যায়, যেমন মহুয়া—দ্বিজ কানাই, চন্দ্রাবতী- নয়ানচাঁদ ঘোষ, কমলা- দ্বিজ ঈশান, দস্যু কেনারামের পালা- চন্দ্রাবতী, দেওয়ানা মদিনা- মনসুর বয়াতি। কঙ্ক ও লীলার রচয়িতা হিসেবে ৪ জনের নাম পাওয়া যায়- দামোদর দাস, রঘুসুত, শ্রীনাথ বিনোদ ও নয়ানচাঁদ ঘোষ। অবশিষ্ট গীতিকার রচয়িতার নাম জানা যায় না। গীতিকায় রচয়িতার নাম থাকলেও তাঁদের স্বতন্ত্র কবিত্বের চিহ্ন নেই; বরং বিষয়বস্ত্ত,
শিল্পাঙ্গিক, ভাষাভঙ্গি ও পরিবেশনা রীতি অভিন্ন বলেই প্রতিভাত হয়। আখ্যানগুলি লোকসমাজ থেকেই গৃহীত হয়েছে। ধর্ম নয়, পার্থিব জীবনকথা গীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মৈমনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালা ছাড়া বাকি ৯টি পালার মুখ্য বিষয় নরনারীর লৌকিক প্রেম। প্রেমের পরিণতি কোনোটির মিলনাত্মক, কোনোটির বিয়োগান্তক। নায়িকার নামানুসারে গীতিকাগুলির নামকরণ হয়েছে। গীতিকাগুলিতে পুরুষ চরিত্রের তুলনায় নারী চরিত্রের ভূমিকা উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত। প্রেমের প্রতিষ্ঠায় তারাই বেশি সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। নারীদের একনিষ্ঠ প্রেম ও বলিষ্ঠ চরিত্র থেকে অনেকে মনে করেন, গীতিকাগুলিতে কোনো মাতৃতান্ত্রিক সমাজের প্রভাব থাকতে পারে। নারী-চরিত্রের মহিমা কীর্তন করে দীনেশচন্দ্র সেন গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, ‘এই গীতিকাগুলির নারী চরিত্রসমূহ প্রেমে দুর্জয় শক্তি, আত্মমর্যাদার অলঙ্ঘ পবিত্রতা ও অত্যাচারীর হীন পরাজয় জীবন্তভাবে দেখাইতেছে। নারীপ্রকৃতি মন্ত্র মুখস্থ করিয়া বড় হয় নাই—চিরকাল প্রেমে বড় হইয়াছে।’
রচয়িতাদের আবির্ভাব কাল, কাব্যের জীবনকথা, আর্থ-সামাজিক পটভূমি, ভাষাদর্শ ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে গীতিকাগুলি মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। ‘কাজলরেখা’ রূপকথাধর্মী; এর বিষয়বস্ত্ত প্রাচীন। এটি ছাড়া অন্য সব গীতিকায় সামন্ত যুগের সমাজচেতনার ও মূল্যবোধের ছায়াপাত রয়েছে। রাজা, জমিদার, দেওয়ান, কাজী, কারকুন, সওদাগর, পীর-দরবেশ, সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি চরিত্র মধ্যযুগের মুসলিম শাসন-ব্যবস্থাকেই সূচিত করে। সামন্তসমাজের মূল্যবোধ ধারণ করেও মানবপ্রেমের মহিমা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, ইহজাগতিকতা এবং নৈতিকতা মৈমনসিংহ গীতিকাকে এমন সাহিত্যিক মূল্য ও মর্যাদা দান করেছে, যা আধুনিক যুগের উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা যায়।
এ প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গ গীতিকার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত ও সমাদৃত হওয়ার পরে দীনেশচন্দ্র সেন ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আরও অনেক গীতিকা সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে পূর্ববঙ্গ গীতিকা (১৯২৬) নামে মোট তিন খন্ডে প্রকাশ করেন। স্থানীয় গ্রামের মানুষ এগুলিকে ‘পালাগান’ নামে অভিহিত করে থাকে। দীনেশচন্দ্র সেন ইংরেজি ballad-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে ‘গীতিকা’ শব্দটি গ্রহণ করেন। বাংলা গীতিকা বর্ণনামূলক গীতি-আলেখ্য; তবে এতে প্রচুর নাটকীয় ঘটনার এবং চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপেরও স্থান আছে। একজন গায়েন আনুপূর্বিক ঘটনার বিবরণ ও চরিত্রের উক্তি-প্রত্যুক্তি গান করে পরিবেশন করেন; দোহাররা ধুয়া গেয়ে এবং বাজনদাররা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাঁকে সাহায্য করে। গ্রামের সাধারণ মানুষ এর দর্শক-শ্রোতা; তারা আসরে বসে মুগ্ধচিত্তে গীতিকার গীতিরস ও নাট্যরস উপভোগ করে। [ওয়াকিল আহমদ]
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.ময়মনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেছিলেন,
আশুতোষ ভট্টাচার্য
দীনেশচন্দ্র সেন
চন্দ্রকুমার দে
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
#.’মৈয়মনসিংহ গীতিকা’র সংগ্রাহক ছিলেন কে?
আশুতোষ ভট্টাচার্য
দীনেশচন্দ্র সেন
চন্দ্রকুমার দে
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র
#.’মৈমনসিংহ গীতিকা’কে সংগ্রহ করেন?
সুকুমার সেন
হীরালাল সেন
দীনেশচন্দ্র সেন
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
#.দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ‘ পূর্ববঙ্গ গীতিকার’র কোন খন্ড ‘মৈয়মনসিংহ গীতিকা’ নামে প্রকাশিত হয়?
প্রথম খন্ড
দ্বিতীয় খন্ড
তৃতীয় খন্ড
চতুর্থ খন্ড
#.মৈমনসিংহ গীতিকা নয়-
মহুয়া
চন্দ্রাবতী
মলুয়া
ভেলুয়া
পূর্ববঙ্গ গীতিকা
পূর্ববঙ্গ গীতিকা হল পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) লোকসাহিত্যের একটি বিখ্যাত সংকলন। এটি মূলত লোকমুখে প্রচলিত পালা-গান বা গাথাগুলির একটি সংকলন, যা বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য:
·
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি: পূর্ববঙ্গ গীতিকা পূর্ববঙ্গের লোকঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।
·
সংগ্রহ ও সম্পাদনা: চন্দ্রকুমার দে এটি সংগ্রহ করেন এবং দীনেশচন্দ্র সেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে সম্পাদনা করেন।
·
গুরুত্বপূর্ণ পালা: এই সংকলনে বেশ কিছু বিখ্যাত পালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: মহুয়া, দেওয়ানা মদিনা, মলুয়া, ও অন্যান্য পালা।
·
পালাগুলি: এই গীতিকাগুলোতে সাধারণত প্রেম, বিরহ, যুদ্ধ, সামাজিক অসাম্য ইত্যাদি বিষয় স্থান পেয়েছে।
·
অঞ্চল: ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, সিলেট সহ বিভিন্ন অঞ্চলের পালা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
·
সাম্প্রতিক সংস্করণ: ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক ১৯৭১-১৯৭৫ সালে সাত খণ্ডে প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশ করেন।
ডাক ও খনার বচন
ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লোকসাহিত্যের দুটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ডাক, যিনি সম্ভবত একজন জ্যোতিষী ছিলেন, এবং খনা, যিনি কৃষি ও আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতেন, তাদের নামে প্রচলিত উক্তি বা বচনগুলো 'ডাক ও খনার বচন' নামে পরিচিত। এই বচনগুলোতে গ্রামীণ জীবন, কৃষি, আবহাওয়া এবং সাধারণ জ্ঞানের বিভিন্ন দিক প্রতিফলিত হয়েছে।
ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন লোকসাহিত্যের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এগুলো মূলত ছড়ার আকারে রচিত এবং মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল।
·
ডাক:
ডাক ছিলেন একজন বিখ্যাত জ্যোতিষী এবং তার বচনগুলো মূলত ভবিষ্যৎবাণী ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে রচিত। উদাহরণস্বরূপ, "যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ" এই বচনটি মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়।
·
খনা:
খনা ছিলেন একজন বিদুষী নারী, যিনি কৃষি এবং আবহাওয়া বিষয়ক জ্ঞানের জন্য পরিচিত ছিলেন। তার বচনগুলো মূলত কৃষি বিষয়ক এবং এতে চাষাবাদ, বৃক্ষরোপণ, এবং গৃহনির্মাণের মতো বিষয়গুলো স্থান পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, " "যদি বর্ষ B, A, D তে, তবে জানবে ফসল হবে তে" এই বচনটি বর্ষার সময়ের উপর ভিত্তি করে ফসলের পূর্বাভাস দেয়।
এই বচনগুলো যুগ যুগ ধরে বাংলার গ্রামীণ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং এখনও মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব বিদ্যমান।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.‘খনার বচন' কোন যুগে সমৃদ্ধি লাভ করে?
প্রাচীন যুগ
মধ্য যুগের শেষে
প্রাচীন যুগের শেষে
মধ্যযুগের শুরুতে
#.‘খনার বচন’ কী সংক্রান্ত?
কৃষি
ব্যবসা
শিল্প
রাজনীতি
#.ডাক ও খনার বচনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ভূমিকা রেখেছেন-
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
রামমোহন রায়
বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
#.খনার বচনের উপজীব্য হচ্ছে-
কৃষিকাজ
শিল্প কাজ
মাটির কাজ
লোকচার জীবনাচরণের কাজ
#.খনার বচন কী সংক্রান্ত?
ব্যবসায়
কৃষি
রাজনীতি
শিল্প
লোককথা
লোককথা হলো একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত গল্প, উপকথা, কিংবদন্তি, এবং ঐতিহ্যবাহী রীতিনীতি। এটি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসে। লোককথাগুলি প্রায়শই সহজ ভাষায় বলা হয় এবং জীবনের বিভিন্ন দিক, যেমন নৈতিকতা, মূল্যবোধ, এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা দেয়।
লোককথার বৈশিষ্ট্য:
·
মৌখিক ঐতিহ্য:
লোককথা সাধারণত লিখিত আকারে না থেকে, মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত থাকে।
·
সাধারণ ভাষা:
গল্পগুলি সহজ, সরল ভাষায় বলা হয়, যা সবাই বুঝতে পারে।
·
নৈতিক শিক্ষা:
লোককথাগুলিতে প্রায়শই নৈতিক শিক্ষা, মূল্যবোধ, এবং সমাজের রীতিনীতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.যে স্ত্রীলোক প্রিয় কথা বলে তাকে বলা হয়--
প্রিয়ংবদা
অবীরা
মাধুকর
কেকা
কবিগান
কবিগান এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক গান। দুটি দলে এ প্রতিযোগিতা হয়। দলের দলপতিকে বলে কবিয়াল বা সরকার। কবিয়ালের সঙ্গীদের নাম দোহার। যন্ত্রসঙ্গীতকারীদের মধ্যে ঢুলি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দল দুটি পর্যায়ক্রমে আসরে এসে গান পরিবেশন করে। এ গানের বেশ কয়েকটি অঙ্গ আছে, যেগুলি বিশেষ অনুক্রমে বিন্যস্ত, যেমন: ডাক, মালসি, সখীসংবাদ, কবি, কবির টপ্পা, পাঁচালি ও ধুয়া এবং জোটের পাল্লা। এগুলির মধ্যে মালসি, সখীসংবাদ ও কবি নামক গানগুলির গঠনশৈলী অভিন্ন। এসব গানের পদক্রম এরূপ: ধরণ, পাড়ন, ফুকার, মিশ, মুখ, প্যাঁচ, খোচ, অন্তরা, পরচিতান ও ছুট্টি। ডাক গান বন্দনামূলক এবং এগুলি লঘুসঙ্গীতের মতো। বাউল গানের সমতুল্য ধুয়া গানগুলিও প্রায় একই গঠনের, যা পাঁচালির ফাঁকে ফাঁকে পরিবেশিত হয়। পাঁচালি অংশে পয়ার ও ত্রিপদীতে কবিয়ালগণ ছড়া কাটেন। সবশেষে জোটের পাল্লা অংশে দু কবিয়াল কোনো একটা গানের সুরে ছড়া কাটতে কাটতে গান শেষ করেন। আঠারো শতক কবিগানের উদ্ভবকাল। বাংলাদেশের একাধিক লোকসঙ্গীতের সমন্বয়ে এ গানের সৃষ্টি হয়েছে।
কবিগান সর্বপ্রথম ঐতিহাসিক তাৎপর্য অর্জন করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতায়। নবউত্থিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে কবিগান তখন বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সময় ও শিল্পের গুরুত্ব বিবেচনায় এ গান বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। গোঁজলা গুঁইকে বলা হয় কবিগানের আদি কবিয়াল। তাঁর আবির্ভাবকাল আঠারো শতকের প্রথমার্ধ। উনিশ শতকের কলকাতায় যে কয়জন কবিয়াল বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন, তাঁদের মধ্যে হরু ঠাকুর (১৭৪৯-১৮২৪), নিতাই বৈরাগী (১৭৫১-১৮২১), রাম বসু (১৭৮৬-১৮২৮), ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিলগ্নে কলকাতায় কবিগান গুরুত্ব হারাতে শুরু করে। তবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এ গানের জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকে। এ অঞ্চলে কবিগান নতুন কিছু বৈশিষ্ট্যও অর্জন করে। এ পর্বের কবিগানে বাংলাদেশের লোকসাধারণের কবিপ্রতিভা, সৃজনশীলতা এবং সঙ্গীতসাধনার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এক্ষেত্রে প্রথম প্রতিভাধর কবিয়াল ছিলেন তারকচন্দ্র সরকার (১৮৪৭-১৯১৪)। বিশ শতকে সর্বাধিক জনপ্রিয় কয়েকজন কবিয়াল হরিচরণ আচার্য (১৮৬১-১৯৪১), রমেশ শীল (১৮৭৭-১৯৬৭), রাজেন্দ্রনাথ সরকার (১৮৯২-১৯৭৪), মানিকগঞ্জের রাধাবল্লভ সরকার, উপেন্দ্র সরকার, ভাসান সরকার, কুমুদ সরকার, অভয়চরণ সরকার, বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী (১৯০৩-১৯৮৫), গুমানী দেওয়ান প্রমুখ। [স্বরোচিষ সরকার]
#.কবি গানের প্রথম কবি কে?
গোঁজলা পুট
হরু ঠাকুর
ভবানী ঘোষ
নিতাই বৈরাগী
পুঁথিসাহিত্য
পুঁথিসাহিত্য বলতে হাতে লেখা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যকে বোঝায়। বিশেষ করে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকর্ম যা হাতে লিখে সংরক্ষণ করা হতো, তাকে পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। এই সাহিত্য মূলত কবিতা, গান, গল্প, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রচিত হতো।
প্রাচীনকালে যখন ছাপাখানার প্রচলন ছিল না, তখন হাতে লিখে বই বা সাহিত্যকর্ম তৈরি করা হতো। এই ধরনের লেখাকে "পুস্তিকা" বা "পুঁথি" বলা হতো। অতএব, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য যা হাতে লেখা ছিল, তাকে পুঁথিসাহিত্য বলা হয়। এই সাহিত্য সাধারণত আরবি, ফারসি, হিন্দি এবং বাংলা ভাষার মিশ্রণে রচিত হতো।
পুঁথিসাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য:
·
হাতে লেখা: পুঁথিসাহিত্য হাতে লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হতো, যা তখনকার সময়ের একমাত্র উপায় ছিল।
·
বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণ: পুঁথিসাহিত্যে বাংলা ভাষার সাথে আরবি, ফারসি ও হিন্দির মিশ্রণ দেখা যায়। এটি তৎকালীন সমাজের ভাষাগত চিত্র তুলে ধরে।
·
কাহিনিভিত্তিক রচনা: পুঁথিসাহিত্য সাধারণত কোনো একটি কাহিনিকে কেন্দ্র করে রচিত হতো।
·
পাঠের রীতি: পুঁথিপাঠ করার জন্য বিশেষ রীতি ও পদ্ধতি ছিল, যেখানে নানা অঙ্গভঙ্গি ও হাস্য-রসাত্মক কথার ব্যবহার করা হতো।
·
সংরক্ষণ: পুঁথিসাহিত্য মূলত ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল।
পুঁথিসাহিত্যের গুরুত্ব:
·
ঐতিহাসিক দলিল: পুঁথিসাহিত্য তৎকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও জীবনযাত্রার ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে কাজ করে।
·
সাহিত্যিক ঐতিহ্য: এটি বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এর মাধ্যমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক ধারা সম্পর্কে জানা যায়।
·
ভাষার ক্রমবিকাশ: পুঁথিসাহিত্য বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং তৎকালীন ভাষারীতি সম্পর্কে ধারণা দেয়।
·
সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য: পুঁথিসাহিত্য তৎকালীন সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিচয় বহন করে।
কিছু বিখ্যাত পুঁথিসাহিত্য:
গুলেব কাওলি, চর্যাপদ, রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য, লাইলী মজনু, ইউসুফ জুলেখা.
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.পুঁথি সাহিত্যের ভাষা কিরূপ ?
বাংলা
ফারসি
হিন্দি
মিশ্র
#.কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয়?
ময়মনসিংহ গীতিকা
ইউসুফ জুলেখা
পদ্মাবতী
লাইলী মজনু
#.উল্লিখিত কোন রচনাটি পুঁথি সাহিত্যের অন্তর্গত নয় ?
ময়মনসিংহ গীতিকা
ইউসুফ জুলেখা
পদ্মাবতী
লাইলী মজনু
#.পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?
আমীর হামজা
দৌলত কাজী
ফকির গরিবুল্লাহ্
আলাওল
#.পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক কে?
আমীর হামজা
দৌলত কাজী
ফকির গরিবুল্লাহ্
আলাওল
টপ্পাগান
টপ্পা গান কলকাতা অঞ্চলের একটি লৌকিক গান। এটি পাঞ্জাব অঞ্চলের মূলগানের সাথে মিল থাকলেও বাংলায় এটি রাগাশ্রয়ী গান হিসেবে পরিচিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু) এর উদ্ভাবক বলে পরিচিত।[১] অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে পাঞ্জাব অঞ্চলের লোকগীতি টপ্পা গানের প্রচলন শুরু হয়। প্রধানত উটের গাড়ি চালকের মুখেই টপ্পা গান বেশি শোনা যেত।[২][৩] শোরী মিয়া (১৭৪২-১৭৯২) নামে একজন সঙ্গীতজ্ঞ টপ্পা গানগুলোকে সাঙ্গিতিক আদর্শে সাজিয়ে সম্পূর্ণ আলাদা একটি গায়ন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।[৪] এ পদ্ধতি অনুসরণ করে রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু (১৭৪১-১৮৩৯) বাংলা টপ্পা রচনা করেন। এখানেই ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে বাংলা রাগসঙ্গীত চর্চা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে টপ্পাকার কালীমির্জা (১৭৫০-১৮২০), বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রীতির প্রবর্তক রামশংকর ভট্টাচার্য (১৭৬১-১৮৫৩) এবং বাংলা ভাষায় খেয়াল রচয়িতা রঘুনাথ রায় (১৭৫০-১৮৩৬) বাংলা গানকে আরও সমৃদ্ধ করে হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের ধারার সঙ্গে যুক্ত করেন। টপ্পার উৎপত্তি কখন এবং কীভাবে শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে নানা রকমের গল্প আছে। A.F. Strangways তার Music of India গ্রন্থে– পাঞ্জাবের উট চালকদের লোকগান থেকে টপ্পার উৎপত্তি। কিন্তু অনেকেই এই কথা মানতে রাজি নন। তবে আদি টপ্পাতে পাঞ্জাবি ভাষার আধিক্য রয়েছে। এই বিচারে বলা যায়, পাঞ্জাবের লোকগীতি থেকে এই গানের সূত্রপাত ঘটেছিল। হয়তো অন্যান্য পেশার মানুষের সাথে উটচালকরা এই গান গাইতেন। কাপ্তেন উইলার্ভকে উদ্ধৃতিকে অনুসরণ করে রাজ্যেশ্বর মিত্র তার বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানা দিক গ্রন্থের টপ্পার উৎস সম্পর্কে লিখেছেন– ‘টপ্পা ছিল রাজপুতনার উষ্ট্র চালকদের গীত। শোনা যায়, মধ্যপ্রাচ্য থেকে যেসব বণিক উটের পিঠে চেপে বাণিজ্য করতে আসত, তারা সারারাত নিম্নস্বরে টপ্পার মতো একপ্রকার গান গাইতে গাইতে আসত। তাদের গানের দানাদার তানকেই বলা হতো ‘জমজমা’। আসলে জমজমা শব্দে‘দলবদ্ধ উষ্ট্র’ বোঝায়। সাধারণভাব উষ্ট্রবিহারিদের গানও এই শব্দের আওতায় এসে গেছে। লাহোরে উট বদল হতো। এই লাহোর থেকেই টপ্পার চলটি ভারতীয় সংগীতে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে।’এটা ভারতের একটা সংগীত।
পাঁচালি গান
পাঁচালি গান বাংলার প্রাচীন লৌকিক সংগীতগুলোর অন্যতম। এই গান প্রধাণতঃ সনাতন ধর্মীদের বিবিন্ন আখ্যান বিষয়ক বিষয়বস্তু সংবলিত ও তাদের তুষ্টির জন্য পরিবেশিত হয়।[১] লক্ষীকান্ত বিশ্বাস কর্তৃক এই গান সর্বাপ্রথম প্রচলিত হওয়ায় তাকেই এর স্রষ্টা বলে গণ্য করা হয়।[২]
নামকরণ
[সম্পাদনা]
"প্যাঁচাল" শব্দটি থেকে "পাঁচালি" শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়।
প্রচলিত অঞ্চল
[সম্পাদনা]
এই গান / নাচ বাংলাদেশের বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর অঞ্চলেই অধিক পরিচিত। এই এলাকাগুলো ছাড়াও উত্তর বঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের কিছু এলাকায় এর প্রসার রয়েছে। এছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে আদিকাল থেকেই এর প্রচলন পরিলক্ষিত হয়।[৩]
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.পাঁচালিকার হিসাবে সর্বাধিক খ্যাতি কার ছিল?
দশরথি রায়
রামনিধি গুপ্ত
ফকির গরীবুল্লাহ
রামরাম বসু
বাংলা পাঁচালি গান
#.
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'পথের পাঁচালি' একটি ---
নাটক
ভ্রমণ কাহিনী
গল্প
উপন্যাস
বাউল গান ও লালন শাহ
বাউল গান ও লালন শাহ বাংলা লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। লালন শাহ ছিলেন একজন বিখ্যাত বাউল সাধক, যিনি তার গান ও দর্শনের মাধ্যমে বাউল মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন।
বাউল গান:
·
বাউল গান এক ধরনের লোকসঙ্গীত যা বিশেষ সুর ও বাদ্যযন্ত্রের সাথে পরিবেশিত হয়।
·
বাউল গান সাধারণত গ্রামীণ পরিবেশে গাওয়া হয় এবং এর মধ্যে জীবন, জগৎ, এবং আধ্যাত্মিকতা নিয়ে গভীর ভাবনা প্রকাশ করা হয়।
·
বাউলরা সাধারণত সাদামাটা জীবনযাপন করেন এবং একতারা, দোতারা, ঢোলক ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন।
·
বাউল গান "ভাবগান" বা "ভাবসঙ্গীত" নামেও পরিচিত।
লালন শাহ:
·
লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) ছিলেন একজন বিখ্যাত বাউল সাধক, যিনি "বাউল সম্রাট" হিসেবেও পরিচিত।
·
তিনি ছিলেন একজন গীতিকার, সুরকার এবং গায়ক।
·
লালন শাহের গানগুলি বাংলা লোকসাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
·
তার গানগুলোতে মানবতাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, এবং জীবনের গভীরতা প্রকাশ পায়।
·
লালন শাহের গানগুলি আজও মানুষের মনে গভীর রেখাপাত করে।
·
তিনি প্রায় ২,০০০ গান রচনা করেছেন বলে মনে করা হয়।
লালন শাহ ও বাউল গান:
·
লালন শাহ বাউল গানের একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন।
·
তাঁর গানের মাধ্যমে উনিশ শতকে বাউল গান জনপ্রিয়তা লাভ করে।
·
লালন শাহের গানগুলি বাউল দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
·
বাউল গান ও লালন শাহ একে অপরের পরিপূরক।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.“বাউল গানকে” হেরিটেজ অব হিউম্যানিটি বলে স্বীকৃতি দিয়েছে-
ইউনেস্কো
ইউনিসেফ
ইউএনডিপি
ইউএনএফপিএ
#.বাউল গানের বিশেষত্ব কি?
মরমীবাদ
মারেফাত
আধ্যাত্ম্য বিষয়ক
প্রেম বিষয়ক
অবক্ষয় যুগ/যুগ সন্ধিক্ষণ (১৭৬০-১৮৬০ খ্রি.)
অবক্ষয় যুগ:
১। ১৭৬০সালে ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যুুর পর থেকে আধুনিকতার যথার্থ বিকাশকাল পর্যন্ত(১৮৬০সালে মাইকেলের আবির্ভাব) অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির স্বল্পতা,পরিবেশ-পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে এ পর্যায়কে একটি স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
২। কেউ কেউ এ যুগের পরিধি ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ সাল অর্থাৎ কবি ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব-পূর্বকাল পর্যন্ত নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরুর এ সময়টাকে ‘অবক্ষয় যুগ’ বলে। কেউ কেউ এ সময়টাকে ‘যুগ সন্ধিক্ষণ’ নামেও অভিহিত করেন।
৩। মধ্য ও আধুনিক যুগের মধ্যবর্তী এ একশত বছরের সাহিত্য নিদর্শন বাংলা সাহিত্যের দুই যুগের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে।
৪। অবক্ষয় যুগ তথা যুগ সন্ধিক্ষণের ফসল হিন্দু কবিওয়ালাদের কবিগান আর মুসলমান শায়েরদের দোভাষী পুঁথি।
বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)
মুসলমান শাসনের সূত্রপাতে দেশে রাজনৈতিক অরাজকতার অনুমান করে কোন কোন পণ্ডিত অন্ধকার যুগ চিহ্নিত করেছেন। এ ধরনের ইতিহাসকারেরা বিজাতীয় বিরূপতা নিয়ে মনে করেছেন, 'দেড় শ দু শ কিংবা আড়াই শ বছর ধরে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালানো হয় কাফেরদের ওপর। তাদের জীবন-জীবিকা এবং ধর্ম-সংস্কৃতির ওপর চলে বেপরোয়া ও নির্মম হামলা। উচ্চবিত্ত ও অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই মরল, কিছু পালিয়ে বাঁচল, আর যারা এর পরেও মাটি কামড়ে টিকে রইল, তারা ত্রাসের মধ্যেই দিনরজনী গুণে গুণে রইল। কাজেই, ধন জন ও প্রাণের নিরাপত্তা যেখানে অনুপস্থিত, যেখানে প্রাণ নিয়ে সর্বক্ষণ টানাটানি, সেখানে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার বিলাস অসম্ভব । ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির উন্মেষ-বিকাশের কথাই ওঠে না।' ড. সুকুমার সেনের মতে, “মুসলমান অভিযানে দেশের আক্রান্ত অংশে বিপর্যয় শুরু হয়েছিল। গোপাল হালদারের মতে, তখন 'বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি তুর্ক আঘাতে ও সংঘাতে, ধ্বংসে ও অরাজকতায় মূর্ছিত অবসন্ন হয়েছিল। খুব সম্ভব, সে সময়ে কেউ কিছু সৃষ্টি করবার মত প্রেরণা পায় নি।' কেউ মনে করেন এ সময়ে 'বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বারম্বার হরণকারী বৈদেশিক তুর্কিদের নির্মম অভিযান প্রবল ঝড়ের মত বয়ে যায় এবং প্রচণ্ড সংঘাতে তৎকালীন বাংলার শিক্ষা সাহিত্য সভ্যতা সমস্তই বিনষ্ট ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা মুসলমানেরা অমানুষিক বর্বরতার মাধ্যমে বঙ্গসংস্কৃতির ক্ষেত্রে তামসযুগের সৃষ্টি করে।' তিনি মনে করেন, 'বর্বর শক্তির নির্মম আঘাতে বাঙালি চৈতন্য' হারিয়েছিল এবং পাঠান, খিলজি, বলবন, মামলুক, হাবশি সুলতানদের চণ্ডনীতি, ইসলামি ধর্মান্ধতা ও রক্তাক্ত সংঘর্ষে বাঙালি হিন্দুসম্প্রদায় কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করছিল।' তিনি আরও লিখেছেন, 'তুর্কি রাজত্বের আশি বছরের মধ্যে বাংলার হিন্দুসমাজে প্রাণহীন অখণ্ড জড়তা ও নাম-পরিচয়হীন সন্ত্রাস বিরাজ করিতেছিল ।...কারণ সেমীয় জাতির মজ্জাগত জাতিদ্বেষণা ও ধর্মীয় অনুদারতা।...১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বাংলাদেশ মুসলমান শাসনকর্তা, সেনাবাহিনী ও পীর ফকির গাজীর উৎপাতে উৎসন্নে যাইতে বসিয়াছিল। শাসনকর্তৃগণ পরাভূত হিন্দুকে কখনও নির্বিচারে হত্যা করিয়া, কখনও বা বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া এদেশে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন। ... হিন্দুকে হয় স্বধর্মত্যাগ, না হয় প্রাণত্যাগ, ইহার যে কোন একটি বাছিয়া লইতে হইত।' ভূদেব চৌধুরীর মতে, *বাংলার মাটিতে রাজ্যলিপ্সা, জিঘাংসা, যুদ্ধ, হত্যা, আততায়ীর হস্তে মৃত্যু— নারকীয়তার যেন আর সীমা ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর প্রজাসাধারণের জীবনের উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ধর্মহানির সম্ভাবনা উত্তরোত্তর উৎকট হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই জীবনের এই বিপর্যয় লগ্নে কোন সৃজনকর্ম সম্ভব হয় নি।' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমানদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'শারীরিক বল, সমরকুশলতা ও বীভৎস হিংস্রতার দ্বারা বাংলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইসলামের অর্ধচন্দ্রখচিত পতাকা প্রোথিত হইল। খ্রিঃ ১৩শ হইতে ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত—প্রায় দুই শত বছর ধরিয়া এই অমানুষিক বর্বরতা রাষ্ট্রকে অধিকার করিয়াছিল; এই যুগ বঙ্গসংস্কৃতির তামসযুগ, য়ুরোপের মধ্যযুগ The Dark Age-এর সহিত সমতুলিত হইতে পারে।' এ সব পণ্ডিত মুসলমান শাসকদের অরাজকতাকেই অন্ধকার যুগ সৃষ্টির কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়?
৬০০-৯০০ খ্রি.
১২০১-১৩৫০ খ্রি.
১৩৫১-১১৪৫০ খ্রি.
৯৫০-১২০০ খ্রি.
বাংলা বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ (১২০১-১৩৫০)
#.কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
১২০১-১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ
৬০০-৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ
১৩৫১-১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ
৬০০-৭৫০ খ্রিষ্টাব্দ
বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ পরবর্তী মধ্যযুগ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আনুমানিক ১২০০ সাল থেকে চৌদ্দ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কাল সৃজনহীন ঊষরতায় আচ্ছন্ন বলে মনে হয় ।
বলা হয়ে থাকে, ক্ষমতালোভী বিদেশাগত মুসলমান আক্রমণকারীরা বিবেচনাহীন সংগ্রাম শাসন আর শোষণের মাধ্যমে দেশে এক অস্বস্তিকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। চারুজ্ঞান বিবর্জিত জঙ্গীবাদী বস্তুবাদী শাসকদের অত্যাচারে সাহিত্য সৃষ্টি করার মত সুকুমার বৃত্তির চর্চা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষের ফলে বাঙালির বহির্জীবনে ও অন্তর্জীবনে ভীতি বিহ্বলতার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলমান শাসনের সূত্রপাত এদেশের জন্য কোন কল্যাণ বহন করে এনেছিল কিনা তা সর্বাগ্রে পর্যালোচনা করে বিতর্কের অবতারণা করা উচিত ছিল।
প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যবর্জিত তথাকথিত অন্ধকার যুগের জন্য তুর্কিবিজয় ও তার ধ্বংসলীলাকে দায়ী করা বিভ্রান্তিকর। এ সময়ের যে সব সাহিত্য নিদর্শন মিলেছে এবং এ সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার যে সব তথ্য লাভ করা গেছে তাতে অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। অন্ধকার যুগের দেড় শ বছর মুসলমান শাসকেরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন এ কথা সত্য নয়। ইলিয়াস শাহি আমলের পূর্ব পর্যন্ত খিলজি বলবন ও মামলুক বংশের যে পঁচিশ জন শাসক বাংলাদেশ শাসন করেছিলেন তাঁদের কারও কারও রাজত্বে সাকুল্যে পনের-বিশ বৎসর মাত্র দেশে অশান্তি ছিল, অন্যদের বেলায় শান্ত পরিবেশ বিদ্যমান ছিল বলে ইতিহাস সমর্থন করে। তৎকালীন যুদ্ধবিগ্রহ দিল্লির শাসকের বিরুদ্ধে অথবা অন্তর্বিরোধে ঘটেছে বলে তা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি। ফলে তাতে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার কোনও কারণ ঘটে নি। বরং এদেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষা, ধর্মকর্ম, আচারব্যবহার, আহারবিহার প্রভৃতির প্রবর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীর মধ্যে ইসলামি পরিবেশ গড়ে উঠছিল ।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের সময়কাল কত?
১২০১-১২৫০
১২০১ -১৩৫০
১২৫০-১৩৫০
১২৫০-১৪৫০
#.কোন সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
১৩৫১-১৫০০
৬০০-৭৫০
১২০১-১৩৫০
৬০০-৯৫০
#.কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
পাল
সেন
গুপ্ত
তুর্কী
কোনোটিই নয়
#.কোন শাসকদের সময়কে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে?
পাল
সেন
গুপ্ত
তুর্কী
কোনটিই নয়
#.কোন শাসকদের সময়কালকে বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয়?
পাল
সেন
গুপ্ত
তুর্কি
কোনটিই নয়