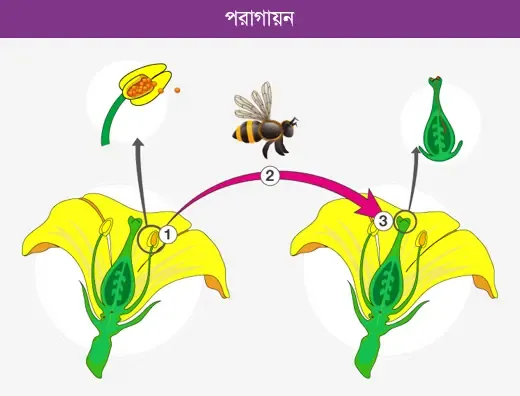DAILY SCIENCE (LEC 18)
ব্যাপন, অভিস্রবণ, শোষণ, পরিবহন ও প্রস্বেদন
উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে এবং সেই পানি ও রস কান্ডের ভিতর দিয়ে পাতায় পৌঁছায়। আবার দেহে শোষিত পানি উদ্ভিদ বাষ্প আকারে দেহ থেকে বের করে দেয়। উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন গ্যাস ত্যাগ করে, দেহে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করে ঐ রস দেহের নানা অঙ্গে পরিবহন করে ও দেহ থেকে পানি বাষ্প আকারে বের করে দেয় সেই সব প্রক্রিয়া ব্যাপন, অভিস্রবণ, শোষণ, পরিবহন ও প্রস্বেদনের মাধ্যমে ঘটে।
Table of
Content
·
ব্যাপন
·
অভিস্রবণ
·
উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ
ব্যাপন
আমরা জানি সব পদার্থই কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু দিয়ে তৈরি। এ অণুগুলো সবসময় গতিশীল বা চলমান অবস্থায় থাকে। তরল ও গ্যাসের ক্ষেত্রে অণুগুলোর চলন দ্রুত হয় এবং বেশি ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের দিকে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে যতক্ষণ না অণুগুলোর ঘনত্ব দুই স্থানে সমান হয়। অণুগুলোর এরূপ চলন প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে। ব্যাপনকারী পদার্থের অণু-পরমাণুগুলোর গতিশক্তির প্রভাবে এক প্রকার চাপ সৃষ্টি হয় যার প্রভাবে অধিক ঘনত্বযুক্ত স্থান থেকে কম ঘনত্বযুক্ত স্থানে অণুগুলো ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রকার চাপকে ব্যাপন চাপ বলে। কোনো পদার্থের অণুর ব্যাপন ততক্ষণ চলতে থাকে যতক্ষণ না উক্ত পদার্থের অণুগুলোর ঘনত্ব সর্বত্র সমান হয়। অণুগুলোর ঘনত্ব সমান হওয়া মাত্রই পদার্থের ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়। যেমন- ঘরে সেন্ট বা আতর ছড়ালে বা ধূপ জ্বালালে সমস্ত ঘরে তার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। এটি ব্যাপনের কারণে ঘটে। ধূপের ধোঁয়া ও সেন্টের অণুগুলো অধিক ঘনত্ব সম্পন্ন হওয়ায় সম্পূর্ণ ঘরে কম ঘনত্ব সম্পন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাই সমস্ত ঘর সুবাসে ভরে যায়।
উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ হতে পানি হারানোর জন্য ব্যাপন দায়ী। বায়ুমন্ডলের চাপ, মাধ্যমের ঘনত্ব, তাপমাত্রা ইত্যাদি ব্যাপনের গতিনিয়ন্ত্রণকারী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।
ব্যাপনের গুরুত্ব: জীবের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজে ব্যাপন প্রক্রিয়া ঘটে। যেমন- উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণের সময় বাতাসের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। এই অত্যাবশ্যক কাজ ব্যাপন দ্বারা সম্ভব হয়। জীবকোষে শ্বসনের সময় গ্লুকোজ জারণের জন্য অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বারা কোষে অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে যায়। উদ্ভিদ দেহে শোষিত পানি বাষ্পাকারে প্রস্বেদনের মাধ্যমে দেহ থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের করে দেয়। প্রাণীদের শ্বসনের সময় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের আদান-প্রদান ও রক্ত থেকে পুষ্টি উপাদান, অক্সিজেন প্রভৃতি লসিকায় বহন ও লসিকা থেকে কোষে পরিবহন করা ব্যাপন দ্বারা সম্পন্ন হয়।
অভিস্রবণ
অভিস্রবণ প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য আমাদের যে বিষয়ের ধারণা দরকার তার মধ্যে অন্যতম হলো ভিন্ন ঘনত্ব বিশিষ্ট দুইটি দ্রবণের মধ্যে অবস্থিত পর্দার বৈশিষ্ট্য জানা। পর্দাকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, অভেদ্য পর্দা, ভেদ্য পর্দা ও অর্ধভেদ্য পর্দা।
অভেদ্য পর্দা: যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয় প্রকার পদার্থের অণুগুলো চলাচল করতে পারে না তাকে অভেদ্য পর্দা বলে। আরো সহজ ভাষায় বললে , যে পর্দা দিয়ে পর্দা ভেদ করে কোন কিছু আসা এবং যাওয়া সম্ভব হয় না তাকে ভেদ্য পর্দা বলে । যেমন- পলিথিন, কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর।
ভেদ্য পর্দা: যে পর্দা দিয়ে দ্রাবক ও দ্রাব উভয়েরই অণু সহজে চলাচল করতে পারে তাকে ভেদ্য পর্দা বলে। অর্থাৎ যে পর্দা ভেদ করে সহজেই কোন কিছু যাওয়া এবং আসা সম্ভব হয় তাকে ভেদ্য পর্দা বলে । যেমন- কোষপ্রাচীর।
অর্ধভেদ্য পর্দা: যে পর্দা দিয়ে কেবল দ্রবণের দ্রাবক অণু (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) চলাচল করতে পারে কিন্তু দ্রাব অণু চলাচল করতে পারে না তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে। অর্থাৎ যে পর্দা ভেদ করে কোন কিছু প্রবেশ করতে পারে কিন্তু আর ফেরত আসতে পারে না তাকে অর্ধভেদ্য পর্দা বলে । যেমন- কোষপর্দা, ডিমের খোসার ভিতরের পর্দা, মাছের পটকার পর্দা ইত্যাদি।
যদি একটা শুকনা কিশমিশকে পানিতে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখি তাহলে সেটি ফুলে উঠে। এটি কিশমিশ দ্বারা পানি শোষণের কারণে ঘটে এবং পানি শোষণ অভিস্রবণ দ্বারা ঘটে। অভিস্রবণও এক প্রকার ব্যাপন। অভিস্রবণ কেবলমাত্র তরলের ক্ষেত্রে ঘটে এবং একটি অর্ধভেদ্য পর্দা অভিস্রবণের সময় দুটি তরলকে পৃথক করে রাখে। আরো সহজ করে বললে , কিশমিশের ভেতর অর্ধভেদ্য পর্দা ভেদ করে পানি প্রবেশ করেছে ঠিকই কিন্তু সেই পানি আর কিশমিশ থেকে বের হতে পারে না । এটাই মূলত অভিস্রবণ ।
যে প্রক্রিয়ায় একই পদার্থের কম ঘনত্ব এবং বেশি ঘনত্বের দুটি দ্রবণ অর্ধভেদ্য পর্দা দ্বারা পৃথক করা হলে দ্রাবক পদার্থের অণুগুলো কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে অধিক ঘনত্বের দ্রবণের দিকে যায় তাকে অভিস্রবণ বা অসমোসিস বলে ।
অভিস্রবণের গুরুত্ব : জীবকোষের কোষাবরণ বা প্লাজমা পর্দা অর্ধভেদ্য পর্দা হিসেবে কাজ করে। প্লাজমা পর্দা দিয়ে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় মাটিস্থ পানি মূলরোমের মধ্যে প্রবেশ করে এবং মূলরোম থেকে উদ্ভিদের সম্পূর্ণ অংশে প্রবাহিত হয় । এতে কোষস্থিত পানি খনিজ লবণকে দ্রবীভূত করে কোষ রসে পরিণত হয়। সুতরাং কোষের মধ্যে বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলোকে সচল রাখার জন্য অভিস্রবণের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদ কোষের রসস্ফীতি ঘটে। কান্ড ও পাতাকে সতেজ এবং খাড়া রাখতে সাহায্য করে। ফুলের পাপড়ি বন্ধ বা খুলতে পারে। তাছাড়া প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষিত হতে পারে।
উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ
উদ্ভিদের পানি শোষণ পদ্ধতি: মাটি থেকে পানি ও পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ উদ্ভিদ দেহের সজীব কোষে টেনে নেওয়ার পদ্ধতিকে সাধারণভাবে শোষণ বলা যেতে পারে। স্থলে বসবাসকারী উদ্ভিদগুলো মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে। পানিতে নিমজ্জিত উদ্ভিদ সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে। স্থলজ উদ্ভিদগুলোর মূলরোম মাটির সুক্ষ্নকণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় নিজ দেহে টেনে নেয়।
মূলরোমের প্রাচীরটি ভেদ্য, তাই প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় পানি শোষণ করে এবং কোষপ্রাচীরের নিচে অবস্থিত অর্ধভেদ্য প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে আসে। মূলরোমের কোষীয় দ্রবণের ঘনত্বের তুলনায় তার পরিবেশের দ্রবণের ঘনত্ব কম থাকায় পানি (দ্রাবক) কোষের মধ্যে অন্তঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করে। মূলের বাইরের আবরণ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব কোষের কোষ রসের ঘনত্ব সমান নয়। ফলে কোষান্তর অভিস্রবণের কারণে মূলের এক কোষ থেকে অন্য কোষে পানির গতি অব্যাহত থাকে এবং পরিশেষে পানি কান্ডের জাইলেম বাহিকার মাধ্যমে পাতায় পৌঁছায়।
ইমবাইবিশন: অধিকাংশ কলয়েডধর্মী পদার্থই পানিগ্রাহী। উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন ধরনের কলয়েডধর্মী পদার্থ বিদ্যমান। যথা- স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি। এসব পদার্থ তাদের কলয়েডধর্মী গুণের জন্যই পানি শোষণ করতে সক্ষম। কলয়েডধর্মী বিভিন্ন পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষপ্রাচীর) যে প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের তরল পদার্থ (উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পানি) শোষণ করে তাকে ইমবাইবিশন বলে।
কলয়েডধর্মী পদার্থ : যেসব পদার্থের পানি শোষণ ক্ষমতা আছে তাদেরকে কলয়েডধর্মী পদার্থ বলে। কলয়েড পদার্থ পানিগ্রাহী। স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন ইত্যাদি পানি শোষণ করতে পারে। এ কারণে স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিনকে কলয়েডধর্মী পদার্থ বলে।
উদ্ভিদের খনিজ লবণ শোষণ পদ্ধতি : উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য কতগুলো খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণের উৎস মাটিস্থ পানি। মাটিস্থ পানিতে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। খনিজ লবণগুলো মাটিস্থ পানিতে দ্রবীভূত থাকলেও পানি শোষণের সঙ্গে উদ্ভিদের লবণ শোষণের কোনো সম্পর্ক নেই, দুটি প্রক্রিয়াই ভিন্নধর্মী। উদ্ভিদ কখনো লবণের সম্পূর্ণ অণুকে শোষণ করতে পারে না। লবণগুলো কেবল আয়ন হিসেবে শোষিত হয়। উদ্ভিদ মাটির রস থেকে খনিজ লবণ শোষণ দুইভাবে সম্পন্ন করে। যথা- ১. নিষ্ক্রিয় শোষণ; ২. সক্রিয় শোষণ।
প্রস্বেদন
প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন উদ্ভিদের একটি বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। আমরা জানি , উদ্ভিদের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের জন্য পানি অপরিহার্য। তাই উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে প্রচুর পরিমাণ পানি শোষণ করে। শোষিত পানির কিছু অংশ উদ্ভিদ তার বিভিন্ন বিপাকীয় কাজে ব্যবহার করে এবং বাকি অংশ বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পরিত্যাগ করে। উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তর থেকে পাতার মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানির এই নির্গমনের প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন বলে।
প্রস্বেদন প্রধানত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে হয়। এছাড়া কান্ড ও পাতার কিউটিক্স এবং কান্ডের ত্বকে অবস্থিত লেন্টিসেল নামক এক বিশেষ ধরনের অঙ্গের মাধ্যমেও অল্প পরিমাণ প্রস্বেদন হয়। প্রস্বেদন কোথায় সংঘটিত হচ্ছে তার ভিত্তিতে প্রস্বেদন তিন প্রকার যথা- ১. পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন , ২. ত্বকীয় বা কিউটিকুলার প্রস্বেদন এবং ৩. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পত্ররন্ধ্র এবং খালি চোখে কান্ডের লেন্টিসেল সহজে দেখা যায়।
পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন : পাতায় , কচিকাণ্ডে , ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ ( Guard cell ) বেষ্টিত এক ধরনের রন্ধ্র থাকে । এদেরকে পত্ররন্ধ্র ( একবচন stoma , বহুবচন stomata ) বলে । এই পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদনকে পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের 90-95 % হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে ।
কিউটিকুলার প্রস্বেদন: কচি কাণ্ড ও পাতায় কিউটিন আস্তরন থাকে। কিউটিনযুক্ত এ আস্তরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদনকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।
লেন্টিকুলার প্রস্বেদন: উদ্ভিদের পরিণত কাণ্ডে সেকেন্ডারী বৃদ্ধির ফলে স্থানে স্থানে ফেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। এ ছিদ্রকে বলে লেন্টিসেল। লেন্টিসেলের মধ্য দিয়ে প্রস্বেদনকে বলা হয় লেন্টিকুলার প্রস্বেদন।
·
কোন ধরনের প্রস্বেদন বেশি হয়: পত্ররন্ধ্রীয় (৯০-৯৫%)।
·
প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় পাতার কোন অংশে বায়ু পানির সাথে মিশে: নিম্নবহিঃত্বকে।
·
সূর্যের প্রখর তাপেও গাছের পাতা গরম হয় না কেন: প্রস্বেদনের জন্য।
·
পত্ররন্ধ্র খোলা বা বন্ধ হয় কি দিয়ে: রক্ষীকোষ দিয়ে।
·
প্রস্বেদন কখন হয়: দিনে।
·
পত্ররন্ধ্র কোন সময় খোলা ও বন্ধ থাকে: দিনের আলোতে খোলা থাকে, রাতে বন্ধ থাকে।
·
বড় গাছের নিচে ঠাণ্ডা লাগে কেন: প্রস্বেদনের জন্য।
·
প্রস্বেদন পরিমাপ করা হয়: পটোমিটার যন্ত্র দিয়ে।
·
শীতকালে প্রস্বেদন কম হয় কেন: পাতা ঝরে যায়।
·
আলোর সাথে প্রস্বেদনের সম্পর্ক: আলো থাকলে সালোক সংশ্লেষণ বেশি হয় বলে প্রস্বেদনও বেশি হয়।
·
প্রস্বেদনের উপর বায়ুর আর্দ্রতা প্রভাব: বায়ুর আর্দ্রতা কম হলে বায়ুর জলীয় বাষ্প ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ফলে প্রস্বেদন বেশি হয়। বায়ুর আর্দ্রতা বেশি হলে প্রস্বেদন কম হয়।
·
বায়ু প্রবাহ বৃদ্ধি পাইলে → প্রস্বেদন বৃদ্ধি পায় (জলীয় বাষ্প কমে যায় বলে)
·
প্রস্বেদনের উপর বায়ুর চাপের প্রভাব: বায়ুর চাপ কম হলে কম তাপেই পানি বাষ্পে পরিণত হয় ফলে প্রস্বেদন বৃদ্ধি পায়।
·
কলার চারা লাগানোর সময় পাতা কেটে ফেলা হয় কেন: প্রস্বেদন রোধ করার জন্য।
প্রস্বেদনের গুরুত্ব : উদ্ভিদ জীবনে প্রস্বেদন একটি অনিবার্য প্রক্রিয়া। প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদদেহ থেকে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বেরিয়ে যায়। এতে উদ্ভিদের মৃত্যুও হতে পারে। তাই আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদের জীবনে প্রস্বেদনকে ক্ষতিকর প্রক্রিয়া বলেই মনে হয়। এজন্য প্রস্বেদনকে বলা হয় উদ্ভিদের জন্য এটি একটি "Necessary
evil", তবুও প্রস্বেদন উদ্ভিদ জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ তার দেহ থেকে পানিকে বের করে অতিরিক্ত পানির চাপ থেকে মুক্ত করে। প্রস্বেদনের ফলে কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কোষরসের ঘনত্ব বৃদ্ধি অন্তঃঅভিস্রবণের সহায়ক হয়ে উদ্ভিদকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদদেহকে ঠান্ডা রাখে এবং পাতার আর্দ্রতা বজায় রাখে। প্রস্বেদনের ফলে খাদ্য তৈরির জন্য পাতায় অবিরাম পানি সরবরাহ সম্ভব হয়। পাতায় প্রস্বেদনের ফলে জাইলেম বাহিকায় পানির যে টান সৃষ্টি হয় তা মূলরোম কর্তৃক পানি শোষণ ও উদ্ভিদের শীর্ষে পরিবহনে সাহায্য করে। উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া সালোকসংশ্লেষণ ও শ্বসনের মতো পরিবেশে তেমন কোনো প্রভাব রাখে না। তবে পানিচক্রে বাষ্পীভবনে অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের পানি জলীয়বাষ্প হিসেবে বায়ুমন্ডলে প্রেরণ করতে স্থলজ উদ্ভিদের প্রস্বেদন প্রক্রিয়া ভূমিকা রাখে। প্রস্বেদনের ফলে প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে পৌছায়।
পানি ও খনিজ লবণের পরিবহন
জামরা জেনেছি যে উদ্ভিদ মূলের মূলরোমের সাহায্যে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে। এই পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণকে কান্ড এবং শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌঁছানো দরকার। কারণ পাতাই প্রধানত এগুলোকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরির রসদ হিসেবে ব্যবহার করে। আবার পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদ তার দেহের বিভিন্ন অংশে যথা- কান্ড ও শাখা-প্রশাখায় পাঠিয়ে দেয়। উদ্ভিদের মূলরোম দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণ মূল থেকে পাতায় পৌঁছানো এবং পাতায় তৈরি খাদ্যবস্তু সারা দেহে ছড়িয়ে পড়াকে পরিবহন বলে। শোষণের মতো পরিবহন পদ্ধতি ও উদ্ভিদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। জাইলেম ও ফ্লোয়েম নামক পরিবহন টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদে পরিবহন ঘটে। জাইলেমের মাধ্যমে মূল দ্বারা শোষিত পানি পাতায় যায় এবং ফ্লোয়েম দ্বারা পাতায় উৎপন্ন তরল খাদ্য সারা দেহে পরিবাহিত হয়। সুতরাং জাইলেম ও ফ্লোয়েম হলো উদ্ভিদের পরিবহনের পথ। উদ্ভিদের পরিবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিতভাবে সম্পন্ন হয়-
উদ্ভিদের মূলরোম দিয়ে পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় এবং পানিতে দ্রবীভূত খনিজ লবণ নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে শোষিত হয়ে জাইলেম টিস্যুতে পৌঁছায়। জাইলেমের মাধ্যমে উদ্ভিদদেহে রসের ঊর্ধ্বমুখী পরিবহন হয়। ফ্লোয়েমের মাধ্যমে পাতায় তৈরি খাদ্যরসের উভমুখী পরিবহন হয়। উদ্ভিদের সংবহন বা পরিবহন বলতে প্রধানত উর্ধ্বমুখী পরিবহন এবং নিম্নমুখী পরিবহনকে বোঝায়। মাটি থেকে মূলরোমের দ্বারা শোষিত পানি ও খনিজ লবণের দ্রবণ (রস) জাইলেম বাহিকার মধ্য দিয়ে পাতায় পৌঁছায় ।
অঙ্কুরোদগম | Germination
সাধারণত বীজ থেকে শিশু উদ্ভিদ উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। যথাযথভাবে অঙ্কুরোদগম হওয়ার জন্য মাটি , পানি, তাপ ও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। তবে মাটি ছাড়া ও অঙ্কুরোদগম হতে পারে যেমন- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের অঙ্কুরোদগম হয় জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম যেখানে মাটির প্রয়োজন পড়ে না । অঙ্কুরোদগমকে যথাযথভাবে বোঝার জন্য আমরা একটি ছোলা বীজের অঙ্কুরোদগম বর্ণনা করছি ।
একটি বাটির মধ্যে একটি ফিল্টার পেপার রেখে পানি দিয়ে ভিজিয়ে তার উপর ৮/১০টি ভেজা ছোলার বীজ ৩/৪ দিন ঢেকে রেখে দিলে এগুলো থেকে অঙ্কুর বের হবে। বীজের সূঁচালো অংশের কাছে একটি ছিদ্র আছে, একে মাইক্রোপাইল বা ডিম্বকরন্ধ্র বলে। এর ভিতর দিয়ে ভ্রুণমূল বাইরে বেরিয়ে আসে। অঙ্কুর বের হওয়া বীজটিকে দুই আঙ্গুল দিয়ে সামান্য চাপ দিয়ে ছোলা বীজের আবরণটি সরিয়ে ফেললে হলুদ রঙের একটি অংশ বের হবে, এটিকে আরও একটু চাপ দিলে পুরু বীজপত্র দুটি দুই দিকে খুলে যাবে। এ দুটো যেখানে লেগে আছে সেখানে সাদা রঙের একটি লম্বাটে অঙ্গ দেখা যাবে। এর নিচের দিকের অংশকে ভ্রুণমূল এবং উপরের অংশকে ভ্রুণকাণ্ড বলে।
ভ্রূণকাণ্ডের নিচের অংশকে বীজপত্রাধিকান্ড (এপিকোটাইল) ও ভূণমূলের উপরের অংশকে বীজপত্রাবকাণ্ড (হাইপোকোটাইল) বলে। ভ্রুণমূল , ভ্রুণকাণ্ড ও বীজপত্রকে একত্রে ভ্রুণ এবং বাইরের আবরণটিকে বীজত্বক বলে। বীজত্বক দু'স্তরবিশিষ্ট। বাইরের অংশকে টেস্টা এবং ভিতরের অংশকে টেপমেন বলে।
ছোলা বীজের অঙ্কুরোদগম : এক্ষেত্রে মৃদগত অঙ্কুরোদগম হয়। এ প্রকার অঙ্কুরোদগমে বীজপত্র দু'টি মাটির নিচে রেখে ভ্রুণকাণ্ড উপরে উঠে আসে। বীজ পত্রাধিকাণ্ডের অতিরিক্ত বৃদ্ধি এর কারণ। ছোলাবীজ একটি অসস্যল দ্বিবীজপত্রী বীজ। মাটিতে ছোলা বীজ বুনে পরিমিত পানি, তাপ ও বায়ুর ব্যবস্থা করলে দুই তিন দিনের মধ্যে বীজ হতে অঙ্কুর বের হবে এবং মাটির উপরে উঠে আসবে। পানি পেয়ে বীজটি প্রথমে ফুলে উঠে এবং ডিম্বকরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ভ্রুণমূল বেরিয়ে আসে। এটি ধীরে ধীরে প্রধান মূলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় ধাপে ভ্রুণকাণ্ড মাটির উপরে উঠে আসে। এক্ষেত্রে বীজপত্র দুটি মাটির নিচে থেকে যায়। প্রাথমিক অবস্থায় ভ্রুণ তার খাদ্য বীজপত্র থেকে পেয়ে থাকে।
অঙ্কুরোদগমের প্রকারভেদ : সুপ্তবস্থা কাটিয়ে ভ্রুনের বৃদ্ধি হওয়াকে অঙ্কুরোদগম বলে। অঙ্কুরোদগম মূলত উদ্ভিদের বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়া যার সাহায্যে উদ্ভিদ টিকে আছে এবং বংশবিস্তার করতে পারছে । এই অঙ্কুরোদগম সংঘটিত না হলে উদ্ভিদকূল টিকে থাকত না । আর সমস্ত প্রাণী ও টিকে থাকত পারত না । কারণ প্রাণীকূল উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল । যার ফলস্বরুপ পৃথিবীর অস্তিত্বে প্রাণের সন্ধান আর খুজে পাওয়া যেত না । এই অঙ্কুরোদগম তিন প্রকার যথা : মৃদগত অঙ্কুরোদগম , মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম , জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম ।
মৃদগত অঙ্কুরোদগম : যখন ভ্রূণকান্ড মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে কিন্তু বীজপত্রটি মাটির ভিতরে থেকে যায় তখন তাকে মৃদগত অঙ্কুরোদগম বলে, যেমন- ছোলা, ধান ইত্যাদি।
মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম : যদি বীজপত্রসহ ভ্রূণমুকুল মাটি ভেদ করে উপরে উঠে আসে তখন তাকে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম বলে। কুমড়া, রেড়ী, তেঁতুল ইত্যাদি বীজে মৃদভেদী অঙ্কুরোদগম দেখা যায়।
জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম : লবণাক্ত মাটি বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য উপযোগী নয় , তাই এই মাটিতে বসবাসকারী উদ্ভিদের বীজের অঙ্কুরোদগম ফলের মধ্যেই উদ্ভিদের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায় হয় বলে একে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম বলে । যেমন- কেওড়া , সুন্দরী ইত্যাদি ।
এই প্রকার অঙ্কুরোদগমে প্রথমে ফল ভেদ করে বীজের ভ্রুণমূল অংশ বাইরে বেরিয়ে আসে । তারপর বীজ পত্রাবকান্ড বেরিয়ে স্ফীত হয়ে গদার আকৃতি ধারণ করে এবং ফলসহ অঙ্কুরিত বীজটি উদ্ভিদ থেকে বিচ্যুত হয় এবং বীজ পত্রাবকান্ড সহ ভ্রুণমূল মাটিতে গেঁথে যায় এবং ভ্রুণমূল অংশ মাটির উপরে থাকে ।
·
বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান: পানি-তাপ-বায়ু।
·
ছোলাবীজে মৃৎগত ধরনের অঙ্কুরোদগম হয়।
·
শিমবীজে মৃৎভেদী ধরনের অঙ্কুরোদগম হয়।
·
তামাক বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য অন্ধকার প্রয়োজন।
·
সীম বীজে মৃৎগত অংকুরোদগম হয়।
উদ্ভিদের ফুল ও ফলের বর্ণনা
ফুল
ফুলের বিভিন্ন অংশ
বৃতি: ফুলের সবচেয়ে বাইরের স্তবককে বৃতি বলে। সাধারণত এরা সবুজ রঙের হয়। বৃতি খণ্ডিত না হলে সেটি যুক্ত বৃতি, কিন্তু যখন এটি খণ্ডিত হয় তখন বিযুক্ত বৃতি বলে। এর প্রতি খণ্ডকে বৃত্যাংশ বলে। বৃতি ফুলের অন্য অংশগুলোকে বিশেষত কুঁড়ি অবস্থায় রোদ, বৃষ্টি ও পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে।
দলমণ্ডল: এটি বাইরের দিক থেকে দ্বিতীয় স্তবক। কতগুলো পাপড়ি মিলে দলমণ্ডল গঠন করে। এর প্রতিটি অংশকে পাপড়ি বা দলাংশ বলে। পাপড়িগুলো পরস্পর যুক্ত (যেমন-ধূতরা) অথবা পৃথক (যেমন-জবা) থাকতে পারে। এরা বিভিন্ন রঙের হয়। দলমণ্ডল রঙিন হওয়ায় পোকা-মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।
পুংস্তবক বা পুংকেশর: এটি ফুলের তৃতীয় স্তবক। এই স্তবকের প্রতিটি অংশকে পুংকেশর বলে। পুংকেশরের দন্ডের মতো অংশকে পুংদন্ড এবং শীর্ষের থলির মতো অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। পরাগরেণু থেকে পুং জননকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।
স্ত্রীস্তবক বা গর্ভকেশর: এটি ফুলের চতুর্থ স্তবক। এক বা একাধিক গর্ভপত্র নিয়ে একটি স্ত্রীস্তবক গঠিত হয়। একের অধিক গর্ভপত্র সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকলে তাকে যুক্তগর্ভপত্রী, আর আলাদা থাকলে বিযুক্তগর্ভপত্রী বলে। একটি গর্ভপত্রের তিনটি অংশ, যথা- গর্ভাশয়, গর্ভদণ্ড ও গর্ভমুন্ড। গর্ভাশয়ের ভিতরে ডিম্বক সাজানো থাকে। ডিম্বকে স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। এরা পুংস্তবকের মতো সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে। বৃতি ও দলমণ্ডলকে ফুলের সাহায্যকারী স্তবক এবং পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবককে অত্যাবশ্যকীয় স্তবক বলে।
পুষ্পমঞ্জরি : কান্ডের শীর্ষমুকুল বা কাক্ষিক মুকুল থেকে উৎপন্ন একটি শাখায় ফুলগুলো বিশেষ একটি নিয়মে সাজানো থাকে। ফুলসহ এই শাখাকে পুষ্পমঞ্জরি বলে। পরাগায়নের জন্য এর গুরুত্ব খুব বেশি। এ শাখার বৃদ্ধি অসীম হলে অনিয়ত পুষ্পমঞ্জরি ও বৃদ্ধি সসীম হলে তাকে নিয়ত পুষ্পমঞ্জরি বলে।
ফলের উৎপত্তি
আমরা ফল বলতে সাধারণত আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা, আঙুর, আপেল, পেয়ারা, সফেদা ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলগুলোকে বুঝি। এগুলো পেকে গেলে রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়। লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটল ইত্যাদি সবজি হিসেবে খাওয়া হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো সবই ফল। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয়। এর ডিম্বকগুলো বীজে রুপান্তরিত হয়। নিষিক্তকরণের পর গর্ভাশয় এককভাবে অথবা ফুলের অন্যান্য অংশসহ পরিপুষ্ট হয়ে যে অঙ্গ গঠন করে তাকে ফল বলে।
শুধু গর্ভাশয় ফলে পরিণত হলে তাকে প্রকৃত ফল বলে, যেমন- আম, কাঁঠাল। গর্ভাশয় ছাড়া ফুলের অন্যান্য অংশ পুষ্ট হয়ে যখন ফলে পরিণত হয় তখন তাকে অপ্রকৃত ফল বলে, যেমন-আপেল, চালতা ইত্যাদি। প্রকৃত ও অপ্রকৃত ফলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- সরল ফল, গুচ্ছ ফল ও যৌগিক ফল।
১) সরল ফল: ফুলের একটি মাত্র গর্ভাশয় থেকে যে ফলের উৎপত্তি তাকে সরল ফল বলে, যেমন- আম। এরা রসাল বা শুষ্ক হতে পারে। সরল ফল দুই প্রকার।
রসাল ফল: যে ফলের ফলত্বক পুরু এবং রসাল তাকে রসাল ফল বলে। এ ধরনের ফল পাকলে ফলত্বক ফেটে যায় না। যেমন- আম, জাম, কলা ইত্যাদি।
নীরস ফল : যে ফলের ফলত্বক পাতলা এবং পরিপক্ক হলে ত্বক শুকিয়ে ফেটে যায় তাকে নীরস ফল বলে। যেমন-শিম, ঢেঁড়স, সরিষা ইত্যাদি।
২) গুচ্ছ ফল: একটি ফুলে যখন অনেকগুলো গর্ভাশয় থাকে এবং প্রতিটি গর্ভাশয় ফলে পরিণত হয়ে একটি বোঁটার উপর গুচ্ছাকারে থাকে তখন তাকে গুচ্ছ ফল বলে, যেমন- চম্পা, নয়নতারা, আকন্দ, আতা, শরীফা ইত্যাদি।
৩) যৌগিক ফল: একটি মঞ্জরির সম্পূর্ণ অংশ যখন একটি ফলে পরিণত হয় তখন তাকে যৌগিক ফল বলে, যেমন- আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি ।
আদর্শ ফল : আদর্শ ফলের তিনটি অংশ -বহিঃত্বক, মধ্যত্বক ও অন্তঃত্বক। যেমন - লিচু। পৃথিবীতে সর্বাধিক উৎপাদিত হয় কলা। পাকা কলায় অ্যামাইল অ্যাসিটেট থাকে। সবচেয়ে সুস্বাদু ফল হল আম। ফল পাকার জন্য দায়ী ইথিলিন, হলুদ রংয়ের জন্য কার্যকর জ্যান্থোফিল, সবুজ রঙের জন্য ক্লোরোফিল।
সব ফুল থেকে ফল হয় না কেন?
ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বা পুংরেণু ফুলের গর্ভমুণ্ড হয়ে গর্ভাশয়ে পৌঁছায় এবং সেখানে ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়ে পরবর্তীতে ফল সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ পুরো প্রক্রিয়াটি কোন কারণে বাধাগ্রস্ত হলে ফল সৃষ্টি হয় না। অনেক সময় গর্ভমুণ্ডের শুষ্কতার জন্য পরাগরেণু অংকুরিত হয় না। আবার পরাগনালী কখনো এত ছোট হয় যে, তা ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না - এ রকম নানা কারণে ফুল হলেও গাছে ফল হয় না।
পারথেনোর্কাপী ফলোৎপাদন : সাধারণ অবস্থায় উদ্ভিদের ফলের উৎপত্তি পরাগযোগ ও নিষেকের মাধ্যমে ঘটে। কিন্তু অক্সিন প্রয়োগে পরাগযোগ ব্যতীত ফল উৎপাদন করা যায়। পরাগযোগ ব্যতীত বীজহীন ফল উৎপাদন করাকে পারথেনোর্কাপী বা বীজহীন ফলোৎপাদন বলা হয়। অক্সিন প্রয়োগে শশা, আঙ্গুর, টমেটো প্রভৃতি ফল উৎপাদন করা সম্ভব।
ফটোপিরিওডিজম
ফটোপিরিওডিজম: উদ্ভিদের ফুল ধারণের উপর দিবালোকের দৈর্ঘ্যের প্রভাবকে ফটোপিরিওডিজম বলে। অ্যালার্ড (
Allard) ১৯২০ সালে উদ্ভিদের পুষ্প ধারনের উপর ভিত্তি করে এই নামকরণ করেন । ফটোপিরিওডিজমের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে । যথা--
ছোট দিনের উদ্ভিদ: দিনের দৈর্ঘ্য ছোট হলে এ ধরনের উদ্ভিদে ফুল ফোটে। যেমন- সয়াবিন, আলু, ইক্ষু, কসমস, শিম, ডালিয়া, তামাক, চন্দ্রমল্লিকা, রোপা আমন, পাট। এদের দীর্ঘরাত্রির উদ্ভিদও বলা হয়।
বড়দিনের উদ্ভিদ: দিনের দৈর্ঘ্য বড় হলে এ জাতীয় ফুল ফোটে। যেমন- ঝিঙ্গা, লেটুস, পালংশাক, আফিম, যব। এদের ছোট রাত্রির উদ্ভিদও বলা হয়।
দিন নিরপেক্ষ উদ্ভিদ: দিনের আলোর সময় সীমার উপর উদ্ভিদের ফুল ধারণ নির্ভর করেনা। যেমন- সূর্যমূখী, টমেটো, শসা, কার্পাস, আউস ধান।
ভার্নালাইজেশন
যে প্রক্রিয়ার দ্বারা বীজ বপনের আগে প্রয়োজনমত নিম্ন বা উচ্চতাপ প্রয়োগ করে স্বাভাবিক সময়কালের পূর্বে উদ্ভিদের ফুল ধরানো হয় তাকে ভার্নালাইজেশন বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে এক দেশের উদ্ভিদকে স্বাভাবিকভাবে অন্য দেশের ভিন্ন আবহাওয়া এবং জলবায়ুতে জন্মানো সম্ভবপর নয়। কিন্তু ভার্নালাইজেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে কোন উদ্ভিদকে যে কোন আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপযোগী করে যেকোন স্থানে জন্মানো যেতে পারে।
অনুশীলন অধ্যায়
১. উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ হতে পানি হারানোর জন্য দায়ী কে ? [মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদর্শক ২০১৩ ]
·
শ্বসন
·
ব্যাপন
·
নিষেক
·
শোষণ
২. ‘অসমোসিস’ শব্দটির অর্থ কী ? [প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে ভিএফ/ এফ এ/ কম্পাউন্ডার পদে নিয়োগ পরীক্ষা- ২০২০ ]
·
ব্যাপন
·
অভিস্রবণ
·
পানি শোধণ
·
প্রস্বেদন
৩. উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে পানি শোষণ করে কোন প্রক্রিয়ায় ? [দুর্নীতি দমন কমিশনের অধীনে সহকারী পরিচালক পদে নিয়োগ পরীক্ষা-২০২০ ]
·
শ্বসন
·
ব্যাপন
·
ইমবাইবিশন
·
অভিস্রবণ
৪. সূর্যের প্রখর উত্তাপেও গরম হয় না কোনটি ? [তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৩ / জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১২/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রকৌশলী, মেকানিক্যাল এন্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংঃ ৯৯ ]
·
গাছের পাতা
·
বায়ুমণ্ডল
·
গাছের ফল
·
মাটি
৫. শীত বা গ্রীষ্মের পূর্বে গাছের পাতা ঝরে যায় কেন ? [ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষকঃ ০১/ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে সহকারী পরিচালকঃ ৯৪]
·
খাদ্যের অভাবে
·
শ্বসনের হার কমাতে
·
অভিস্রবণ কমাতে
·
প্রস্বেদন কমাতে
৬. শীতকালে প্রস্বেদন কম হয়, কারণ- [ থানা নির্বাচন অফিসার :
০৪]
·
আর্দ্রতা কম থাকে
·
পত্ররন্ধ্র বন্ধ থাকে
·
পাতা ঝরে যায়
·
সবগুলোই
৭. কলার চারা লাগানোর সময় পাতা কেটে ফেলা হয় কেন ? [মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা মহিলা কর্মকর্তাঃ ০৫/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী পরিদর্শকঃ ০৫/ সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারঃ ০৪/ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী শ্রম অফিসারঃ ০৩/ থানা শিক্ষা অফিসারঃ ১৬ ]
·
প্রস্বেদন রোধ করার জন্য
·
শ্বসন বন্ধ করার জন্য
·
অভিস্রবণ ত্বরান্বিত করার জন্য
·
সালোকসংশ্লেষণের উপযোগী করে তোলার জন্য
৮. প্রস্বেদন পাতার একটি- [ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা-২০১৪ ]
·
বিশেষ কাজ
·
স্বাভাবিক কাজ
·
অসম্পূর্ণ কাজ
·
আদৌ পাতার কাজ নয়
·
কোনোটিই নয়
৯. ২. উদ্ভিদ কোষ থেকে বাষ্পাকারে পানি বের হয়ে যাওয়ার প্রণালীকে বলে- [প্রাক-প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা-২০১৩/(প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১২ যমুনা/প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা ২০১২ - সিলেট/প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক, - ঢাকা বিভাগঃ ০৭/ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক, খুলনা বিভাগঃ ০৬ ]
·
প্রস্বেদন
·
বাষ্পীভবন
·
শ্বসন
·
ব্যাপন
১০. ৩. লেন্টিকুলার প্রস্বেদন উদ্ভিদের কোন অংশে হয় ? [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষকঃ ০১ ]
·
মূল
·
পাতা
·
কাণ্ড
·
ফুল