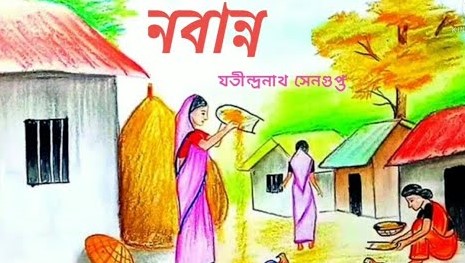নবান্ন (যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)
লেখক-পরিচিতি
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের
বর্ধমান জেলার পাতিলপাড়া গ্রামে ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৬এ জুন জন্মগ্রহণ করেন। ত পিতার
নাম দ্বারকানাথ সেনগুপ্ত । যতীন্দ্রনাথ পেশায় ছিলেন একজন প্রকৌশলী । দুঃখকেই জীবনের
চূড়ান্ত সত্য আর জেনেছিলেন তিনি । মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষের স্বপ্ন
ও বাস্তবের সংঘাতকে তিনি কবিতায় তুলে ধরেছেন। কল্পনাবিলাস কিংবা ভাবালুতায় ছিল তাঁর
চরম অবিশ্বাস । নতুন ধরনের কবিতা রচনা করে রবীন্দ্রনাথের অনুসারী কবিলেন নতুন দৃষ্টি
দিয়ে চারপাশের জগৎকে দেখার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি । তাঁর এই নবীন দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তীকালের
আলোর কবিকেই প্রভাবিত করেছিল । বিষয় ও গঠনের দিক থেকে তিনি কবিতাকে ঢেলে সাজাতে আগ্রহী
ছিলেন । একেবারে দৈনন্দিন জীবনের নানাকিছু যে শিল্পের সীমা লঙ্ঘন না করেও অনায়াসে
কাব্য-বিষয় হতে পারে তার পরিচয় রয়েছে তাঁর কাব্যে । সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যে স্থান
পেয়েছে গদ্যসুলভ শব্দ ও উপমার অভিনবত্ব। তাঁর কবিতার বক্তব্য যেমন সমকালীন সাহিত্যিকদের
চমক লাগিয়েছিল তেমনি তাঁর বলার ভঙ্গি পাঠককে করেছিল মুগ্ধ। যতীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ
'মরীচিকা'। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'মরুশিখা', 'মরুমায়া', 'সায়ম',
'ত্রিযামা', 'নিশান্তিকা' প্রভৃতি। শেষ বয়সে তিনি "হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'ওথেলো',
'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্যের অনুবাদ করেছিলেন । তিনি ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দের
১৭ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন ।
মূল কবিতা
এসেছ বন্ধু? তোমার কথাই জাগছিল ভাই প্রাণে,—
কাল রাতে মোর মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা ধানে ।
ধান্যের ঘ্রাণে ভরা আঘ্রানে শুভ নবান্ন আজ,
পাড়ায় পাড়ায় উঠে উৎসব, বন্ধ মাঠের কাজ ।
লেপিয়া আঙিনা দ্যায় আল্পনা ভরা মরাইএর পাশে;
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য ত্যাজি' এবার নিবসে চাষে ।
এমন বছরে রাতারাতি মোর পাকা ধানে পড়ে মই !
দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসো, সে দুখের কথা কই;
বোশেখ, জ্যষ্টি, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্দর, আশ্বিন,
আশা-আতঙ্কে খেয়াল ছিল না কোথা দিয়ে কাটে দিন ।
দুর্যোগে সবে বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা,
বুকের রক্ত জল কোরে কভু সেচিনু পাণ্ডু চারা ।
কার্তিকে দেখি চারিদিকে, একি! এবার ত নহে ফাঁকি!
পাঁচরঙা ধানে ছক-কাটা মাঠ জুড়ায় চাষার আঁখি ।
অঘ্রানে থাকে থাকে
কাটিয়া তোলায় খামারে গোলায় যাহার যেমন পাকে ।
আমি রোজ ভাবি— ফসলটা নাবি, আরও ক'টা দিন
যাক,
ভরা অঘ্রানে ঘটেনা ত কোনো দৈব দুর্বিপাক ।
মরাই-সারাই শেষ কোরে, সবে খামারে দিইছি হাত, কালুকে হঠাৎ-
বন্ধু, দোহাই, তুলোনাকো হাই, হইনু অপ্রগল্ভ, -
ক্ষমা করো সখা,— বন্ধ করিনু তুচ্ছ ধানের গল্প ।
শব্দার্থ ও টীকা
নবান্ন - ফসল কাটার
উৎসব। গ্রাম-বাংলায় প্রতিবছর হেমন্তকালে ঘরে ফসল তোলার উপলক্ষে নাচ-গানসহ নতুন ধানে
তৈরি নানারকম খাবারের আয়োজনের মধ্য দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশে পালিত হয় নবান্ন উৎসব ।
মই প'ড়ে গেছে ক্ষেতভরা পাকা
ধানে" - পাকা ধানে মই দেওয়া" একটি বাংলা প্রবাদ । এর অর্থ হলো প্রায়সম্পন্ন
কোনো কাজ পণ্ড করা। অন্যের ক্ষতি করা। জমিতে মই দেওয়া হয় বীজ বোনা কিংবা চারা লাগানোর
আগে; মাটিকে নরম ঝুরঝুরে করার জন্য । কিন্তু যে জমি ফসলে পূর্ণ, যখন ফসল কাটার সময়
আসন্ন তখন মই দিলে তো সব ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতি বোঝাতে ব্যবহৃত এই প্রবাদটিকে কবি
কৌশলে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন।
আল্পনা - গ্রামে বিভিন্ন
উৎসব উপলক্ষে বাড়ির আঙিনায় হাতে আঁকা নকশা। ঐতিহ্যগতভাবে আতপ চাল বেটে তার সঙ্গে
প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল এবং নানারকম রং মিশিয়ে আপনার উপকরণ প্রস্তুত করা হয়। ইদানীং
সিনথেটিক রং দিয়েও আল্পনা আঁকা হয় ।
মরাই - হোগলা, বেত ইত্যাদি
দিয়ে তৈরি শস্য জমা রাখার বড় আধার।ধানের গোলা।
লক্ষ্মী বোধ হয় বাণিজ্য
ত্যাজি এবার নিবসে চাষে - প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে— “বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"।
অর্থাৎ, ব্যবসায়- বাণিজ্যে প্রচুর অর্থলাভ হয় তথা ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর আগমন
ঘটে । আলোচ্য কবিতায় কবি প্রবাদটিকে পাল্টে দিয়েছেন। কবিতায় বর্ণিত কৃষকের মাঠে
এবার এমন ফসল হয়েছে যে, কৃষকের মনে হচ্ছে লক্ষ্মী দেবী এবার বাণিজ্যের পরিবর্তে ফসলের
ক্ষেতে বিরাজ করছেন। আর তাই প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কৃষককে আনন্দ-স্বপ্নে বিভোর
করছে।
দাওয়া - ঘরের আঙ্গিনা
বালির বাঁধনে বাঁধিনু বন্যাধারা
- বাংলা প্রবাদ "বালির বাধ"কবি শৈল্পিকভাবে এই কবিতায় ব্যবহার করেছেন।
“বালির বাঁধ”-এর
অর্থ হলো এমন কিছু যা ক্ষণভঙ্গুর বাঁচানোর লক্ষ্যে সকল দুর্যোগ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে
নিজের যথাসাধ্য চেষ্টাকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু তার সবই বালির বাঁধের মতো শেষ পর্যন্ত
বিফলে গেছে।
বুকের রক্ত জল করে কভু সেচিনু
পান্ডু চারা - কৃষকের ফসল ফলানোর অপরিহার্য শর্ত হলো পর্যাপ্ত জলসেচের ব্যবস্থা। এদেশের
প্রেক্ষাপটে এই সেচ ব্যবস্থাও কখনও হয়ে ওঠে অনিশ্চিত। নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে
বাংলার কৃষক তার ফসলের মাঠ সেচ দিয়ে সজীব রাখে। মলিন মৃতপ্রায় চারাকে বাঁচিয়ে রাখার
প্রাণপণ শ্রম ঢালে ।
পাণ্ডু - ফ্যাকাশে মলিন।
নাবি - দেরিতে হয় এমন
দুর্বিপাক - বিপদ। দুর্যোগ।
অপ্রগলভ - অচঞ্চল বিনয়ী,
আচরণে শালীন।
পাঠ-পরিচিতি
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "নবান্ন" কবিতাটি তাঁর
'মরুমায়া' গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে । একদিকে বাংলার কৃষকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের
বেদনাময় বাস্তবতা এই কবিতায় শিল্প অবয়ব লাভ করেছে; অপরদিকে, 'কৃষক' আর ‘পাকা ধান'-এর
প্রতীকে কবির আপন সৃষ্টির ধ্বংস হওয়ার বেদনা দ্যোতিত হয়েছে ।
জনৈক বন্ধুর সঙ্গে কবি তাঁর মনের দুঃখকথা বলে চলেছেন –
এমন ভঙ্গি ব্যবহার করে কবিতাটির সূচনা । কবির সেই বেদনা-কাহনে উঠে এসেছে তাঁর ক্ষেতভরা
পাকা ধান কীভাবে এক রাতে ধ্বংস হয়ে গেছে সেই কথা। ফসল কাটার সময় সমাগত বিবেচনা করে
কৃষক কবির বাড়ি সেজে উঠেছিল আল্পনায়, গোলাঘর মেরামত করে। ধান সংগ্রহের সকল আয়োজন
হয়েছিল সম্পন্ন । একদিকে বাড়িতে এতসব আয়োজন আর অন্যদিকে মাঠে ফসল কাটার প্রতীক্ষা
। এ যেন বাংলার কৃষক-জীবনের অকৃত্রিম রূপায়ণ কৃষকেরা মাসের পর মাস ধরে রক্ত জল করা
শ্রমে চারাগাছ থেকে তিল তিল করে বড় করে তোলে পাকা ধান এই সময় জুড়ে বিভিন্ন প্রকৃতিসৃষ্ট
ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের আশঙ্কায় দুলে ওঠে তাদের হৃদয় তবু তারা স্বপ্ন দেখে, বিভোর
হয় আসন্ন সুখময় দিনের কল্পনায় । কবিও একইভাবে ধান কাটার অপেক্ষায় দিন গুনেছেন অগ্রহায়ণ
মাসে দুর্বিপাক ঘটার শঙ্কা না থাকায় ভেবেছেন ফসলগুলো আরেকটু পরিপক্ক হলে তবে কাটবেন।
কিন্তু তার আগেই তাঁর পাকা ধানে মই পড়ে গেছে। কিন্তু মই দেওয়া তো কোনো প্রাকৃতিক
দুর্যোগ নয়। তবে কি কবি কারও শত্রুতার শিকার? এই প্রশ্নের উত্তর কবিতায় নেই ৯ এর
কারণ অনুসন্ধানের তাগিদ তিনি অনুভব করেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির দুঃখ শেষ হয় না।
কবির এই কষ্টের কথা শোনার ধৈর্যও কারও হয় না। কবির বন্ধুর অসহিষ্ণুতা থামিয়ে দেয়
কবিকে। ফসল হারিয়ে নিঃস্ব হওয়ার এই অমোঘ বাস্তবতা শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় এক অসমাপ্ত
গল্পে। এভাবেই বেদনার রেশ টেনে নবান্নের আনন্দ মুছে দিয়ে সমাপ্ত হয় কবিতাটি।
কবিতাটির একটি প্রতীকী তাৎপর্যও লক্ষণীয়। 'পাকা ধান'-এর
প্রতীকে, কৃষকের রূপকল্পে যতীন্দ্রনাথ আপন সৃষ্টিকে আরও নিজের করে পেতে চান। কিন্তু
সেই সৃষ্টিকর্ম যখন সমালোচিত হয়, সঠিকভাবে মূল্যায়িত হয় না। তখন কবি বেদনাহত হন।
পাকা ধান নষ্ট হওয়া হৃতসম্বল কৃষকের সঙ্গে নিজের সাদৃশ্য খুঁজে পান তিনি । এভাবে এক
স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যতীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবকে শিল্পায়িত করেছেন আলোচ্য “নবান্ন”
কবিতায় ।
কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। এর পর্ব বিভাগ মুখ্যত
৬+৬+৬+২। অর্থাৎ, চরণের শেষে ২ মাত্রার একটি পর্ব বিদ্যমান। অবশ্য কোনো কোনো চরণে এর
ব্যতিক্রমও
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
১. 'নবান্ন' কবিতায় কবি কোথায় বসে তার বন্ধুকে গল্প শোনার
কথা বলেছেন।
ক. ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে
খ. দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়ে
ঘ. বারান্দায় রাখা মানুরে বসে
গ. বসার ঘরের চেয়ারে বসে
২. 'দৈব-দুর্বিপাক' বলতে কোন ধরনের দুর্যোগকে বোঝানো হয়েছে?
ক. প্রাকৃতিক
খ. দেবতাসৃষ্ট
গ. আকস্মিক
ঘ. মানবসৃষ্ট
নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।
আগামীকাল বাঙালির প্রাণের
উৎসব বাংলা নববর্ষ। করতোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ উদ্দীপনার শেষ
নেই। সবাই মিলে আজ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তাটি আলপনায় তরে তুলতে কাজে নেমেছে। ছোট ছোট
হাত, কচি মন আর নানা রংয়ের মিশ্রণে রাস্তাটি হয়ে উঠেছে আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের আধার।
কিন্তু সন্ধ্যা বেলার আকস্মিক ঝড়বৃষ্টি কচি মনের সব স্বপ্ন মুছে দেয়।
৩. উদ্দীপকে "নবান্ন" কবিতার যে দিকগুলোর ইঙ্গিত
রয়েছে তা হলো-
i. উৎসবের প্রস্তুতি
ii. স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা
iii. প্রতিহিংসার বহিপ্রকাশ
নিচের কোনটি ঠিক?
ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. iii ও ii
ঘ. i, ii ও iii
৪. উক্ত বক্তব্য পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে "নবান্ন"
কবিতাটিকে কোন শ্রেণিভুক্ত করা যায়?
ক. সংলাপধর্মী
গ. প্রতীকধর্মী
খ. কাহিনিধর্মী
ঘ. রূপকাশ্রয়ী
সৃজনশীল প্রশ্ন
অকালে ঝরে গেল একটি স্বপ্ন
নিজস্ব প্রতিবেদক, দৈনিক
সর্পণ ও অগৈলঝাড়া, বরিশাল। তারিখ। ১৫/০৫/২০১৬
এক নিমেষেই চুরমার হলো ধনঞ্জয়ের
দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। চিকিৎসার অভাবে স্ত্রীর মৃদ্ধার পর একমাত্র সন্তান মৃত্যুভয়কে
অনেক বড় ডাক্তার বানানোর প্রতায় গ্রহণ করেন তিনি। উদ্দেশ্য, তার স্ত্রীর মতো আর কেউ
যেন অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা না যায়। অন্যের জমিতে কাজ করে কখনোবা এলাকার ছোট
ছোট ছেলে-মোয়াক পড়িয়ে ছেলের পড়াশোনার খরচ জুগিয়েছেন ধনঞ্জয়। গতকাল তিনি জানতে পেরেছেন
যে, ছেলে তার ডাক্তারি পাস করেছে। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন এবায় পূরণ হবে। কিন্তু স্বপ্ন
তাঁর চুরমার হয়ে গেল।
সড়ক দুর্ঘটনা কেড়ে নিল মৃত্যুঞ্জয়ের
প্রাণ।
ক "নবত্র' কবিতায় কোথায়
আলপনা আঁকার কথা বলা হয়েছে।
খ. 'মই পড়ে গেছে ক্ষেততরা
পাকা ধানে'। বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
গ. উদ্দীপকে ধনঞ্জয়ের মধ্যে
"কযন্ত্র' কবিতার যে দিকটির আভাস পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।
ঘ. 'ভাবগত সাদৃশ্য বাকলের
উদ্দীপক ও "নবদ্রে" কবিতার মূল বক্তযোর পার্থক্য অনেক মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর