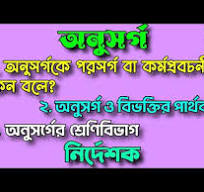অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়,ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব
অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয়
বাংলা ভাষায় যে অব্যয় শব্দগুলো কখনো স্বাধীন পদ রূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, সেগুলোকে অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে।
অনুসর্গগুলো কখনো প্রাতিপদিকের পরে ব্যবহৃত হয়, আবার কখনো বা ‘কে’ এবং ‘র’ বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে বসে। যেমন-
বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? (প্রাতিপদিকের পরে
সনে : ময়ূরীর সনে নাচিছে ময়ূর। (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে
দিয়ে : তোমাকে দিয়ে আমার চলবে না। (দ্বিতীয়ার ‘কে' বিভক্তিযুক্ত শব্দের পরে)
বাংলা ভাষায় বহু অনুসর্গ আছে। যেমন—
প্রতি, বিনা, বিহনে, সহ, ওপর, অবধি, হেতু, মধ্যে, মাঝে, পরে, ভিন্ন, বই, ব্যতীত, জন্যে, জন্য, পর্যন্ত অপেক্ষা, সহকারে, তরে, পানে, নামে, মতো, নিকট, অধিক, পক্ষে, দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক, সঙ্গে, হইতে, হতে, থেকে, চেয়ে, পাছে, ভিতর, ভেতর ইত্যাদি ।
এদের মধ্যে দ্বারা, দিয়া (দিয়ে), কর্তৃক, হইতে (হতে), চেয়ে, অপেক্ষা, মধ্যে প্রভৃতি কয়েকটি অনুসর্গ বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয়। কারক প্রকরণে এদের উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে।
অনুসর্গের প্রয়োগ
১।বিনা/বিনে : কর্তৃ কারকের সঙ্গে – তুমি বিনা (বিনে) আমার কে আছে ?
বিনি : করণ কারকের সঙ্গে – বিনি সুতায় গাঁথা মালা ।
বিহনে : উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?
২.সহ : সহগামিতা অর্থে – তিনি পুত্রসহ উপস্থিত হলেন।
সহিত : সমসূত্রে অর্থে – শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না।
সনে : বিরুদ্ধগামিতা অর্থে – ‘দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।’
সঙ্গে তুলনায় – মায়ের সঙ্গে এ মেয়ের তুলনা হয় না ।
৩. অবধি : পর্যন্ত অর্থে – সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করব।
৪.পরে : স্বল্প বিরতি অর্থে — এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না ।
পর : দীর্ঘ বিরতি অর্থে শরতের পরে আসে বসন্ত ৷
৫. পানে : প্রতি, দিকে অর্থে – ঐ তো ঘর পানে ছুটেছেন
‘
শুধু তোমার মুখের পানে চাহি বাহির হনু।'
৬.মতো
ন্যায় অর্থে – বেকুবের মতো কাজ করো না।
তরে
মত অর্থে - এ জন্মের তরে বিদায় নিলাম ।
৭. পক্ষে সক্ষমতা অর্থে – রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।
সহায় অর্থে –আসামির পক্ষে উকিল কে?
৮. মাঝে মধ্যে অর্থে – ‘সীমার মাঝে অসীম তুমি'।
একদেশিক অর্থে এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল।
ক্ষণকাল অর্থে – নিমেষ মাঝেই সব শেষ ।
মাঝারে : ব্যাপ্তি অর্থে – ‘আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে।
৯.কাছে নিকটে অর্থে – আমার কাছে আর কে আসবে?
কর্মকারকে ‘কে’ বোঝাতে – ‘রাখাল শুধায় আসি ব্রাহ্মণের কাছে।'
১০.প্রতি প্রত্যেক অর্থে – মণপ্রতি পাঁচ টাকা লাভ দেব।
দিকে বা ওপর অর্থে – ‘নিদারুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি।'
১১. হেতু : নিমিত্ত অর্থে –‘কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া । '
জন্যে নিমিত্ত অর্থে – ‘এ ধন-সম্পদ তোমার জন্যে। '
সহকারে : সঙ্গে অর্থে – আগ্রহ সহকারে কহিলেন।
বশত : কারণে অর্থে – দুর্ভাগ্যবশত সভায় উপস্থিত হতে পারিনি।
সাধারণ অনুসর্গ
সাধারণ অনুসর্গ: এধরনের অনুসর্গ পদ ক্রিয়াপদ ব্যতীত অন্য পদগুলো থেকে উৎপন্ন হয়।যেমন: উপরে, কাছে, জন্য, দ্বারা, বনাম।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.সংস্কৃত অনুসর্গ কোনটি?
a)বাদে
b)জন্য
c)তরে
d)সাথে
#.কোথায় অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়েছে?
a) বছরখানেক পরে রেণুকে বিয়ে করে অপু
b) তার চোখে নেই রাগ, অভিমান
c) ক্যাপিটালে আমাদের আলাপ হয়েছিল
d) ভোরে ছেলেবুড়ো এসে জমায়েত হল
#.কোনটি অনুসর্গ?
এর
এরে
তরে
রে
#.অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধুরীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিতরীতিতে সংক্ষিপ্তরূপ-
হয় না
কখনো কখনো হয়
হয়
কখনোই হয় না
#.অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধুরীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিতরীতিতে সংক্ষিপ্ত রূপ-
হয়
কখনো কখনো হয়
হয় না
কখনোই হয় না
ক্রিয়াজাত অনুসর্গ
ক্রিয়াজাত অনুসর্গ: এধরনের অনুসর্গ পদ শুধুমাত্র ক্রিয়াপদ থেকেই উৎপন্ন হয়।যেমন: করে, থেকে, দিয়ে, ধরে, বলে।
ক্রিয়ার কাল
কাল : ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।
১. আমরা বই পড়ি। ‘পড়া’ ক্রিয়াটি এখন অর্থাৎ বর্তমানে সংঘটিত হচ্ছে।
২. কাল তুমি শহরে গিয়েছিলে। ‘যাওয়া’ ক্রিয়াটি পূর্বে অর্থাৎ অতীতে সম্পন্ন হয়েছে।
৩. আগামীকাল স্কুল বন্ধ থাকবে। ‘বন্ধ থাকা' কাজটি পরে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে। সুতরাং, ক্রিয়া, বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হওয়ার সময় নির্দেশই ক্রিয়ার কাল। এ হিসেবে ক্রিয়ার কাল প্রধানত তিন প্রকার : ১. বর্তমান কাল, ২. অতীত কাল এবং ৩. ভবিষ্যৎ কাল।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.'এবার আমি পরীক্ষায় ভালো করেছি কোন কালের উদাহরণ?
সাধারণ অতীত
পুরাঘটিত অতীত
ঘটমান বর্তমান
পুরাঘটিত বর্তমান
#.ভেতরে আসতে পারি কোন কালের উদাহরণ?
ঘটমান বর্তমান
বর্তমান অনুজ্ঞা
সাধারণ বর্তমান
ঘটমান বর্তমান
#.'বৃষ্টি আসে আসুক- এটি কোন প্রকার ক্রিয়ার ভাব?
অনুজ্ঞা
নির্দেশক
সাপেক্ষ
আকাঙখা প্রকাশক
#.”রোগ হলে ওষুধ খাবে।” কোন কালের অনুজ্ঞা?
বর্তমান
ভবিষ্যৎ
অতীত
ঘটমান বর্তমান
#.‘এখন যেতে পার’। এখানে ‘যেতে পার’ কোন ক্রিয়ার উদাহরণ
মিশ্র ক্রিয়া
যৌগিক ক্রিয়া
সমাপিকা ক্রিয়া
প্রযোজক ক্রিয়া
বর্তমান কাল :-
যে ক্রিয়া এখন সম্পন্ন হয় বা হচ্ছে বুঝায়, তাকে বর্তমান কাল বলে। যেমন:
আমি পড়ি।
সে যায়।
কাকলি দৌড়ায়।
সাধারণ বর্তমান বা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল
নিত্য বা সাধারণ বর্তমান :-সাধারণভাবে যে ক্রিয়া বর্তমানে ঘটে, বা নিত্যই ঘটে, তাকে বলা হয় নিত্য-বর্তমান।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর সঙ্গে ই, অ, এন, ইস্, এ ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন :
সে হাসে। আমি পড়ি। সূর্য ওঠে। মানুষ মরে। বাতাস বয়।
ঘটমান বর্তমান কাল
ঘটমান বর্তমান :-বর্তমানে যে ক্রিয়ার কাজ আরম্ভ হয়েও শেষ হয়নি, অর্থাৎ যে-ক্রিয়ার কাজ এখনও চলছে, তাকে বলা হয় ঘটমান বর্তমান।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে ইতেছে’ (ছে), ইতেছ (ছ), ইতেছি (ছি) প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি বসে। সাধুভাষায় ইতেছে, ইতেছ, ইতেছি এবং চলিতভাষায় ছে, ছ, ছি প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি বসে। যদিও বর্তমানে চলিতভাষা প্রাধান্য পেয়েছে, তবুও সাধুভাষায় ক্রিয়া-বিভক্তির রূপগুলি জানা প্রয়োজন।
বন্ধনীর মধ্যে চলিতভাষার ক্রিয়ারুপ দেখানো হয়েছে। যেমন :
সে হাসিতেছে (হাসছে)।
তুমি কাঁদিতেছ, (কাঁদছ)।
আমি পড়িতেছি (পড়ছি)।
সূর্য উঠিতেছে (উঠছে) ইত্যাদি।
পুরাঘটিত বর্তমান কাল
পুরাঘটিত বর্তমান :-কিছুক্ষণ পূর্বে যে ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছে, অথচ যার ফল এখনও বর্তমান, তার কালকে বলা হয় পুরাঘটিত বর্তমান।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে ইয়াছে (এছে), ইয়াছ (আছ), ইয়াছি (এছি) প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়।
যেমন :
সে হাসিয়াছে (হেসেছে)।
তুমি কাঁদিয়াছ (কেঁদেছ)।
আমি পড়িয়াছি (পড়েছি) ইত্যাদি।
অতীত কাল
ক্রিয়া আগেই সম্পন্ন হয়েছে, তার কালকে অতীত কাল বলে। যেমন:
আমি তাকে দেখেছিলাম।
গতকাল ঢাকা গিয়েছিলাম।
মা রান্না করছিলেন।
অতীত কালের প্রকারভেদ :-
অতীত কালকে চারভাগে ভাগ করা যায়।
যেমন -
১.নিত্য-অতীত;
২. ঘটমান অতীত;
৩. পুরাঘটিত অতীত এবং
৪. নিত্যবৃত্ত-অতীত।
সাধারণ অতীত কাল
নিত্য বা সাধারণ অতীত :-সাধারণভাবে যে-ক্রিয়ার কাজ পূর্বে অর্থাৎ, অতীতে সম্পূর্ণ হয়েছে তার কালকে বলা হয় নিত্য-অতীত। এতে নির্দিষ্ট কোনো সময়ের উল্লেখ থাকে না। তবে বাক্য থেকে বুঝা যায় যে, এই শ্রেণির কাজ খুব বেশি পূর্বে নিষ্পন্ন হয়নি।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে-ইলাম (লাম), ইলে (লে), ল প্রভৃতি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন :
হেনা গান গাহিল (গাইল)।
আমি একটি গল্প লিখিলাম (লিখলাম)।
বাবা বাজার হইতে (থেকে) আসিলেন (এলেন)।
নিত্যবৃত্ত অতীত কাল
নিত্যবৃত্ত অতীত :পূর্বে যে ক্রিয়ার কাজ কিছুকাল ধরে চলত বা নিয়মিত ভাবে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হত, তার কালকে বলা হয় নিত্যবৃত্ত অতীত।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে-ইত (-ত), ইতাম (-তাম), ইতে (-তে) ইত্যাদি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমনঃ
প্রত্যহ সকালে হেনা সঙ্গীতচর্চা করিত (রোজ সকালে হেনা গানের রেওয়াজ করত)।
আমি যখন ঘুম হইতে উঠিতাম (আমি যখন ঘুম থেকে উঠতাম)।
বাবা তখন প্রাতর্জ সারিয়া বাড়িতে ফিরিতেন।
ঘটমান অতীত কাল
ঘটমান অতীত কাকে বলে :-পূর্বে যে-ক্রিয়ার কাজ হচ্ছিল এবং তখনও যা সম্পূর্ণ হয়নি, তার কালকে বলা হয় ঘটমান অতীত।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে- ইতেছিলাম (ছিলাম), -ইতেছিলে (ছিলে). ইতেছিল (ছিল) ইত্যাদি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন :
হেনা গান গাহিতেছিল (গাইছিল, গাচ্ছিল)।
আমি একটি গল্প লিখিতেছিলাম (লিখছিলাম)।
বাবা বাজার হইতে (থেকে) আসিতেছিলেন (আসছিলেন)।
পুরাঘটিত অতীত কাল
পুরাঘটিত-অতীত :অনেক পূর্বেই যে ক্রিয়ার কাজ ঘটেছিল, তাকে বলা হয় পুরাঘটিত-অতীত।
এই ঝাল বুঝাতে ধাতুর শেষে ইয়াছিল (এছিল), ইয়াছিলাম (এছিলাম), ইয়াছিলে (-এছিলে) ইত্যাদি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন :
হেনা গান গাহিয়াছিল (গেয়েছিল)।
আমি একটি গল্প লিখিয়াছিলাম (লিখেছিলাম)।
তখন বাবা বাজার থেকে আসিয়াছিলেন (এসেছিলেন)।
ভবিষ্যৎ কাল
ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে :-যে ক্রিয়া আগামীতে বা ভবিষ্যতে সম্পন্ন হবে এমন বোঝায়, তার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন:
বৃষ্টি আসবে।
সীমা কাল গান গাইবে।
পার্থ নাচবে।
সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল
সাধারণ ভবিষ্যৎ :-পরে অর্থাৎ ভবিষ্যতে যে ক্রিয়ার কাজ অনুষ্ঠিত হবে, তার কালকে বলা হয় সাধারণ ভবিষ্যৎ।
এই কাল বুঝাতে ধাতুর শেষে হবে -ইব (-ব), (-বে) ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমনঃ
কাল পরীক্ষা হইবে (হবে)।
আমি তোমার গান শুনিব (শুনব)।
বাবা বেড়াইতে যাইবেন (বেড়াতে যাবেন)।
ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল
ঘটমান ভবিষ্যৎ :-পরে যে ক্রিয়া ঘটতে থাকবে, তার কালকে বলা হয় ঘটমান-ভবিষ্যৎ।
এই কাল বুঝাতে মূল ধাতুর শেষে-ইতে (-তে) ক্রিয়া-বিভক্তি এবং তার পরে আছ (থাক্) ধাতুর সাথে -ইব (-ব), ইবে (-বে), ইবি (-বি) ইত্যাদি ক্রিয়া-বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমনঃ
সে তখন হাঁটিতে থাকিবে (হাঁটতে থাকবে)।
আমি যখন লিখিতে থাকিব (লিখতে থাকব)।
পাশের বাড়িতে তখন কাসরঘণ্টা বাজিতে থাকিবে (বাজতে থাকবে)।
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ :-পূর্বে যে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকবে, তার কাল হয় পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ। যেমন :
আপনি সেদিন আমাকে ভুল বুঝিয়া থাকিবেন (বুঝে থাকবেন)। সেই হয়তো লিখিয়া থাকিবে (লিখে থাকবে) ইত্যাদি।
ক্রিয়ার ভাব
ক্রিয়ার ভাবের সংজ্ঞা : যা দ্বারা ক্রিয়াপদের বর্ণিত কার্য ঘটার ধরন, প্রকার বা রীতিবোধ প্রকাশ পায়, তাকে ক্রিয়ার প্রকার বা ভাব বা ধরন বলে।
অথবা, যা দ্বারা কোনো কাজ সংঘটিত হওয়ার ভাব অর্থাৎ রীতি প্রকাশ পায় তাকে ক্রিয়ার ভাব বা প্রকার বলে।
ক্রিয়ার ভাবের প্রকারভেদ : ক্রিয়ার প্রকার বা ভাব চার ভাগে বিভক্ত। যথা–
(১) নির্দেশক ভাব
(২) অনুজ্ঞা ভাব
(৩) শর্তবাচক ভাব
(৪) আকাঙ্ক্ষাবাচক ভাব
নির্দেশক ভাব
নির্দেশক বা অবধারক ভাব : সাধারণভাবে কোনো কিছু নির্দেশ করলে তখন তাকে ক্রিয়াপদের নির্দেশক ভাব বলে। যেমন– “অর্থ, হায়রে পাতকী অর্থ, তুই জগতের সকল অনর্থের মূল।”
যারা দিনে পাঁচবার প্রার্থনা করে তারা মুসলমান।
অনুজ্ঞা ভাব
অনুজ্ঞা বা নিয়োজক ভাব : যে বাক্যে আদেশ, নিষেধ, অনুরোধ, উপদেশ, আশীর্বাদ, প্রার্থনা, কামনা ইত্যাদি ভাব প্রকাশ করে তাকে ক্রিয়া পদের অনুজ্ঞা বা নিয়োজক ভাব বলে। যেমন– এখন পড়। সদা সত্য কথা বলবে। গোলমাল করো না। সুখে থাক।
সাপেক্ষ ভাব
শর্তবাচক বা সাপেক্ষ ভাব : কোনো বাক্যে একটি ক্রিয়া শর্তের ওপর নির্ভর করে সম্পাদিত হলে তাকে ক্রিয়াপদের শর্তবাচক ভাব বলে। যেমন– প্রভু, এমন শক্তি দাও যাতে জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারি। পরিশ্রম করলে তোমরা অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে।
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশক ভাব