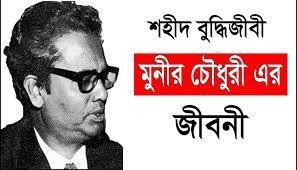সুকান্ত ভট্টাচার্য,শামসুদ্দীন আবুল কালাম,রশীদ করীম, মুনীর চৌধুরী, LEC 7
এই পর্বে যা যা থাকছে
সুকান্ত ভট্টাচার্য
শামসুদ্দীন আবুল কালাম
রশীদ করীম
মুনীর চৌধুরী
সুকান্ত ভট্টাচার্য
সুকান্ত ভট্টাচার্যের সাহিত্যকর্ম
|
সাহিত্যিক উপাদান |
সাহিত্যিক তথ্য |
|
জন্ম |
১৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা- ৩০ শ্রাবণ, ১৩৩৩) কলকাতার মহিম হালদার স্ট্রিট, কালীঘাটে (মাতুলালয়) জন্মগ্রহণ করেন। পৈতৃক নিবাস গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ার উনশিয়া গ্রামে । |
|
উপাধি |
তিনি বামপন্থি মার্কসবাদী বিপ্লবী কবি হিসেবে খ্যাত হলেও ‘কিশোর কবি' হিসেবে পরিচিত। |
|
সম্পাদনা |
তিনি ছিলেন দৈনিক পত্রিকা ‘স্বাধীনতা'র কিশোর সভা অংশের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। |
|
কাব্যগ্রন্থ |
তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহের নাম: |
|
সাহিত্য সংকলন সম্পাদনা |
‘আকাল’ (১৯৪৩) : পঞ্চাশের মন্বন্তর এ সংকলনের কবিতাগুলোর মূল প্রেরণা। ১৯৬৬ সালে সুভাস মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি ছিল জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত তাঁর একমাত্র গ্রন্থ । |
|
বিখ্যাত কবিতা |
‘আঠারো
বছর
বয়স' । কবিতাটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। |
|
গুরুত্বপূর্ণ পঙক্তি |
১. “ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, |
|
মৃত্যু |
তিনি ১৪ মে, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে (বাংলা- ২৯ বৈশাখ, ১৩৫৪) যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে যাদবপুর টিবি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। (তিনি মাত্র ২০ বছর ৯ মাস জীবিত ছিলেন) । |
শামসুদ্দীন আবুল কালাম
শামসুদ্দীন আবুল কালাম (১৯২৬-১৯৯৭)
বাংলাদেশের একটি বিশেষ এলাকার জীবনপ্রবাহকে শামসুদ্দীন আবুল কালাম প্রাণবন্তরূপে পরিবেশন করে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষ ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য এবং এসকল মানুষের প্রতি ছিল প্রগাঢ় সহানুভূতি। তাঁর গল্প- উপন্যাসে সমকালীন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট চিত্রিত হয়েছে।
শামসুদ্দীন আবুল কালামের সাহিত্যকর্ম
|
সাহিত্যিক উপাদান |
সাহিত্যিক তথ্য |
|
জন্ম |
শামসুদ্দীন আবুল কালাম আগস্ট, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঝালকাঠি জেলার নলছিটির কামদেবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । |
|
প্রকৃত নাম |
তাঁর প্রকৃত নাম আবুল কালাম শামসুদ্দীন । ‘দৈনিক আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকের নাম তাঁর নামের সাথে মিলে যাওয়ায় তিনি ১৯৫৫ সালে পত্র-পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে ‘শামসুদ্দীন আবুল কালাম' নামে পরিচিত হন । |
|
সম্পাদনা |
তিনি ‘মাহেনও’ (১৯৪৯) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। |
|
পুরস্কার |
তিনি ১৯৯৪ সালে ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' পান। |
|
উপন্যাস |
তাঁর উপন্যাসগুলো: |
|
গল্পগ্রন্থ |
তাঁর গল্পগ্রন্থসমূহ: |
|
মৃত্যু |
তিনি ১০ জানুয়ারি, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালির রোমে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁকে ঢাকায় সমাহিত করা হয় । |
রশীদ করীম
রশীদ করীম (১৯২৫-২০১১)
প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রশীদ করীম নাগরিক জীবন-ইতিহাস-নগর সমাজের সমন্বয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের এবং বাংলাদেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক জীবনের বহুমুখী পরিচয় বিধৃত করেছেন। সমাজ মনস্কতা, মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্ব ও টানাপোড়েন তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য ।
রশীদ করীমের সাহিত্যকর্ম
|
সাহিত্যিক উপাদান |
সাহিত্যিক তথ্য |
|
জন্ম |
রশীদ করীম ১৪ আগস্ট, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন । কথাসাহিত্যিক আবু রুশদ তাঁর ভাই । |
|
প্রথম গল্প |
তাঁর রচিত প্রথম গল্প ‘ আয়েশা ’ ১৯৪২ সালে ‘ সওগাত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। |
|
পুরস্কার ও সম্মাননা |
তিনি আদমজী পুরস্কার (১৯৬১), বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭২), একুশে পদক (১৯৮৪), লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৯১) পান । |
|
উপন্যাস |
তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহ: |
|
প্রবন্ধগ্রন্থ |
তাঁর রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ সমূহ : |
|
গল্পগ্রন্থ |
গল্পগ্রন্থ: ‘প্রথম প্রেম' । |
|
আত্মজীবনী |
আত্মজীবনী: ‘জীবন মরণ' (১৯৯৯)। |
|
মৃত্যু |
তিনি ১৯৯২ সালে পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং ২৬ নভেম্বর, ২০১১ সালে ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টারে মারা যান । |
মুনীর চৌধুরী
মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১)
বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, অসাধারণ বক্তা, সৃজনশীল নাট্যকার, তীক্ষ্ণধী সমালোচক ও সফল অনুবাদক মুনীর চৌধুরী। সাহিত্য, ধ্বনিতত্ত্বের গবেষণা ও তুলনামূলক সমালোচনায় তিনি রেখে গেছেন অনন্য পাণ্ডিত্য ও উৎকর্ষের ছাপ। তিনি বাংলাদেশের আধুনিক নাটক ও নাট্য আন্দোলনের পথিকৃৎ।
মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম
|
সাহিত্যিক উপাদান |
সাহিত্যিক তথ্য |
|
জন্ম |
মুনীর চৌধুরী ২৭ নভেম্বর, ১৯২৫ সালে মানিকগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন । পৈতৃক নিবাস- নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার গোপাইরবাগ গ্রামে। |
|
পুরো নাম |
পুরো নাম আবু নায়ীম মোহাম্মদ মুনীর চৌধুরী । অধ্যাপক কবীর চৌধুরী তার ভাই এবং ফেরদৌসী মজুমদার তার বোন। |
|
রবীন্দ্রসংগীত প্রচার |
২২ জুন, ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে এক বিবৃতিতে রেডিও ও টেলিভিশন থেকে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলে সে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। |
|
বর্ণমালা সংস্কার |
১৯৬৮ সালে বাংলা বর্ণমালা সংস্কার পদক্ষেপের বিরোধিতা করেন। |
|
পুরস্কার ও সম্মাননা |
তিনি নাটকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬২), . দাউদ পুরস্কার (১৯৬৫) পান। তিনি ১৯৬৬ সালে 'সিতারা- ই-ইমতিয়াজ' খেতাব লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক আহূত অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এ খেতাব বর্জন করেন । |
|
বাংলা টাইপ রাইটার |
প্রথম বাংলা টাইপ রাইটার নির্মাণ করেন মুনীর চৌধুরী। এটি ‘মুনীর অপটিমা’ নামে পরিচিত। ১৯৬৫ সালে এটি উদ্ভাবন করেন । |
|
নাটক |
তাঁর রচিত নাটকগুলো: |
|
অনূদিত নাটক |
তাঁর অনূদিত নাটকগুলো: |
|
প্রবন্ধ |
তাঁর রচিত প্রবন্ধগুলো: |
|
মৃত্যু |
১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে স্বাধীনতাবিরোধী আলবদর বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে যায় এবং আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। |
বিয়োগান্তক নাটক হিসেবে ‘রক্তাক্ত প্রান্তর' এর পরিচয়
সাহিত্যকর্মে, বিশেষভাবে নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ যখন তার পরিণতিতে প্রধান চরিত্রের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনে তখন তাকে সাধারণভাবে বিয়োগান্তক নাটক বলে । ১৭৬১ সালের পানিপথের (বর্তমান ভারতের হরিয়ানা প্রদেশের অন্তর্গত প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্র) ৩য় যুদ্ধের কাহিনি এর উপজীব্য। প্রশিক্ষিত মুসলিম যোদ্ধা ইব্রাহীম কার্দি মুসলিম শিবিরে চাকরি না পেয়ে মারাঠা কর্তৃক চাকরি পায় এবং সমাদৃত হয়। যুদ্ধ শুরু হলে ইব্রাহীম কার্দির স্ত্রী জোহরা মন্নুবেগ ছদ্মনাম ধারণ করে এসে স্বামীকে মুসলিম শিবিরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করে। ইব্রাহীম কার্দি বিশ্বাসঘাতকতা না করে মারাঠাদের জন্য যুদ্ধে জীবন দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। নায়ক ইব্রাহীম কার্দির মৃত্যু নাটকটিকে ট্র্যাজিক করে তোলে। এটি ঐতিহাসিক নাটক নয়, ইতিহাস-আশ্রিত ট্র্যাজিক নাটক। এ নাটকের বিখ্যাত উক্তি- ‘মানুষ মরে গেলে পচে যায়, বেঁচে থাকলে বদলায়, কারণে-অকারণে বদলায়।'
'কবর' নাটক এর পরিচয়
মার্কিন নাট্যকার Irwin
Shaw রচিত Bury The Dead (১৯৩৬) নাটকের অনুসরণে মুনীর চৌধুরী এদেশীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘কবর' নাটকটি রচনা করেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার মুনীর চৌধুরীকে ১৯৫২ সালে আটক করে জেলে প্রেরণ করে। জেলে থাকা অবস্থায় বামপন্থী লেখক রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৩ সালে এ নাটকটি রচনা করেন। ১৯৫৩ সালে কারাগারেই রাজবন্দীদের দ্বারা এটি প্রথম মঞ্চায়ন করা হয়। ‘কবর' নাটকে দেখা যায়, রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবীর মিছিলে পুলিশ গুলি করে এবং কারফিউ জারি করে। রাতের আঁধারে বাংলার দামাল ছেলেদের গুলিবিদ্ধ লাশ গুম করার দায়িত্ব দেয়া হয় পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ ও নেতাকে। ছিন্নভিন্ন লাশ কবরস্থ না করে মাটিচাপা দেয়ার সিদ্ধান্তে বাধা দেয় গোর-খোদক ও মুর্দা ফকির। পরবর্তীতে লাশগুলো জিন্দা হয়ে কবরে যেতে অস্বীকৃতি জানায়। উল্লেখ্য, এতে কোনো নারী চরিত্র নেই