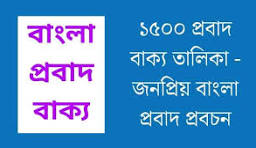বিরাম বা যতি চিহ্ন ও প্রবাদ বাক্যের তালিকা (LEC 6)
বিরাম বা যতি চিহ্ন
বাক্যের অর্থ সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ (হর্ষ, বিষাদ), জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য গঠনে যে ভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তা-ই যতি বা বিরাম বা ছেদচিহ্ন।
বিরাম চিহ্ন কেনো ব্যবহৃত হয়?
ক. বাক্যের অর্থ সহজভাবে বোঝাতে,
খ. শ্বাস বিরতির জায়গা দেখাতে,
গ. বাক্যকে অলংকৃত করতে,
ঘ. বাক্যের অর্থ স্পষ্টকরণের জন্য,
বিরাম বা যতি চিহ্ন এর প্রবর্তক কে?
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । বাংলা সাহিত্যে দাঁড়ি, কমা, কোলন প্রভৃতি বিরাম চিহ্ন তিনি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। এজন্য তাকে বাংলা যতি চিহ্নের প্রবর্তক বলা হয় ।
বিরাম বা যতি চিহ্ন মোট কয়টি?
বিরাম বা যতি চিহ্ন মোট ১২টি। নিম্নে এদের নাম, আকৃতি এবং তাদের বিরতিকালের পরিমাণ নির্দেশিত হলো-
|
যতি চিহ্নের নাম |
আকৃতি |
বিরতিকাল-পরিমাণ |
|
কমা (পাদচ্ছেদ) |
, |
১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন |
|
সেমিকোলন(অর্ধচ্ছেদ) |
; |
১ বলার দ্বিগুণ সময় |
|
দাঁড়ি (পূর্ণচ্ছেদ) |
। |
এক সেকেন্ড |
|
জিজ্ঞাসা চিহ্ন |
? |
|
|
বিস্ময় চিহ্ন |
! |
|
|
কোলন |
: |
|
|
কোলন ড্যাস |
:- |
|
|
ড্যাস |
- |
|
|
উদ্ধরণ চিহ্ন |
“ ” |
এক উচ্চারণে যে সময় লাগে |
|
ইলেক বা লোপচিহ্ন |
’ |
থামার প্রয়োজন নাই |
|
হাইফেন |
- |
|
|
ব্রাকেট (বন্ধনী চিহ্ন) |
(),{},[] |
বাক্যের অভ্যন্তরে বসে : কমা, সেমিকোলন, ড্যাস (৩টি)। বাক্যের প্রান্তে বসে : দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, বিস্ময়চিহ্ন (৩টি)
যতি বা বিরাম চিহ্নের ব্যবহার
১. কমা / পাদচ্ছেদ (,):
ক. বাক্য পাঠকালে সুস্পষ্টতা বা অর্থ-বিভাগ দেখাবার জন্য যেখানে স্বল্প বিরতির প্রয়োজন, সেখানে কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন- সুখ চাও, সুখ পাবে পরিশ্রমে।
খ. পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে বসলে শেষ পদটি ছাড়া বাকি সবগুলোর পরই কমা বসবে। যেমন- সুখ, দুঃখ, আশা, নৈরাশ্য একই মালিকার পুষ্প।
গ. সম্বোধনের পরে কমা বসাতে হয়। যেমন- রশিদ, এখানে আস ।
ঘ. মাসের তারিখ লিখতে বার ও মাসের পর কমা বসবে। যেমন- ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ ।
ঙ. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে (খণ্ড বাক্যের শেষে) কমা বসাতে হবে। যেমন- অধ্যক্ষ বললেন, “ছুটি পাবেন না।”
চ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে। যেমন- ৬৫, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
২. সেমি কোলন (;): কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে, সেমি কোলন বসে। একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমি কোলন বসে। যেমন- সংসারের মায়াজালে আবদ্ধ আমরা; সে মায়ার বাঁধন কি সত্যিই দুশ্ছেদ্য?
৩. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (। ): বাক্যের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করতে হয়। যেমন- কুড়িগ্রাম থেকে ঢাকার দূরত্ব ৩৮০ কিলোমিটার।
৪. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?): বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসে। যেমন- তুমি কখন এলে?
৫. বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন (!): হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে হলে এবং সম্বোধন পদের পরে বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন বসে। যেমন- আহা! কি চমৎকার দৃশ্য।
৬. কোলন ( : ) : একটি অপূর্ণ বাক্যের পরে অন্য একটি বাক্যের অবতারণা করতে হলে কোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন- সভায় সাব্যস্ত হলো : এক মাস পরে নতুন সভাপতি নির্বাচিত করা হবে।
৭. ড্যাস চিহ্ন (-): যৌগিক ও মিশ্র বাক্য পৃথক ভাবাপন্ন দুই বা তার বেশি বাক্যের সমন্বয় বা সংযোগ বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কোনো কথার দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বোঝাতে ড্যাস চিহ্ন বসে। যেমন- তোমরা দরিদ্রের উপকার কর এতে - তোমাদের সম্মান যাবে না - বাড়বে।
৮. কোলন ড্যাস (:-): উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে হলে কোলন এবং ড্যাস চিহ্ন একসাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন- বর্ণ দুই প্রকার। যথা: স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
৯. হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন (-): সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখাবার জন্য হাইফেনের ব্যবহার করা হয়। দুই শব্দের সংযোগ বোঝাতে হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন এ আমাদের শ্রদ্ধা - অভিনন্দন, আমাদের প্রীতি - উপহার।
১০. ইলেক বা লোপ চিহ্ন ('): কোনো বর্ণ বিশেষের লোপ বোঝাতে বিলুপ্ত বর্ণের জন্য লোপচিহ্ন দেয়া হয়। যেমন- মাথার‘পরে জ্বলছে রবি। (‘পরে = ওপরে)
১১. উদ্ধরণ চিহ্ন (“”): বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। যেমন- শিক্ষক বললেন, “গতকাল ‘অগ্রদূত বাংলা’ বইটি প্রকাশিত হয়েছে।”
১২. ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন : (), {}, [] এই তিনটি চিহ্নই গণিতশাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন- ত্রিপুরায় (বর্তমানে কুমিল্লা) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
১০০+ ব্যাখ্যাসহ প্রবাদ
বাক্যের
তালিকা
|| প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার
জন্য
বাংলা লোকসাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ প্রবাদ বাক্য । এর মাধ্যমে নিগুড় সত্য বা বাস্তবতা উঠে আসে। এটি মানুষের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল থেকে ধীরে ধীরে প্রয়োগের ফলে এক সময় সমাজে মিশে যায় বা প্রচলন হয়।আর এভাবেই এক সময় প্রতিনিয়ত ব্যবহারের প্রথা চালু হয়। বাঙালি জাতির হাজার বছরের অধিক সময়ের সংস্কৃতিতে প্রবাদ-প্রবচন/ প্রবাদ বাক্য একটি সমৃদ্ধ ধারা হিসেবে চলে আসছে। প্রবাদ-প্রবচন প্রায় একই অর্থে প্রয়োগ করলেও এই দুটির মধ্যে সামান্য কিছু ভিন্নতা রয়েছে।প্রবাদ হল মানুষের অভিজ্ঞতার ফসল থেকে উদ্ভূত এক ধরনের নিগূড় সত্য যা বিদ্রুপাত্নক উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এর কোন একক রচয়িতা খুজে পাওয়া যাবে না।কিন্তু প্রবচন হল সমাজের সৃষ্টিশীল এবং প্রজ্ঞাবান মানুষের অভিজ্ঞতালদ্ধ কিছু উক্তি যা ব্যবহার করতে করতে এক সময় জনসমাজে মিশে যায়। নিচে আমরা প্রবাদ বাক্য তালিকা প্রস্তুত করেছি যা বিগত সালের প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে তৈরি করা হয়েছে । বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবশ্যই এখান থেকে কমন থাকবে।
প্রবাদ-প্রবচন কাকে বলে?
লোক সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ প্রবাদ-প্রবচন। ‘প্রবাদ' ও 'প্রবচন' প্রায় একই অর্থ বহন করে। প্রবাদ হচ্ছে পরম্পরাগত বাক্য, জনশ্রুতি এবং ‘প্রবচন' হচ্ছে প্রকৃষ্ট বচন, অর্থাৎ বহু প্রচলিত উক্তি। মানুষের দীর্ঘদিনের আচরণ পর্যবেক্ষণ করে ঐ সমাজের কোনো সৃষ্টিশীল ব্যক্তি যে চৌকস অভিব্যক্তি বাণীবদ্ধ করে, তাই কালে কালে প্রবাদে পরিণত হয়। যেমন-বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। এটির রচয়িতা সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি তার পালামৌ উপন্যাসে এই উক্তিটি করেছিলেন। এটি হল প্রবচন যার রচয়িতার হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু প্রবাদের কোন রচয়িতার হদিস পাওয়া যায় না। কালক্রমে রচয়িতা বিলীন হয়ে যায় কিন্তু তার প্রবাদ থেকে যায় জনসমাজে। যেমন- অতি চালাকের গলায় দড়ি, কয়লা ধুলে ময়লা যায় না ইত্যাদি।
প্রবাদ-প্রবচনের পার্থক্য
1.
প্রবাদ লোকসমাজ বা কালের সৃষ্টি।কিন্তু প্রবচন হল সমাজের সৃজনশীল মানুষের সৃষ্টি যেমন কবি,সাহিত্যিক ইত্যাদি।
2.
প্রবাদের কোন লিখিত রুপ নেই যা শুধু মুখে মুখেই প্রচলিত।কিন্তু প্রবচনের লিখিত রুপ আছে। কারণ সেটা জনসমাজের মানুষের লেখা থেকেই প্রচলন শুরু হয়।কালক্রমে সেটা সবাই মুখে মুখে ব্যবহার করে।
3.
প্রবাদ জনসমাজের অভিজ্ঞতার ফসল বা নির্যাস। কিন্তু প্রবচন কোন একক ব্যক্তির অভিজ্ঞালতালদ্ধ উক্তি।
4.
প্রবাদের ব্যজ্ঞনার্থ আছে কিন্তু প্রবচনের রূপক ধর্ম নেই, বাচ্যার্থ বা সরাসরি অর্থই প্রকাশ করে।
5.
সাধারণত প্রবাদ প্রবচনের চেয়ে ছোট হয়।
প্রবাদ বাক্যের বৈশিষ্ট্য
ক. প্রবাদে জাতির দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পরিণত বুদ্ধি এবং লোকমনে প্রচলিত সত্য কথন প্রকাশিত হয়।
খ. প্রবাদের অবয়ব হলো একটি সংক্ষিপ্ত বাক্য ।
গ. উপমা, বক্রোক্তি, বিরোধাভাস প্রভৃতি অলংকারযোগে তা গঠিত হয়।
প্রবাদ বাক্যের শ্রেণীবিভাগ
অর্থ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে প্রবাদ বাক্যকে নানাভাবে ভাগ করা যায়। যেমন-
1.
সাধারণ অভিজ্ঞতাবাচক
: চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
2.
নীতিকথামূলক
: ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।
3.
ইতিকথামূলক
: ধান ভানতে শিবের গীত ।
4.
মানবচরিত্র সমালোচনামূলক
: গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল ।
5.
সামাজিক রীতিনীতিজ্ঞাপক
: মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।
6.
প্রসিদ্ধ ঘটনামূলক
: লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।
ব্যাখ্যাসহ প্রবাদ বাক্যের কিছু উদাহরণ
|
ব্যাখ্যাসহ প্রবাদ বাক্য |