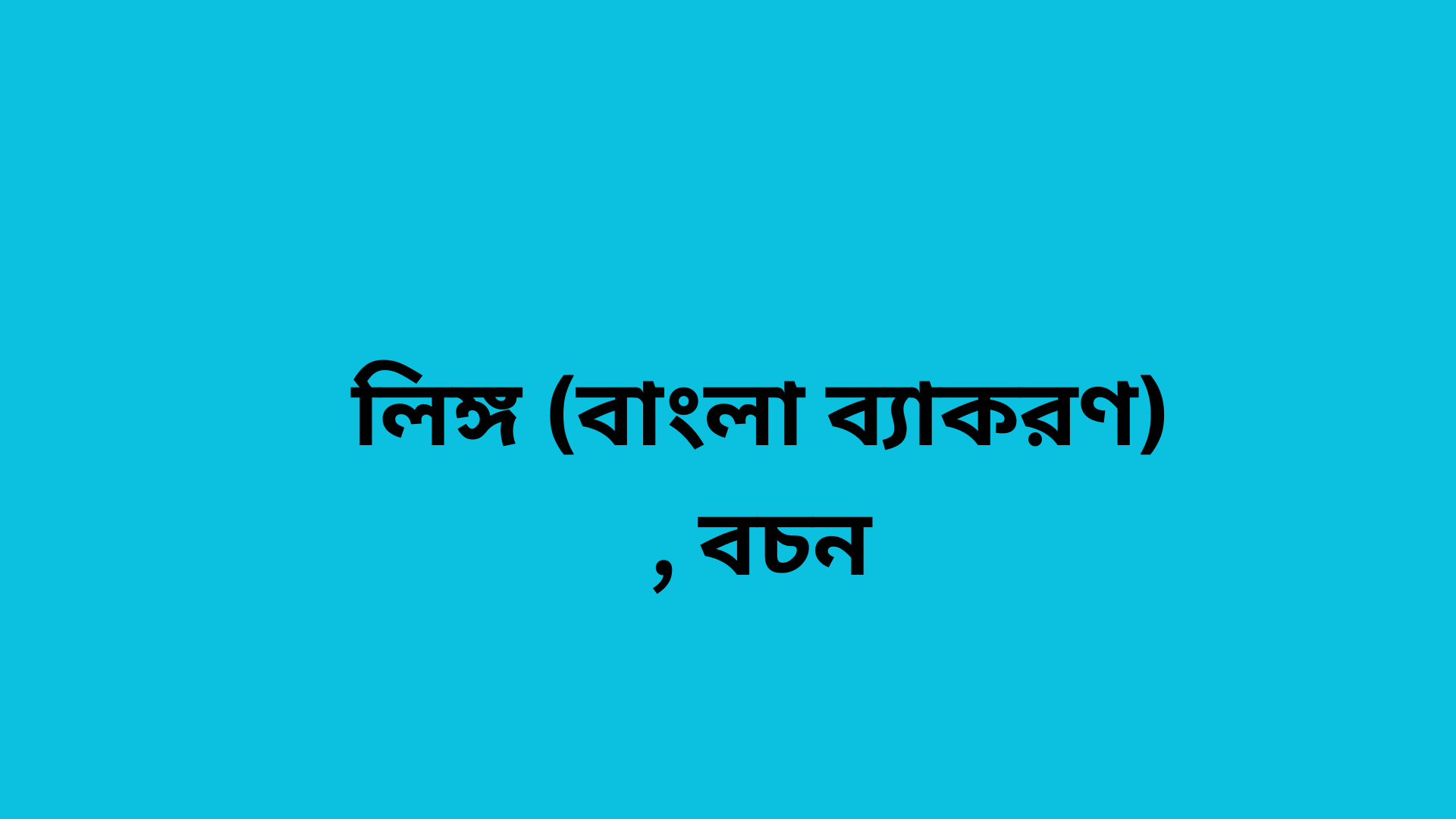লিঙ্গ (বাংলা ব্যাকরণ), বচন,সংখ্যাবাচক শব্দ
লিঙ্গ (বাংলা ব্যাকরণ)
যে সকল শব্দ দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী ও অচেতন বস্তুকে চিহ্নিত করা যায়, তাকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গ চার
প্রকার যথা-
1. পুংলিঙ্গ
2. স্ত্রীলিঙ্গ
3. ক্লীবলিঙ্গ
4. উভয় লিঙ্গ
লিঙ্গ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে
হবে—কেবলমাত্র প্রাণীবাচক শব্দগুলি পুংলিঙ্গ অথবা
স্ত্রীলিঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। অপ্রাণীবাচক শব্দ ক্লীবলিগের অন্তর্গত। সংস্কৃত ব্যাকরণে উভয় লিঙ্গ বলে কোন কিছু নেই; কিন্তু ইংরেজি ব্যাকরণে Common Gender অর্থাৎ উভয় লিঙ্গ আছে।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.লিঙ্গান্তর হয় না এমন শব্দ-
সাহেব
বেয়াই
কবিরাজ
সঙ্গী
#.নিচের কোন শব্দটির লিঙ্গান্তর হয়না?
বেয়াই
পুলিশ
কবিরাজ
নাপিত
#.কোনটির লিঙ্গান্তর হয় না?
চৌধুরী
ক্ষত্রিয়
নবীন
কবিরাজ
#.‘চঞ্চল’ এর স্ত্রী লিঙ্গ কী?
চঞ্চলা
চঞ্চলময়ী
চঞ্চলবতী
চঞ্চলমতি
#.ঈ-প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীলিঙ্গ কোনটি?
জেলেনী
বেদেনী
বাঘিনী
সতী
পুংলিঙ্গ
যেসব শব্দ পুরুষ জাতিকে বোঝায়, তাদের পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—মানুষ, শিক্ষক, ছাত্র, গোয়ালা, সিংহ ইত্যাদি।
স্ত্রীলিঙ্গ
যেসব শব্দ স্ত্রী জাতিকে বোঝায়, তাদের স্ত্রীলিঙ্গ
বলে। যেমন— মা, ছাত্রী, শিক্ষিকা, সিংহী, ইত্যাদি।
উভয় লিঙ্গ
যেসব শব্দ দ্বারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে বোঝানো হয়, তাদের উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন- ডাক্তার, শিশু, বহু
কবি, শিল্পী ইত্যাদি।
ক্লীব লিঙ্গ
এমন কিছু শব্দ আছে যাদের দ্বারা পুরুষ অথবা স্ত্রী না বুঝিয়ে অচেতন বস্তুকে বোঝায়, তাদের ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন—গাছ, ফুল, জামা, বাড়ি, পর্বত, বৃক্ষ ইত্যাদি।
বচন
বচন অর্থ সংখ্যার ধারণা । যা দ্বারা সংখ্যা বুঝায় , তাকে বচন বলে । বচন দু " প্রকার । যথা- একবচন (Singular Number) ও বহুবচন (Plural Number)।
একবচন:- যে বচন দ্বারা একটি মাত্র ব্যক্তি , প্রাণী বা বস্তুকে বুঝায় , তাকে একবচন বলে । যেমন — একটি গরু । একজন ছাত্র । একটি টাকা ।
( ক ) সাধারণত ' এক ’ শব্দ যােগে একবচন নির্দেশ করা হয় । তবে এর সাথে টি , টা , খানা , খানি , থান , গাছি ইত্যাদি প্রত্যয় যােগ করেও একবচন নির্দেশ করা হয় । যেমন একটি কলম । কলমটি । বইখানা । গামছাখানা । চুড়িগাছি ইত্যাদি । আবার শব্দের মূল রূপটি দ্বারাও একবচন বুঝায় । যেমন — গরু , মানুষ , ফল , ফুল ইত্যাদি ।
( খ ) এক বচনে বিভক্তি যােগেও এক বচন বুঝানাে হয় । যেমন – ভাইকে , পিতাকে , মাতাকে ইত্যাদি।
বহুবচন:- যে বচন দ্বারা একের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝায় , তাকে বহুবচন বলে । যেমন — দু'জন বালক , দশটি গরু , শিশুরা , ছাত্রগণ , বইগুলাে , বৃক্ষরাজি , শিক্ষকবৃন্দ , সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি ।
একবচন হতে বহুবচন করার বিবিধ উপায়
( ১ ) একবচন শব্দের সঙ্গে রা , এরা , গুলাে , গুলি , গণ , বৃন্দ , দিগকে , দেরকে ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত করলে বহুবচন বুঝায় । যেমন-
রা- ছাত্ররা , ধনীরা , গরীবেরা , পাখীরা ইত্যাদি ।
এরা- মানুষেরা , মায়েরা , ঝিয়েরা , বড়লােকেরা ইত্যাদি ।
গুলি- প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত হয় । যেমন- লােকগুলি , আমগুলি , টাকাগুলি ।
বিশেষ দ্রষ্টব্য- ‘গুলাে' চলতি ভাষায় ব্যবহৃত হয় । যেমন- টাকাগুলাে দিয়ে দাও । মাছগুলাে নিয়ে এস । বইগুলাে আন।
উন্নত প্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচন
গণ- শিশুগণ , জনগণ , দেবগণ , নর - নারীগণ ইত্যাদি ।
বৃন্দ- শিক্ষকবৃন্দ , ভক্তবৃন্দ , সুধীবৃন্দ , অতিথিবৃন্দ ইত্যাদি ।
মণ্ডলী- শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী , অভিভাবকমণ্ডলী ইত্যাদি ।
বর্গ- ছাত্রবর্গ , পণ্ডিতবর্গ , প্রজাাবর্গ , রাজন্যবর্গ ইত্যাদি ।
প্রাণীবাচক ও অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচন
কুল- পক্ষিকুল , মাতৃকুল , কবিকুল , কৃষককুল ইত্যাদি ।
সকল- মনুষ্য সকল , পর্বত সকল , লােক সকল ইত্যাদি ।
নিচয়- পৰ্বত নিচা কুসুম নিচয় , বৃক্ষ নিচয়া ইত্যাদি ।
সব- ভাইসব , পাখীসব , নথিস ইত্যাদি ।
সমূহ- বৃক্ষসমূহ , পর্বতসমূহ , নদীসমূহ , গ্রামসমূহ ইত্যাদি ।
মহল- ছাত্রমহল , রাজনৈতিকমহল , বুদ্ধিজীবীমহল , সাহিত্যিকমহল ইত্যাদি ।
কেবল অপ্রাণীবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচন
মালা - পর্বতমালা , তরঙ্গমালা ইত্যাদি ।
রাজি - বৃক্ষরাজি , তারকারাজি ইত্যাদি ।
পুঞ্জ – মেঘপুঞ্জ , নক্ষত্রপুঞ্জ , দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি ।
গুচ্ছ - কবিতাগুচ্ছ , ফুলগুচ্ছ , গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি ।
দাম - কেশদাম , শৈবালদাম ইত্যাদি ।
রাশি - বালুকারাশি , আবর্জনারাশি ইত্যাদি ।
বলী - পুস্তকাবলী , গুণাবলী , রত্নাবলী ইত্যাদি ।
বিঃ দ্রঃ – পাল ও যুথ কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয় । যেমন- গরুরপাল , হস্তিযুথ ইত্যাদি ।
যেমন — রাখাল গরুরপাল নিয়ে যাচ্ছে । হস্তিযুথ ফসল নষ্ট করেছে ।
( ২ ) একবচন শব্দের পূর্বে বহুত্ববােধক শব্দ বসিয়ে বহুবচন করা যায় । যেমন — বহু লােক , অনেক ছাত্র , বিস্তর টাকা , নানা কথা , অসংখ্য বাড়ী , অজস্র মানুষ , ঢের খরচ ।
( ৩ ) শব্দের পূর্বে একই বিশেষণ দু'বার ব্যবহার করে বহুবচন করা হয় । যেমন - বড় বড় গাছ , কচি কচি পাতা , লাল লাল ফুল , সাদা সাদা মেঘ , উঁচু উঁচু পাহাড় , কাড়ি কাড়ি লাউ ।
( ৪ ) সংখ্যাবাচক বিশেষণ যােগ করেও বহুবচন গঠন করা যায় । যেমন — দশটি আম , পাঁচশত টাকা , এক হাজার লােক , পনর কেজি চাউল ।
( ৫ ) সর্বনাম পদ দু'বার ব্যবহার করে বহুবচন করা যায় । যেমন – কি কি বই , যে যে বালক , যেখানে যেখানে দরকার , সেই সেই দোকান ইত্যাদি ।
( ৬ ) বিশেষ্য পদ দু’বার ব্যবহার করেও বহুবচন গঠন করা হয় । যেমন- মাঠে মাঠে ধান , ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী , ঘরে ঘরে উৎসৰ , চুলে চুলে মারামারি ইত্যাদি ।
( ৭ ) ক্রিয়াপদের দু’বার প্রয়ােগেও বহুবচন হয় । যেমন— খেটে খেটে মরছি । বলে বলে হানা হলাম ।
( ৮ ) বিশেষ্য পদে একবচনে ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বুঝায় । যেমন — বাঘ বনে থাকে । ( একবচন ও বহুবচন দুই - ই বুঝাচ্ছে ) । মাছের বাজারে লােক জমেছে ( বহু লোক ) । বাগানে ফুল ফুটেছে ( বহু ফুল ) ।
বিশেষ দ্রষ্টব্য– একই সাথে দু'বার বহুবচনবাচক প্রত্যায় বা শব্দের ব্যবহার অশুদ্ধ।যেমন
অশুদ্ধ — সব শিক্ষকেরাই উপস্থিত ছিলেন ।
শুদ্ধ — সব শিক্ষকই উপস্থিত ছিলেন ।
অশুদ্ধ - সব মানুষেরাই মরণশীল ।
শুদ্ধ — সব মানুষ মরণশীল , অথবা মানুষ মরণশীল , অথবা মানুষেরা মরণশীল ।
এইরূপে , এখানে যাবতীয় দ্রব্যসমূহ পাওয়া যায় । এই বাক্য অশুদ্ধ , কিন্তু এখানে যাবতীয় দ্রব্য পাওয়া যায় । এটা শুদ্ধ বাক্য । কেননা যাবতীয় ও সমূহ উভয়ই বহুবচনবাচক শব্দ । তদ্রুপ , অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এ মত পােষণ করেন - এটা ভুল , কিন্তু অন্যান্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ মত পােষণ করেন- এটা শুদ্ধ ।
একবচন
একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একটিমাত্র সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে একবচন বলে।
যেমন – সে এলো। মেয়েটি স্কুলে যায়নি
বহুবচন
বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোনো প্রাণী, বস্তু বা ব্যক্তির একের অধিক অর্থাৎ বহু সংখ্যার ধারণা হয়, তাকে বহু বচন বলে। যেমন : তারা গেল। মেয়েরা এখনও আসেনি।
কেবলমাত্র বিশেষ্য ও সর্বনাম শব্দের বচনভেদ হয়। কোনো কোনো সময় টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি যোগ করে বিশেষ্যের একবচন নির্দেশ করা হয়। যেমন – গরুটা, বাছুরটা, কলমটা, খাতাখানা, বইখানি ইত্যাদি ।
বাংলায় বহুবচন প্রকাশের জন্য রা, এরা, গুলা, গুলি, গুলো, দিগ, দের প্রভৃতি বিভক্তি যুক্ত হয় এবং সব, সকল, সমুদয়, কূল, বৃন্দ, বর্গ, নিচয়, রাজি, রাশি, পাল, দাম, নিকর, মালা, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়। সমষ্টিবোধক শব্দগুলোর বেশিরভাগই তৎসম বা সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত ৷
প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক এবং ইতর প্রাণিবাচক ও উন্নত প্রাণিবাচক শব্দভেদে বিভিন্ন ধরনের বহু বচনবোধক
প্রত্যয় ও সমষ্টিবোধক শব্দ যুক্ত হয়। যেমন-
(ক) রা–কেবল উন্নত প্রাণিবাচক শব্দের সঙ্গে ‘রা’ বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- ছাত্ররা খেলা দেখতে গেছে। তারা সকলেই লেখাপড়া করে। শিক্ষকেরা জ্ঞান দান করেন।
যে ধরনের শব্দে ‘রা' যুক্ত, সে ধরনের শব্দের শেষে কোনো কোনো সময় ‘এরা' ব্যবহৃত হয়। যেমন মেয়েরা ঝিয়েরা একত্র হয়েছে। সময় সময় কবিতা বা অন্যান্য প্রয়োজনে অপ্রাণী ও ইতর প্রাণিবাচক শব্দেও রা, এরা যুক্ত হয়। যেমন – ‘পাখিরা আকাশে উড়ে দেখিয়া হিংসায় পিপীলিকারা বিধাতার কাছে পাখা চায়।” কাকেরা এক বিরাট সভা করল। -
(খ) গুলা, গুলি, গুলো প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচনে যুক্ত হয়। যেমন – অতগুলো কুমড়া দিয়ে কী হবে? আমগুলো টক। টাকাগুলো দিয়ে দাও। ময়ূরগুলো পুচ্ছ নাড়িয়ে নাচছে।
(ক) উন্নত প্রাণিবাচক মনুষ্য শব্দের বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ
গণ :দেবগণ, নরগণ, জনগণ ইত্যাদি ।
বৃন্দ : সুধীবৃন্দ, ভক্তবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ ইত্যাদি ৷
মণ্ডলী: শিক্ষকমণ্ডলী, সম্পাদকমণ্ডলী ইত্যাদি।
বর্গ: পণ্ডিতবর্গ, মন্ত্রিবর্গ ইত্যাদি।
(খ) প্রাণিবাচক ও অপ্রাণিবাচক শব্দে বহুবচনে ব্যবহৃত শব্দ
কুল : কবিকুল, পক্ষিকুল, মাতৃকুল, বৃক্ষকুল ইত্যাদি।
সকল: পর্বতসকল, মনুষ্যসকল ইত্যাদি।
সব : ভাইসব, পাখিসব ইত্যাদি।
সমূহ: বৃক্ষসমূহ, মনুষ্যসমূহ ইত্যাদি।
(গ) অপ্রাণিবাচক শব্দে ব্যবহৃত বহুবচনবোধক শব্দ
আবলি, গুচ্ছ, দাম, নিকর, পুঞ্জ, মালা, রাজি, রাশি। যেমন-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাবলি, কবিতাগুচ্ছ, কুসুমদাম, কমলনিকর, মেঘকুঞ্জ, পর্বতমালা, তারকারাজি, বালিরাশি, কুসুমনিচয় ইত্যাদি ।
দ্রষ্টব্য : পাল ও যূথ শব্দ দুটি কেবল জন্তুর বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। যেমন - রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে ।
হস্তিযূথ মাঠের ফসল নষ্ট করছে।
# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন
#.কাগজ’এর বহুবচন -
কাগজাত
কাগজগুলো
কাগজসমূহ
কাগজাদি
#.বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন কোনটি?
জঙ্গলে সাপ থাকে
পোকায় ধান খেয়েছে।
হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ
নয়নদের পরীক্ষা শেষ
#.নিচের কোন উদাহারণটি একবচনের সাহায্য বহুবচনের প্রকাশ?
পোকার আক্রমনে ফসল বিনষ্ট হয়
ওই এক পথই খোলা আছে
আমার ইচ্ছাগুলো যদি পূরণ করতে পারতাম
চোরেরা পুলিশকে দেখে পালিয়ে গেলো
#.কোনটি অপ্রাণিবাচক বহুবচনে ব্যবহৃত হয়?
বৃন্দ
কুল
বর্গ
গুচ্ছ
#.নিচের কোনটিতে বহুবচনের অপপ্রয়োগ ঘটেছে?
আকাশে উঠেছে বকপাঁতি
সমুদয় শিক্ষাবৃন্দ আমন্ত্রিত
সকল শিক্ষক অনুদান হয় না
রাশি রাশি ভারা/ ধান কাটা হলো সালা
সংখ্যাবাচক শব্দ
সংখ্যা মানে গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক ‘এক’। কাজেই সংখ্যাবাচক শব্দে এক একাধিক, প্রথম, প্রাথমিক ইত্যাদির ধারণা করতে পারি। যেমন : এক টাকা, দশ টাকা। এক টাকাকে এক এক করে দশবার নিলে হয় দশ টাকা ।
সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার
১. অঙ্কবাচক,
২. পরিমাণ বা গণনাবাচক,
৩. ক্রম বা পূরণবাচক ও ৪. তারিখবাচক
১. অঙ্কবাচক সংখ্যা
‘তিন টাকা’ বলতে এক টাকার তিনটি একক বা এককের সমষ্টি বোঝায়। আমাদের একক হলো ‘এক’। সুতরাং এক + এক + এক = তিন। এভাবে আমরা এক থেকে একশ পর্যন্ত গণনা করতে পারি। এক থেকে একশ পর্যন্ত এভাবে গণনার পদ্ধতিকে
বলা হয় দশ গুণোত্তর পদ্ধতি।
এক থেকে দশ পর্যন্ত আমরা এভাবে লিখে থাকি : এক (১), দুই (২), তিন (৩), চার (৪), পাঁচ (৫), ছয় (৬), সাত (৭), আট (৮), নয় (৯), দশ (১০)। এখানে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলোকে বলে অঙ্ক। এক থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কে লিখিত। দশ লিখতে এক লিখে তার ডানে একটি শূন্য (১০) দিতে হয়। এই শূন্যের অর্থ বাম দিকে লিখিত পূর্ণ সংখ্যাটির দশগুণ। এটিই দশ গুণোত্তর প্রণালীর নিয়ম। এ ধরনের প্রতিটি ‘দশ’কে একক ধরে আমরা বিশ বা কুড়ি (২০), ত্রিশ (৩০), চল্লিশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষাট (৬০), সত্তর (৭০), আশি (৮০), নব্বই (৯০) পর্যন্ত গণনা করি। তারপরের দশকের একককে বলা হয় একশ (১০০)। এভাবে আমরা দশের গুণন ও এককের সংকলন করে বিভিন্ন সংখ্যা লিখে থাকি। যেমন : এক দশ + এক = এগার (১০+১=১১), এক দশ চার = চৌদ্দ (১০+৪=১৪) ইত্যাদি। এভাবে দশকের ঘরে দুই (২) হলে বলি দুই দশ = বিশ (১০+১০=২০) এবং দুই দশ এক একুশ (১০+১০+১=২১)। এরূপ – তিন দশ + এক = = একত্রিশ, চার দশ + এক = একচল্লিশ ইত্যাদি।
২. পরিমাণ বা গণনা বাচক সংখ্যা
একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তা-ই পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা। যেমন— সপ্তাহ বলতে আমরা সাত দিনের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকি। সপ্ত (সাত) অহ (দিনক্ষণ) সপ্তাহ। এখানে দিন একটি একক। এরূপ—সাতটি দিন বা সাতটি একক মিলে হয়েছে সপ্তাহ । =
পূর্ণসংখ্যার গুণবাচক সংখ্যা : একগুণ এক। যেমন— একেক্কে এক (অর্থাৎ ১×১=১), এরকম—দুয়েক্কে দুই, = সাতেকে সাত ইত্যাদি। দুই গুণ= দ্বিগুণ বা দুগুণ। যেমন –দুই দু গুণে চার (২×২=৪)।
অনুরূপভাবে, পাঁচ দু গুণে দশ (৫×২=১০), সাত দু গুণে চৌদ্দ (৭x২=১৪)। তিন গুণ = তিরিক্কে। যেমন— তিন তিরিক্কে নয় (৩×৩=৯)।
চার গুণ = চার বা চৌকা। যেমন— তিন চারে বা চৌকা বার (৩X৪=১২) পাঁচ গুণ = পাঁচা। যেমন— পাঁচ পাঁচা পঁচিশ (৫X৫=২৫)।
ছয় গুণ = ছয়ে। যেমন— তিন ছয়ে আঠার (৩২৬=১৮)।
সাত গুণ = সাতা। যেমন— তিন সাতা একুশ (৩×৭=২১) আট গুণ = আটা। যেমন— তিন আটা (বা তে আটা) চব্বিশ (৩৮=২৪)।
নয় গুণ = নং বা নয়। যেমন— তিন নং (বা তিন নয়) সাতাশ (৩X৯=২৭)। দশ গুণ = দশং বা দশ। যেমন— তিন দশং (বা তিন দশে) ত্রিশ (৩x১০=৩০)।
বিশ গুণ = বিশং বা বিশ। যেমন – তিন বিশৎ (বা তিন বিশ) ষাট (৩X২০=৬০)। ত্রিশ গুণ = ত্রিশং বা ত্রিশ। যেমন— তিন ত্রিশং (বা তিন ত্রিশ) নব্বই (৩x৩০=৯০)।
এরূপ— চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশি, নব্বই, বা শ'-এর পূরণবাচক সংখ্যা গণনা করা হয়।
পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক ‘সংখ্যা শব্দ'
(ক) ন্যূন
৩. ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়। যেমন— দ্বিতীয় লোকটিকে ডাক। এখানে গণনায় একজনের পরের লোকটিকে বোঝানো হয়েছে। দ্বিতীয় লোকটির আগের লোকটিকে বলা হয় 'প্রথম' এবং প্রথম লোকটির পরের লোকটিকে বলা হয় দ্বিতীয়। এরূপ— তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ।
৪. তারিখবাচক শব্দ : বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ
বলে।যেমন—পয়লা বৈশাখ, বাইশে শ্রাবণ ইত্যাদি। তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি শব্দ বাংলার নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত।
নিচে বাংলা অঙ্কবাচক, গণনাবাচক, পূরণবাচক ও তারিখবাচক সংখ্যাগুলো দেওয়া হলো